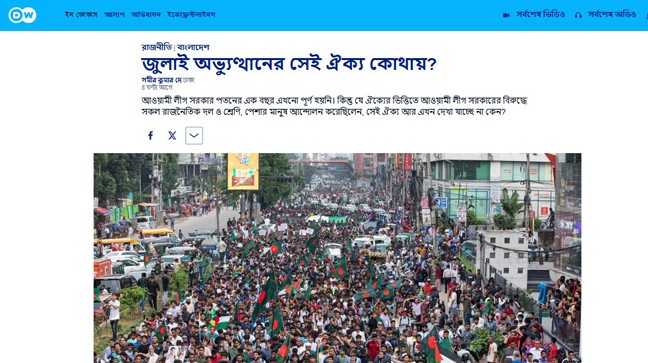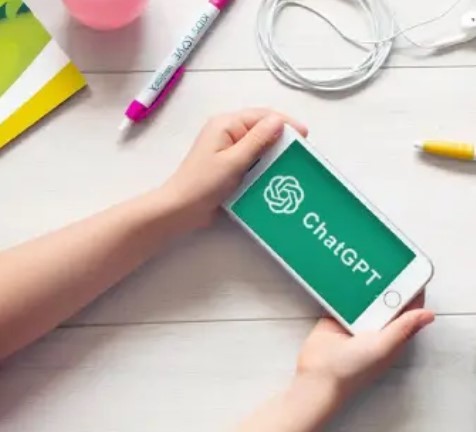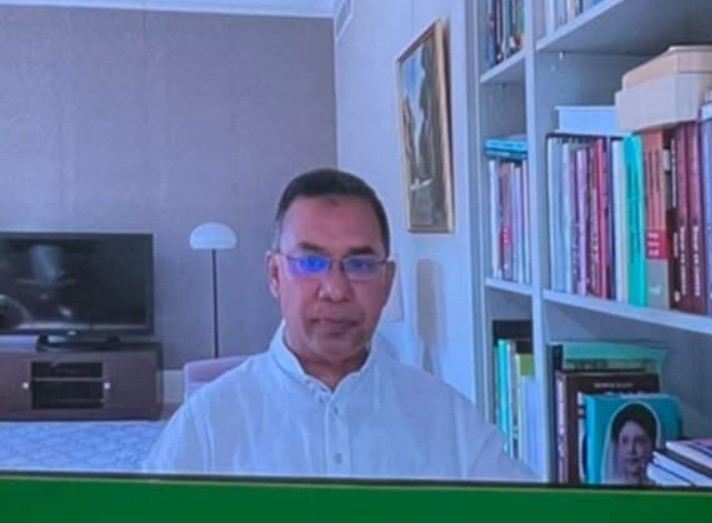গরীব নেওয়াজ: সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশে বিশাল এই জনসংখ্যার ভরণপোষণ এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেশির কারণেই আমাদের এত অভাব-অভিযোগ, দুর্ভোগ, অশান্তি। এসব কথায় মনে হয়, জনসংখ্যাই আমাদের মূল সমস্যা। জনসংখ্যা কমে গেলেই আমাদের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আসলে কি জনসংখ্যাই আমাদের মূল সমস্যা? ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, যখন জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, তখনো লক্ষ-লক্ষ মানুষ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।
ছিয়াত্তরের (১৭৭০ সালে) মন্বন্তরের কথা আমরা জানি, যখন পুরো বাংলায় দুই কোটি মানুষও ছিল না। তখন ওই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। সে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন : ‘চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমূর্ষুদেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শেয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত’।
তিতাল্লিশের (১৯৪৩ সাল) দুর্ভিক্ষের কথা প্রবীণদের স্মরণ থাকতে পারে। তখন দুই বাংলায় সাত কোটির বেশি মানুষ ছিল না। অথচ সে দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ভাতের মাড়টুকুর জন্য কী যে আকুতি তার অনেক কথাই শুনেছি। সেদিন মানুষ শিয়াল-কুকুরেরও অধমে পরিণত হয়েছিল। এই তো সেদিন ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা, তখনো দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষের মৃত্যু হলো। লঙ্গরখানার একটি রুটি বা একমুঠ খিচুড়ির জন্য মানুষ পাগলের মতো ছুটেছে। অথচ সেদিনকার চেয়ে আজকের জনসংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বেশি।
এরও আগে মুঘল আমলেও দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। সুবেদার মীরজুমলার (১৬৬০--১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) আসাম অভিযানকালে বাংলায় ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়যা প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়। জনগণের দুঃখ-কষ্ট এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে, মীরজুমলার সহকর্মী ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন তালিশের কথায়, ‘রুটি হতে জীবন সস্তা মনে হতো এবং রুটি পাওয়া যেত না’। সেদিন সারা বাংলায় লোকসংখ্যা এক/দেড় কোটির বেশি ছিল না। আবার খাদ্যদ্রব্েযর মূল্য কম থাকলেই যে মানুষ সুখে থাকবে তাও ঠিক না। শায়েস্তা খাঁর আমলে যখন টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, তখনো মানুষ না খেয়ে মরেছে। ১৯৭৪ সালে চালের দাম কত ছিল তা জানা আছে।
এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনসংখ্যা আমাদের মূল সমস্যা নয়, জনসংখ্যা কম হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে না, তা দেখানো। জনসংখ্যা মূল সমস্যা হলে গত পঞ্চাশ বছরে যেভাবে মানুষ বেড়েছে, তাতে আজকে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। বরঞ্চ দেখা যায়, জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের অবস্থা তত ভালো হয়েছে। সেই সস্তার যুগে যখন মানুষ অনেক কম ছিল, তখন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অনেক বেশি ছিল। আজ থেকে ৬০/৭০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকে যখন আমাদের জনসংখ্যা কমবেশি পাঁচ কোটি ছিল, তখন গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নগ্ন পায়ে, খালি গায়ে চলাফেরা করত। খাওয়া পরার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। গ্রামের দুই একটি বাড়িতে ছাড়া আর কারও বাড়িতে টিনের ঘর ছিল না; সবই ছোন, পাতা, পাটখড়ির ঘর। হাড়ি-পাতিল, থালা-বাসন সবই মাটির।
ষাট দশকের ছয় কোটি মানুষের তুলনায় কমপক্ষে তিন গুণ মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছি। অথচ আজকে মানুষ অনেক ভালো অবস্থায় আছে। গ্রামীণ জীবনে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের মানুষ আজ জুতা-সেন্ডেল পায়ে দেয়, শার্ট-প্যান্ট পরে, এলুমিনিয়াম ও চীনা মাটির তৈজসপত্র ব্যবহার করে, খাট-পালং বা চোকিতে ঘুমায়। ছোন বা পাতার ঘরের জায়গায় টিনের ঘর, বিল্ডিং উঠেছে।
এককথায় জনসংখ্যা আমাদের মূল সমস্যা নয়। বরঞ্চ দেখলাম, জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, অবস্থা তত ভালো হয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাতে পারি, আমাদের যে সম্পদ আছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলে চল্লিশ কোটি মানুষ খাওয়ানোও কোনো সমস্যা নয়। তাই বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামার দরকার নেই। অবস্থা ভালো হলেই যে ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে কিলবিল করবে, তা ঠিক নয়। Garib Newaz-র ফেসবুক ওয়ালে লেখাটি পড়ুন।