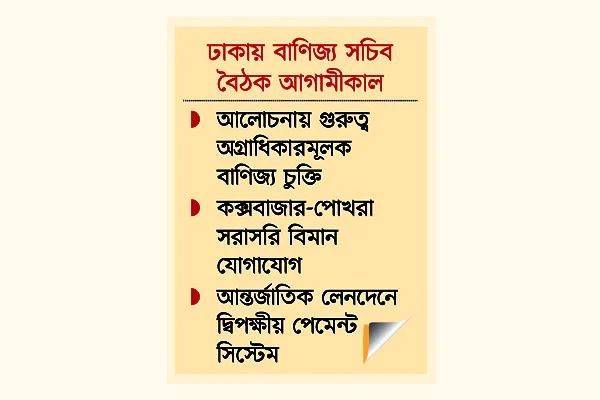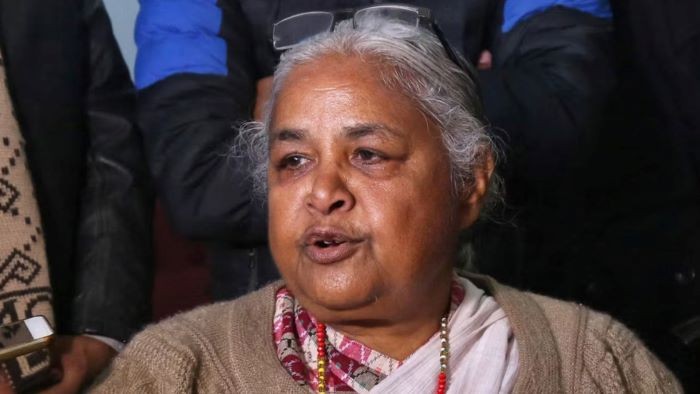খান আসাদ: প্রথম আলোর দুটি সংবাদের শিরোনাম, ‘সিলেটে তরুণী ধর্ষণ’, ‘রাজশাহীতে কিশোরী ধর্ষণ’। এই সংবাদ কী অন্য ভাষায় লেখা যায়? যেমন, সিলেটে বিশ^বিদ্যালয় ছাত্রের বিকৃতকামী সহিংসতা, রাজশাহীতে ধর্মগুরুর বিকৃতকামী নিপীড়ন। অথবা ছাত্রের ও ধর্মগুরুর ধর্ষকামী যৌনসহিংসতা। নারীটি তরুণী বা কিশোরী বলায়, ধর্ষণ শব্দটি প্রতি লাইনে লাইনে লেখায়, জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া কী? একধরনের নরমালাইজেশন ঘটে কী। বিপরীতে এটি একটি ‘বিকৃতি’, একটি ‘পুরুষের’ ধর্ষকামী অপরাধ। ভাষার মধ্যেই বিপরীতভাবে উপস্থাপিত হলেই বা লাভ কী। এই প্রশ্ন করা দরকার।
বাংলাদেশে আপামর শিক্ষিত লোকেরা ধর্ষকের কঠোর শাস্তি চায়। অনুমান কঠোর শাস্তি মানে কম অপরাধ হবে। এই ধরনের চিন্তা হয়তো অপরাধের মহামারি কমাবে। কিন্তু অপরাধের উৎস বন্ধ করে না। মানুষ খুব সরলভাবে মনে করে, কঠোর আইন দিয়ে অপরাধ জন্ম নেওয়া বন্ধ করবে। কিন্তু আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে তো অপরাধ হয়ে যাওয়ার পরে। অপরাধ কেন জন্ম নিলো? এই প্রশ্নের উত্তর আইন দিয়ে মীমাংসা হয় না। এজন্য জার্মানিতে একজন বিচারক, যৌনসহিংসতার বিচার করতে গিয়ে রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক পদাধিকারীদের প্রশ্ন করেন, নারীর যৌন স্বাধীনতার স্বীকৃতি বিষয়ে কী স্কুলে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
জার্মানিতে সমস্যাটা দেখার ভাষা হচ্ছে, strengthening sexual self-determination’ মানে নারীর প্রতি অসম্মান, যৌন ইঙ্গিত, অশ্লীল আচরণ, শারীরিক আঘাত। এই সবই শুধু নারীর শরীরের ওপর আঘাত নয়। আঘাত যৌনতার, ব্যক্তিত্বের ও স্বাধিকারের ওপর। ফলে প্রশ্নটা ব্যক্তির যৌন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের চেতনা বিকাশের। সমাজে, শিক্ষায়, আদালতে, পত্রিকায় নারীর এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা, সংকুচিত করা, আঘাত করা হচ্ছে কী। ধর্ষণ নাম দিয়ে, এটি একটি শারীরিক ব্যাপার করা হচ্ছে কী? নাকি ইতিবাচক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, নারীর যৌন স্বাধিকারের স্বীকৃতি, রক্ষা ও বিকাশের।
যৌন আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাধিকারের প্রশ্নটি ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের ব্যপার। যে কারণে পারসোনাল ইজ পলিটিক্যাল। নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা, শরীর কেন্দ্রিক যৌন-ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায়, আবার যৌন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, স্বাধিকার, ইত্যাদি ভাষা দিয়েও প্রকাশ করা যায়। নারীকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ভাবলে, সেটা প্রকাশের জন্য ভাষার প্রতিও নজর দিতে হবে। শিক্ষাটা পরিবারে, স্কুলে, পত্রিকায়ও সামাজিক মাধ্যমেও দিতে হবে। নতুন ভাষারীতিও নির্মাণ করতে হবে। সেই দায় বুদ্ধিজীবীদেরও। ফেসবুক থেকে

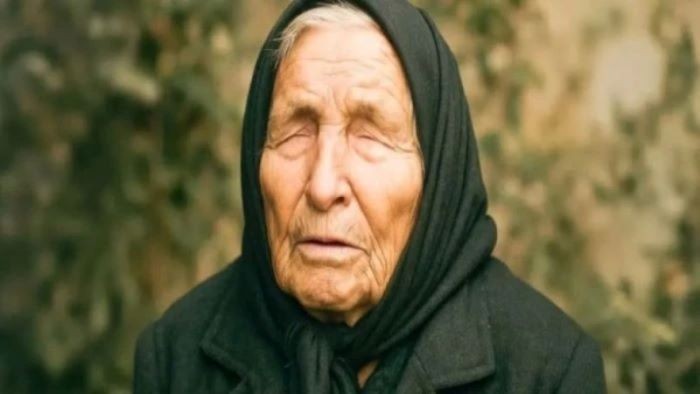
.png)