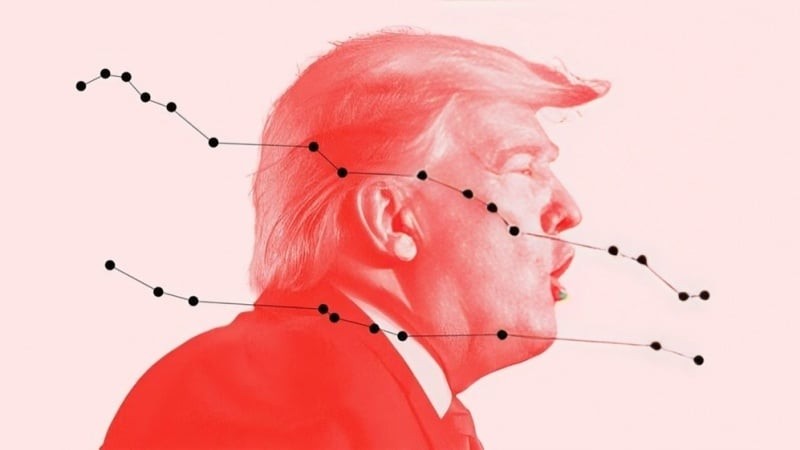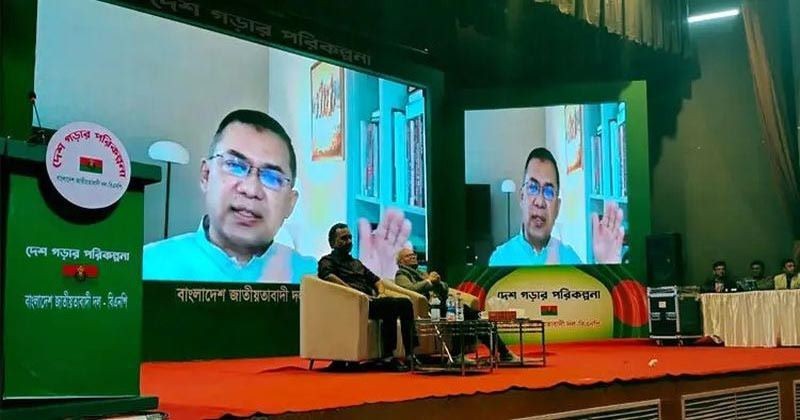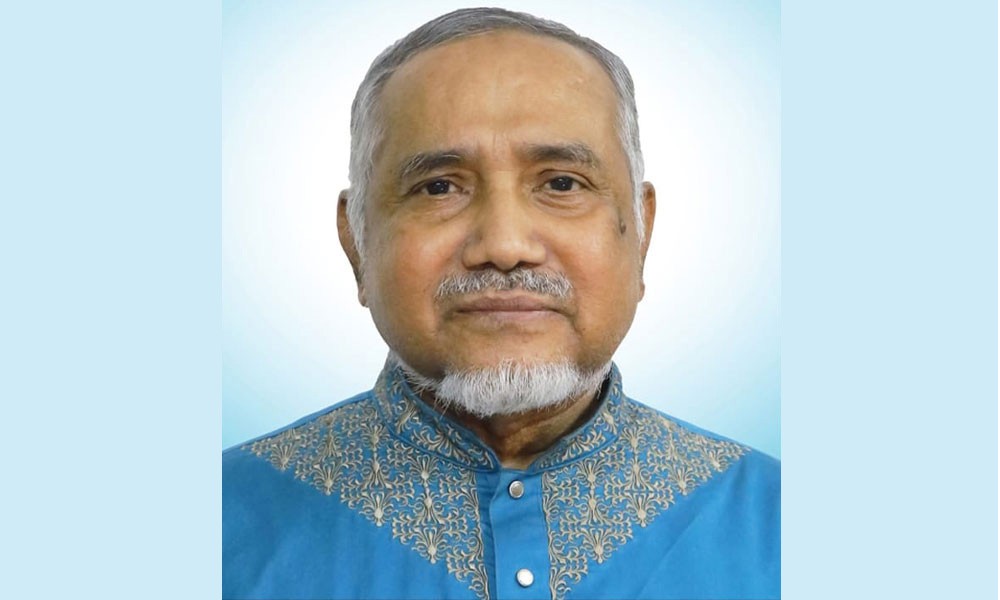কাকন রেজা :  এক.
এক.
তখন যৌবন, কালের বসন্ত। তুমুল লেখালেখি আর আড্ডার নিমগ্ন কাল। সময়টা নব্বই দশকের শেষ বিংশের শুরুর মোহনা। নিজের শহর, আমরা রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে। সাংবাদিকতা তখন পার্টটাইম, ফুলটাইম কবিতা। লেখা ছাপা হয়, শুধু স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতে নয়, ঢাকার জাতীয় দৈনিকেও। সুতরাং পায় কে। রীতিমত উড়ার মৌসুম। সাপোর্টে ‘হোটেল মা-বাবা’ তো রয়েছেই। তবে সে সময়েও আমাদের দুঃখ ছিল উত্তরাধিকার প্রশ্নে। আমাদের পরে কে জেলার সাহিত্য আন্দোলনের হাল ধরবে এ নিয়ে। খুবই হতাশ ছিলাম। কিন্তু আশার আলো জাগালো তিনটি উজ্জ্বল মুখ, সুমন, বিভূতি আর অমিত। তিনজনই উচ্চমাধ্যমিক পড়তে শুরু করেছে, তাও আবার বিজ্ঞানে, কিন্তু ভালোবাসে সাহিত্য। তিনজনেরই লেখার হাত চমৎকার। আমরা বড় ভাই, তবুও লজ্জা কাটিয়ে একদিন আড্ডার শুরু। এভাবে প্রায় প্রতিদিনই বসতাম ‘সাপ্তাহিক শেরপুর’ অফিসে। ফাঁকে বলে নিই, ‘সাপ্তাহিক শেরপুর’ জেলার প্রথম সংবাদপত্র। যার প্রতিষ্ঠাতা আমার পিতা, মরহুম আব্দুর রেজ্জাক। ঢাকার দৈনিক কিষাণ ছেড়ে, শেরপুরে এ জগতের শূন্যতা পূরণে সচেষ্ট মানুষটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পত্রিকাটি। এটি আজো টিকে আছে। যা হোক বলছিলাম, উত্তরাধিকারের কথা, সম্ভাবনার কথা। সুমন, বিভূতি আর অমিতের কথা। আপাতত সুমনের কথা বলি। খুবই ভালো ছাত্র। বিজ্ঞানে পড়া এই ছেলেটিকে নিয়ে হয়তো পরিবারের আশা ছিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরির। কিন্তু সুমনের আকর্ষণ সাহিত্যে। ওর কবিতায় সোজাসাপ্টা বলার ধরণ ছিল খুবই আকর্ষণীয়, আমি ছিলাম মুগ্ধ। পরিবারের চাপের মুখে বিপর্যস্ত সুমনকে বলেছিলাম, সাহিত্যেই রয়ে যেতে। সে রয়ে গেছে। সে আজ ‘সুমন সাজ্জাদ’। একাধারে জাহাঙ্গীরনগরে বাংলার তুমুল জনপ্রিয় শিক্ষক। অন্যধারে কবি ও সাহিত্য গবেষক। বইও রয়েছে বেশকটি এবং তামানোত্তির্ণ। বাংলা সাহিত্যে সুমন, ‘সুমন সাজ্জাদ’ তার জায়গা করে নিয়েছেন। আজ যখন সুমন সাজ্জাদকে টেলিভিশনে সাহিত্যালোচনায় দেখা যায়, যখন মঞ্চে বক্তব্য দেন, তখন তার পরিবারের কাছে আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে, ‘কেমন লাগছে আপনাদের’। আমারতো গর্বে বুক ভরে যায় সুমনকে দেখে, ‘সুমন সাজ্জাদ’কে দেখে।
দুই.
‘সুমন সাজ্জাদ’ প্রসঙ্গ কেন তুললাম, তা বলছি। বলছি আমাদের দেশের অদ্ভুত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। একটি ছেলে সাহিত্যে ভালো, সে বাংলা সাহিত্য বা ইংলিশ লিটারেচার পড়বে। কিংবা একজন থাকবে ফটোগ্রাফি’তে, অন্যজন গাছ ভালো বেসে পড়বে উদ্ভিদবিদ্যায়। না, আমাদের দেশে সেটা সম্ভব নয়। এখানে ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে’ জায়গা পাওয়াই‘ সোনার পাথর বাটি’র মতন, আর বিষয় নির্বাচনতো ‘বহু দূরকাবাত’। সুতরাং কোন রকমে ঢুকতে পারলেই হলো, সে সাহিত্যই হোক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হোক কিংবা আইনবিদ্যা, হলেই হলো তবুতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া। কথা উঠতে পারে, মেধা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনেরতো সুযোগ দেয়া হয়। পাল্টা প্রশ্ন করি, মেধা কাকে বলে? সহসাই কোন ক্ষেত্রে দু’এক নম্বর বেশি পাওয়াকেই মেধা বলে? এমন যোগ্যতায় যদি মেধা মাপা হয়, তাহলে পরিমাপক নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। দশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ নম্বরের হঠাৎ পরীক্ষায় যারা মেধা বোঝার কথা বলেন, সেই পরিমাপের বিষয়টিকে আমি ‘ধৃষ্ঠতা’ বলে আখ্যায়িত করতে চাই। সাথে হঠাৎ করেই কাউকে নিশ্চিত ‘কম মেধা’র ‘সার্টিফিকেট’ দেয়ার এমন ধারাকে এর চেয়ে বেশি সম্মানিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে বিনত ক্ষমা প্রার্থনা করি। এমন ‘সার্টিফিকেট’ প্রদান জনিত বাহুল্যে মেধা ভিত্তিক বিষয় বন্টনটিই অনেকটা ‘বিভ্রান্ত’ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, হুমায়ুন আহমেদ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে ভালো, না সাহিত্যে? পরবর্তী প্রজন্ম কোনটা মনে রাখবে, ইতিহাস কোনটা প্রাধান্য দেবে, শিক্ষকতার হুমায়ুন, না সাহিত্যের হুমায়ুন?
তিন.
ডাক্তার না হয় ইঞ্জিনিয়ার বনতেই হবে, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবার প্রধানরা ছেলে-মেয়েদের এমন ধারণাটি স্কুলের প্রবেশদ্বারের সাথে মাথায় ঢুকিয়ে দেন। পড়ার টেবিলে বসার সময়, পরীক্ষার আগে বারবার তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়, ‘ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার’ হতে হবে। অবশ্য হালসময়ে কোন কারণে দুটি ধারা থেকে ছেলে-মেয়েরা ছিটকে গেলে পরিবার তাদের শেষ এবং আকর্ষণীয় অপশন হিসাবে ‘জনগণের সেবক’ বানাতে উঠে পড়ে লেগে যান। শুরু হয় ‘বিসিএসে’ টেকার আরেক নাছোড় উপাখ্যান।
আমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিসিএসে যোগ দেয়াদের ছোট করার জন্য বলছি না। তারা অবশ্যই মেধাবী, কিন্তু অন্যরা কী নয়? সবাই মেধাবী, তবে মেধার বিকাশের জন্য, প্রমানের জন্য নিজ নিজ পছন্দের ক্ষেত্র দরকার। আনন্দ নিয়ে পড়া আর জোর করে পড়া’র মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, এটা বুঝতে পারাটাই সব চেয়ে আবশ্যিক। একজন মেধাবী জোরকরে পড়ে হয়তো ভালো প্রকৌশলী হবেন, কিন্তু আবিষ্কারক হবেন না। কিন্তু সেই মেধাবী যদি পড়ার আনন্দময় জগত পেতেন তাহলে হয়তো অনেক কিছুই ঘটতে পারতো, আলোকিত হতে পারতো বিশ্বভূবন। হয়তো সে কারণেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ‘আলোকিত মানুষ’ গড়ার কথা বলেন।
চার.
এখন অবশ্য আমাদের দেশে বিকল্প হিসাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। উপায়হীন পিতা মাতারা ‘পাবলিকে’ না পেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’কে বেছে নেন। কিন্তু যাদের ‘উপায়’ অর্থাৎ আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তারা বেছে নেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে, তোড়া তোড়া টাকা দিয়ে যেখানে শিক্ষা কিনতে হয়। যে দেশে ‘শিক্ষা’ কেনার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়, সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উঠে দাঁড়াতে পারে না, পারেনি কোথাও। সে সব দেশই দাঁড়িয়েছে যেখানে শিক্ষাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। তারাই আজ জ্ঞানে-মানে বিশ্বসেরা। আর আমাদের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় সাত’শ সেরার নিচে। তারপরও আমরা গর্ব করি, আহ্লাদ করি শতভাগ পাশের বিষয়ে, উল্লাস করি জিপিএ ফাইভে’র হুজুগে। সেল্যুকাস, সত্যিই হুজুগে জাতি আমরা!
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক
সম্পাদনা : আশিক রহমান ও মোহাম্মদ আবদুল অদুদ