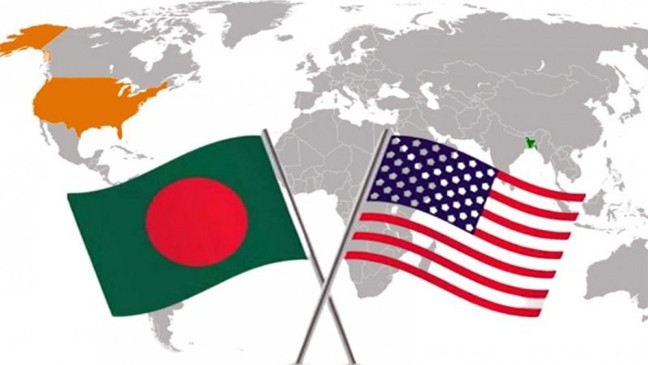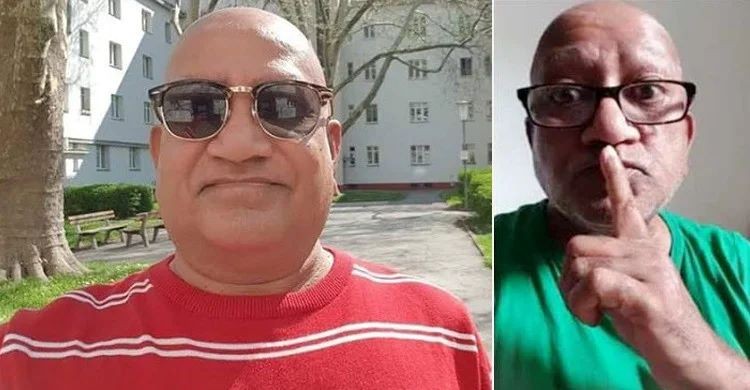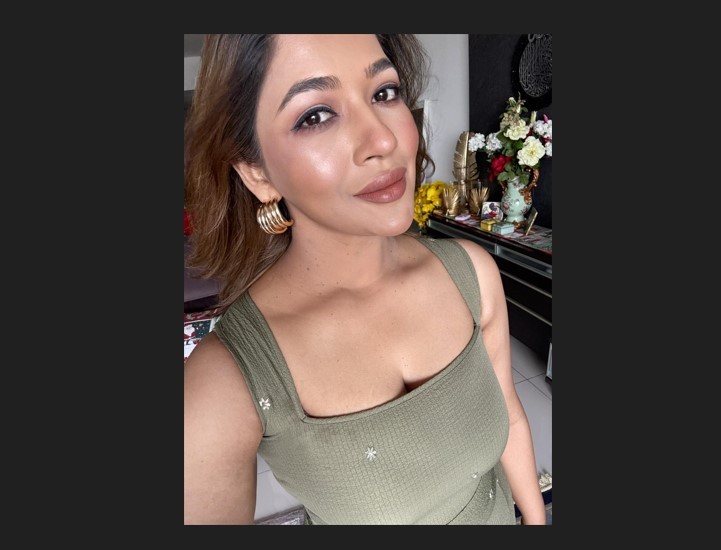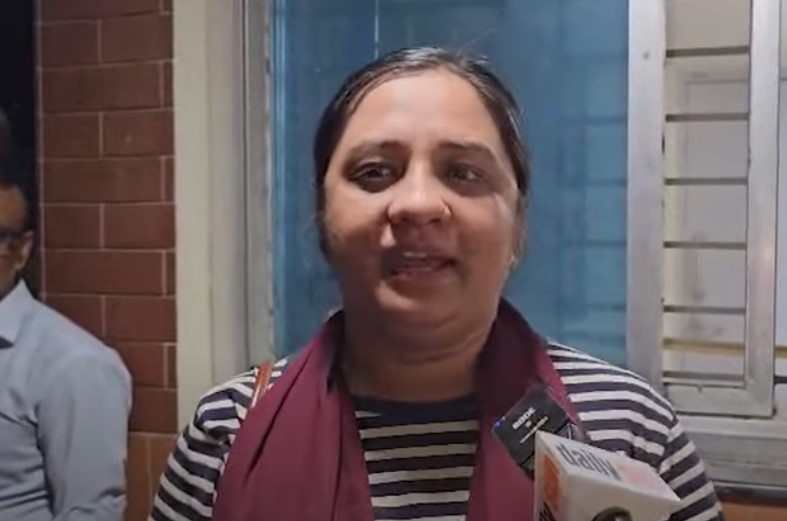জিল্লুর রহমান: ‘রিবা’ শব্দের অর্থ সরাসরি সুদ নয়। সুদ মূলত একটি প্রক্রিয়ার নাম, যা রিবা বা সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। রিবা’র আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি করা। যেমন-আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়।’ ব্যবসার মাধ্যমে বা যে কোন পন্থায় সম্পদ বৃদ্ধি হতেই পারে, তবে সম্পদ বৃদ্ধির অসচ্ছ এবং অনৈতিক প্রক্রিয়াকেই সুদ বলে। উদাহারন দেয়া যাক: ধরুন আপনি একটি রোলস রয়েস গাড়ি বিক্রি করবেন, আপনি চাইলে এটি ক্রেতার কাছে ১০ গুণ দামে বিক্রি করতে পারেন, এটি আপনার জন্য হালাল হবে। কিন্তু আপনি এক কেজি তৈল, কিংবা চাউল তিনগুণ দামে বিক্রি করতে পারেন না, এটি সূদ হবে। কারণ রোলস রয়েস যিনি কিনবেন তিনি চাইলে ২০ গুন দাম বেশি দিয়েও কিনতে পারবেন, এটি সেই ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চাউল আর তেলের দাম কোন কারণ ছাড়াই হুঠ করে তিনগুন বাড়লে সেটি ১০০ জনের মধ্যে ৯৫ জনের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। এই প্রক্রিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি হবে সুদ।
সময়, স্থান কাল পাত্রভেদে রিবা বা সম্পদ বৃদ্ধির এই মাপকাঠি বিবেচনা করতে হবে। শুধু কেনা বেচার ক্ষেত্রে নয়, বিনিয়োগ এবং অংশিদারিত্ব ব্যবসার ক্ষেত্রেও সুদ হয় অসচ্ছ এবং অনৈতিক শর্তের কারণে। যেমন: কোনোভাবেই বিনিয়োগকৃত লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা ধার্য করা যাবে না। ধার্য হবে অংশ অনুযায়ী, লাভের দুই ভাগের একভাগ, কিংবা তিনভাগের এক ভাগ, বা চার ভাগের একভাগ হিসেবে, এবার মুনাফা যে অঙ্কেরই হোক। টাকার বিনিময়ে টাকা নেয়া যাবে না।
বেচা কেনার আরো অনেক শরীয়া আছে, যা মেনে না চললে সুদের কারবার হিসেবে বিবেচিত হবে। এর মধ্যে অন্যতম পণ্য হস্তগত না করে বিক্রি করা। একটি বহুল প্রচলিত হাদিসের সূত্র ধরে বলা হয়, পন্যের দামের একশগুন পর্যন্ত লাভ করা যায়, কিন্তু উক্ত হাদিস ব্যবসার হাদিস ছিলো না, সেটি ছিলো বরকতের হাদিস। এখানেও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। সুদ শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, সকল হারাম উপার্জনকেও সুদ বলা হয়েছে। রিবার আসল অর্থ বৃদ্ধি : তা মূল্যের নয়,পণ্যের মূল্য বিনিময়ের মাঝে যে অসচ্ছ প্রক্রিয়া সেটাই সুদ। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ওই ব্যক্তির ব্যবসা করা উচিত নয়, যিনি ব্যবসার শরীয়া সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয়। লেখক: সাংবাদিক