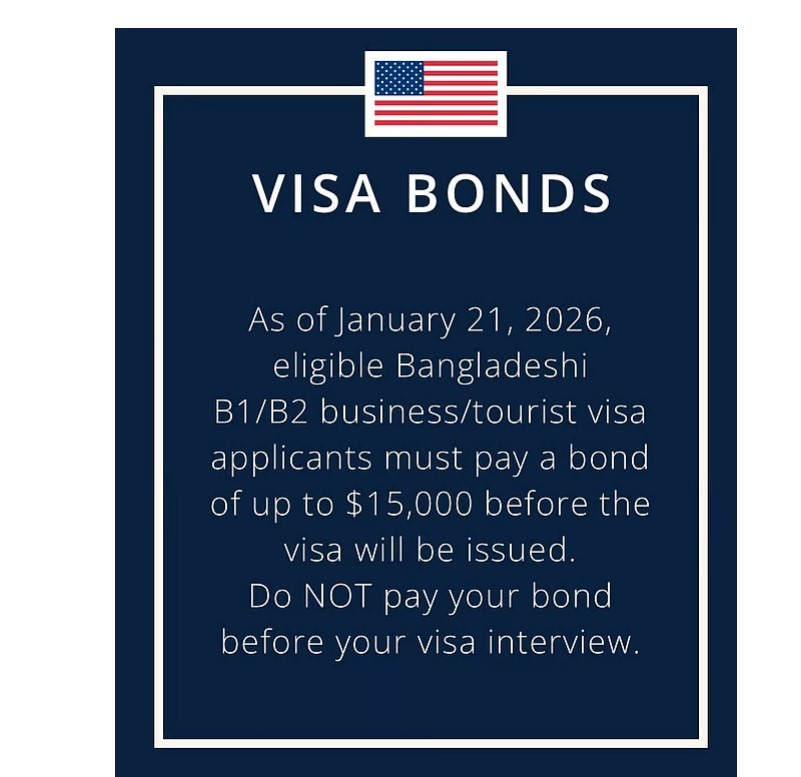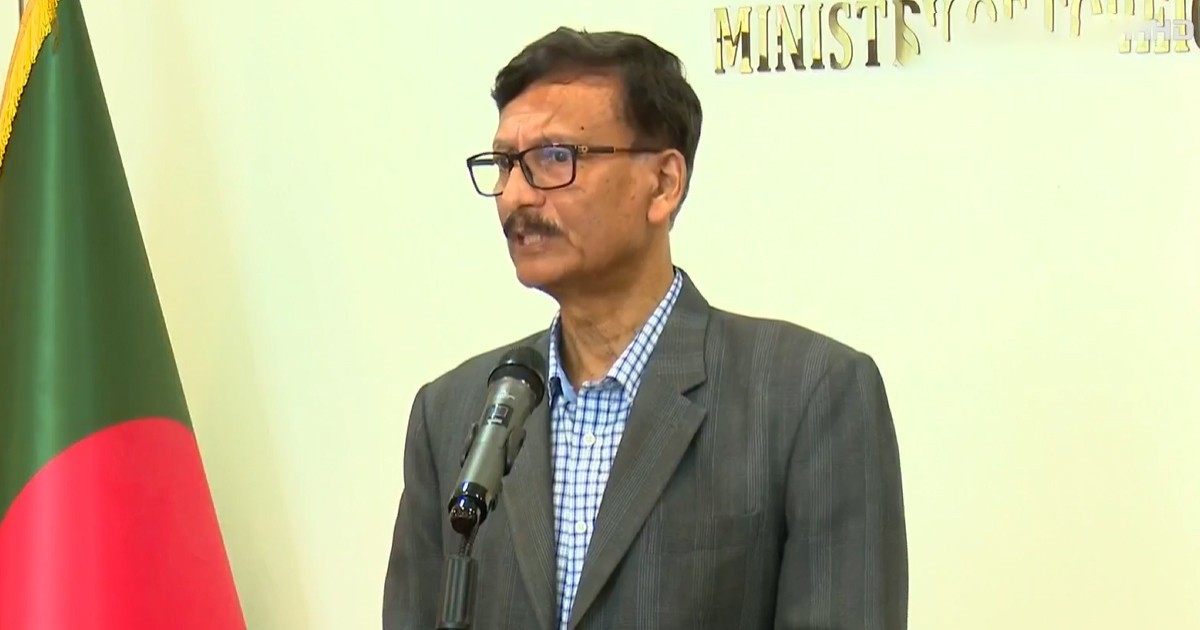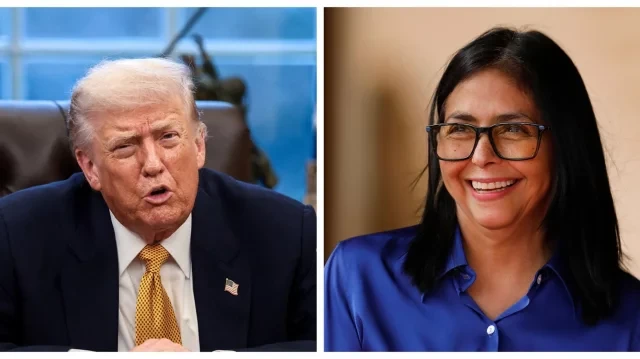তুষার আবদুল্লাহ: অবয়বপত্রে শ্রদ্ধেয় অগ্রজের দেওয়া মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে পারি, তিনি লিখেছেন, ‘টেলিভিশন খুললেই মনে হয় এতো বিটিভি লইয়া আমরা কী করিব?’ আমাদের বিস্তৃত আকাশ এখন সংকীর্ণ। হাতে নিয়ন্ত্রক যন্ত্র থাকলেও আমরা ইচ্ছে করলেই ভিনদেশি চ্যানেলে যেতে পারছি না। থাকতে হচ্ছে দেশীয় চ্যানেলে। বিনোদন দুনিয়ার সুপারশপ থেকে মহল্লার মুদি দোকানে চলে আসতে হয়েছে। এখানে রঙচঙে বাহারি পণ্যের সমাহার নেই। সব মুদি দোকানের মালামাল প্রায় একই আলু, পটোল, সবজি, দুধ ছাড়া চা। স্বাদ পাই না জিভে। বিদেশি চ্যানেলের ওপর ১ অক্টোবর থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সরকার বিদেশি চ্যানেল বন্ধ করার নির্দেশ দেয়নি। বলা হয়েছে আমাদের আকাশে ভিনদেশি চ্যানেলকে আসতে হবে বিজ্ঞাপন ছাড় দিয়ে বা মুক্ত হয়ে। কেন? কারণটা পরিষ্কারশুধু যদি জি বাংলার কথাই বলি, তাদের সারেগামাপা, দাদাগিরি এবং অন্যান্য ধারাবাহিকের বাংলাদেশে যে দর্শক, সেই পরিমাণ দর্শক সর্বসাকুল্যে আমাদের ৩৬টি চ্যানেলে আছে কিনা সন্দেহ। তাই বহুজাতিক পণ্যের বিজ্ঞাপন বাংলাদেশে না এসে ভিনদেশি চ্যানেলে চলে যাচ্ছে। শুধু কী ভিনদেশি বিজ্ঞাপন, দেশি বিজ্ঞাপনও যাচ্ছে। ফলে দেশীয় চ্যানেল থেকে বিজ্ঞাপন সরে যেতে থাকে। এ নিয়ে টেলিভিশন মালিক ও অনুষ্ঠান নির্মাতা ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন অনেক আগে থেকেই। বহুজাতিক পণ্যের বিজ্ঞাপন কমে আসায়, টেলিভিশনের বাজারে যে সংকট দেখা দেয়, তাতে কমমূল্যে বেশি সংখ্যক বিজ্ঞাপন প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছিলো টেলিভিশন চ্যানেলগুলো।
এতে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এতোই বেড়ে যায় যে বিরক্ত হয়ে দেশি চ্যানেল থেকে চোখ সরিয়ে নিতে শুরু করেন দর্শকরা। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো ২০০০ সালের পর থেকেই। যদিও তখন দেশীয় চ্যানেল একুশে, চ্যানেল আই এবং এটিএন বাংলার সুদিন ছিলো। তারপরও বিনোদনের জন্য নির্ভরতা বাড়ছিলো ভিনদেশীয় চ্যানেলের ওপর। ক্যাবল অপারেটরদের ব্যবসাও এসময় সারাদেশে জমে ওঠতে থাকে। ক্যাবল ব্যবসায়ীদের একাধিক সংগঠন তৈরি হয়। খ খ সাম্রাজ্য তৈরি হয় তাদের। সংযোগ প্রতি ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা সেবামূল্য নেওয়া শুরু হয়। ২০০৫ সালের দিকে এসে দেশে চ্যানেলের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি ক্যাবল অপারেটররাও ক্যাবল সংযোগে বাড়াতে থাকে ভিনদেশি চ্যানেলের সংখ্যা। ওই সময় থেকেই ভিনদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন কমতে শুরু করে এবং দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনও উড়াল দিতে থাকে। তখন থেকেই দেশীয় চ্যানেল মালিকরা ক্যাবল সংযোগে ভিনদেশি চ্যানেলে ক্লিন ফিড দাবি করে আসছিলো। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ‘ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ এর ১৯ ধারার ১৩ উপধারায় বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য বিদেশি কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ২০০৭ সালে কিছু চ্যানেল বন্ধও করে দেয় তত্ত¡াবধায়ক সরকার। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।
২০০৮ সালের পর দেশে চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ে। বিজ্ঞাপন বাজারের ভাগিদার বাড়ে। সেই সঙ্গে ভিনদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের বাজার বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়তে থাকে। চ্যানেল মালিকরা আরো অস্থির হয়ে পড়েন। ক্লিন ফিডের জন্যে তাদের দাবি বাড়তে থাকে। কিন্তু তারা নিজেদের অনুষ্ঠানের মান বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেননি। চ্যানেল মালিকরা ক্যাবল অপারেটরদের আয়ত্তে আনতে নানা রকম দাবি তুলতে থাকেন সরকারের কাছে। প্রাথমিক বিজয় আসে ক্যাবল অপারেটরদের দেশীয় চ্যানেলকে অন এয়ারের তারিখ অনুসারে সাজানোর নির্দেশনায়। দ্বিতীয় বিজয় এলো বিদেশি চ্যানেলের ‘ক্লিন ফিড’ সম্প্রচারে। ক্লিন ফিড দেওয়ার বিষয়টিকে জটিল কাজ হিসেবে দেখছেন ক্যাবল অপারেটররা। তাদের মতে, বিজ্ঞাপনমুক্ত সম্প্রচার চ্যানেলকে করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনুষ্ঠান, খেলা বা খবরের আগে, পরে ও মাঝে যে শূন্য জায়গা আছে তাতে দেশীয় বিজ্ঞাপন প্রচার জটিল হবে কিংবা সম্প্রচারের পরে দেখানো যাবে অনুষ্ঠানটি। কিন্তু দেশীয় চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বলছে, যেভাবে সরাসরি সম্প্রচারিত খেলায় বিজ্ঞাপন যুক্ত হয়, সেভাবেই ভিনদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন সংযুক্ত করা যাবে। ক্যাবল অপারেটররা যে অনমনীয়তা দেখাচ্ছে, তা না দেখিয়ে প্রযুক্তিবান্ধব হলে ও দেশীয় স্বার্থ দেখলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে শুরুতেই যেমন বলছিলাম একজন অগ্রজের কথা। দেশীয় সকল চ্যানেল বিটিভির মতো দেখাচ্ছে। অর্থাৎ গুণগতমান ও বিষয় বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র হতে না পারা। এই অক্ষমতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ‘ক্লিন ফিড’ বিজয় উদযাপন না হয়ে দুঃখের কারণও হয়ে ওঠতে পারে। কারণ এরই মধ্যে দর্শকরা টেলিভিশন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। কারণ টেলিভিশন পর্দার ‘লোগো’ বা ‘ডগি’ তুলে নিলে তারা সকল চ্যানেলকে একই পর্দা মনে করছেন। সুতরাং ‘ক্লিন ফিডে’র আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও পুনঃযাত্রা প্রয়োজন। লেখাটি পড়ন অনলাইন নিউজপোর্টাল সংবাদ প্রকাশে।
লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক