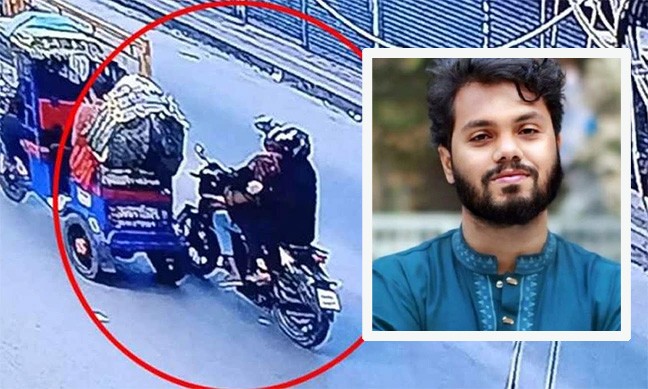রাজিক হাসান: বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়েছিলো ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই। আজ বিধবা বিবাহ আইন পাসের গল্প শোনাই। ফিরে তাকাই অতীতে, হুগলির দশঘরাতে এক অভিজাত বাড়ির একটি ঘটনাতে। সত্যি ঘটনা। ১৮৫৩ সালের বেলা ১১টা। ঘরের মধ্যে চলছে এক আলোচনা সভা। পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত। জলখাবারের আছে লুচি ছোলার, ডাল, নানা মিষ্টি। সুখাদ্যের সুঘ্রানে ঘর মাতোয়ারা। আহার শেষে হবে আলোচনা। বিষয়বস্তু একটি মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গ্রামের মানুষেরা মেয়েদের বাইরে আসতে দিতে নারাজ। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চলছে তারই প্রস্তুতি।
এমন সময় একটি সাদা থান পড়া ছোট্ট ৬/৭ বছরের মেয়ে দৌড়ে এলো ঘরে। বাবা বাবা, মাকে বলো না, আমার খুব খিদে পেয়েছে। দাদারা লুচি খাচ্ছে, আর আমি চাইলেই মা বলছে, ছি! আজ একাদশী না। খাবার কথা বলতে নেই মা। কিন্তু বাবা, আমি সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। একটু জল পর্যন্ত না। তুমি, মা, দাদারা কেউ একাদশী করোনা। আমায় কেন করতে হবে! আমার বুঝি খিদে পায় না? সকলের সামনে লজ্জায়, আর মেয়ের প্রতি মায়ায় করুণ হয়ে ওঠে গৃহকর্তার মুখ। আস্তে করে বলেন, এখানে সভা চলছে মা, তুমি ঘরে যাও। করুণ দৃষ্টিতে সকলের পাতের দিকে তাকিয়ে বিফল মুখে ভেতরের ঘরে ঢুকে যায় একরত্তি অভাগা মেয়েটি। তার পরেই রূপোর থালা বাটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য সুখাদ্য সাজিয়ে ঘরে আসে বামুন ঠাকুর। বিদ্যাসাগর বলেন শরীরটা ঠিক নেই, আমি খাবো না কিছু। নিয়ে যাও।
শুরু হয় সভা। গ্রামের মানুষদের কাছে প্রথমেই বিদ্যাসাগর তুলে ধরেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। নারী শিক্ষা বিষয়ে শ্লোকগুলো বলতে থাকেন একের পর এক। তীক্ষè যুক্তি, উদাহরণ আর বাগ্মিতার সামনে ভেঙে পড়ে সংস্কারের দেওয়াল। সকলে চলে যাবার পর গৃহকর্তাকে বিদ্যাসাগর বলেন, আমি নারীদের শিক্ষার জন্য ছুটছি, কিন্তু এই বিধবা নারীরা, তাদের দুঃখ,তাদের প্রতি এই ধর্মীয় অমানবিকতা এই দিকে সম্পূর্ণ উদাসিন ছিলাম আমি। ছিঃ ছিঃ, ভাবতেই আমার গ্লানি হচ্ছে। রামমোহন রায় মহাশয় তাদের বাঁচিয়ে ছিলেন জ্বলন্ত চিতা থেকে। কিন্তু ওরা মরছে, রোজ জ্বলছে খিদেয়, অবহেলায়,অমানবিকতায়। আপনার কন্যা আজ চোখ খুলে দিয়েছে।
শুরু হলো লড়াই। কলকাতার রক্ষণশীল দল, পুরোহিত সমাজ বিধবা বিবাহের ঘোর বিপক্ষে। তারা কিছুতেই মেনে নেবে না এই অনাচার। তারা পাল্টা আবেদন করেছে সরকারের কাছে, ধর্মবিরোধী এই আইন চালু হলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তারা। বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে চলছে প্রতিবাদ ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ঝড়। নারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নিয়ে অশ্লীল কটূক্তি। বাড়িতে যখন তখন পড়ছে ঢিল, ময়লা, আবর্জনা। একদিন বিদ্যাসাগরকে হামলার মুখেও পড়তে হয়েছে রাস্তায়।
এসব কটাক্ষেও কিন্তু বিদ্যাসাগর অনড়। বড়লাটের দপ্তর বলেছে বেদ পুরানে কি কোনো উদাহরণ আছে পুনর্বিবাহের? না হলে আইন পাশ করা মুশকিল। রক্ষণশীলদের চটিয়ে কিছু করার ইচ্ছা নেই ডালহৌসির। তাই রাতের পর রাত জেগে পুঁথিপত্র পড়ছেন তিনি। অবশেষে পাওয়া গেলো সেই মুক্তো। পরাশর সংহিতার অমর সেই শ্লোক ‘নষ্টে মৃতে প্রবরজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ/পচস্বাপতসু নারীনাং পতিরন্যো বিধয়তে।’(স্বামী মারা গেলে, সন্ন্যাস নিলে, নিখোঁজ হলে, সন্তানগ্রহনে অক্ষম হলে, অধার্মিক ও অত্যাচারী হলে পত্নী আবার বিবাহ করতে পারে।) তিনি ছুটলেন সরকারের দ্বারে। প্রমাণ করলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর বাধা রইলো না কিছুই। এমনই নানা বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে শেষমেশ বিধবা-বিবাহ আইন পাস হলো।
দাশরথি রায় আর শান্তিপুরের তাঁতিরা দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগরের পক্ষে। ‘বিদ্যাসাগর পেড়ে’ শাড়ি বুনলেন তাঁতিরা। পাড়ে লেখা থাকল বিদ্যাসাগরের জয়গান, ‘সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।’ এর পাল্টা বাঙালি শুনলো, ‘শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।’ প্রবল বিরুদ্ধবাদীরা ভাবলেন, আইনে কিইবা হয়। কিন্তু সেই ধারণাও গুঁড়িয়ে গেলো ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। আইনসম্মত বিধবা বিবাহ হল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কালীমতী দেবীর। বিদ্যাসাগরের জয় হলেও এই বিয়ের সূত্রেই তাঁর বৌদ্ধিক ধারণায় নেমে এলো আঘাত। এবার রমাপ্রসাদ রায়ের কাছ থেকে। তিনি এ বিয়েতে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন আগে তিনি জানালেন, এ বিয়েতে তাঁর মনে মনে মত রয়েছে। সাধ্যমতো সাহায্যও করবেন। কিন্তু বিবাহস্থলে না-ই বা গেলেন! ঈশ্বর সব বুঝলেন। আর দেওয়ালে টাঙানো মনীষীর ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।’ ছবিটি রাজা রামমোহন রায়ের। রমাপ্রসাদ তাঁরই পুত্র। রমাপ্রসাদ যে আঘাত দিলেন, পথে নেমে কুৎসিত ভাবে তা-ই যেন প্রকট করল সে কালের বাঙালি জনতার বড় অংশ। বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার ‘অপরাধে’ সমাজে একঘরে করা হল বিদ্যাসাগরকে।
পথে বেরোলেই জোটে গালমন্দ, ঠাট্টা, অশালীন ইংগিত। কেউ বা মারধর, খুনের হুমকিও দেয়। ব্যাপারটা শুধু হুমকিতে থামলো না। বিদ্যাসাগর শুনলেন, তাঁকে খুন করার জন্য ভাড়াটে গুন্ডাদের বরাত দিয়েছেন কলকাতার এক নামী ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর নিজেই সেই তথাকথিত নামীর ঘরে গেলেন। বললেন, ‘শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনাদের ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।’
এই সময়পর্বে ছেলেকে রক্ষার জন্য ঠাকুরদাস বীরসিংহ থেকে জেলে-সর্দার তথা লেঠেল শ্রীমন্তকে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠান। ঠনঠনের কাছে এক হামলার উপক্রম থেকে বিদ্যাসাগরকে রক্ষাও করলেন শ্রীমন্ত সর্দার। শুধু সমাজ নয়, বাঙালির বড় আপনজন, বড় গর্বের ব্যক্তিরও বিদ্যাসাগরকে বুঝতে সমস্যা হলোÑ ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের সূর্যমুখীকে দিয়ে বঙ্কিম লেখালেন, ‘ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?’ আমাদের তৎকালীন আধুনিক অনেক এলিট বুদ্ধিজীবীও তাদের মননের বাটখারায় শুদ্ধ মাপে অপারগ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে মাপতে। যার কারণে জীবনের শেষ বত্রিশ বছর বন্ধুহীন, সমাজহীন হয়ে সরল সাওতালদের অগরল সান্নিধ্য গ্রহন করতে হয়েছিল তাঁকে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "আশ্চর্যের বিষয়, কি করে ভগবান ৪ কৌটি বাঙালির মধ্যে একটি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। সর্বকালের, সর্বযুগের জ্ঞানী ও সমাজসংস্কারক মানবতাবাদী মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি আজকের এই দিনে। ফেসবুক থেকে