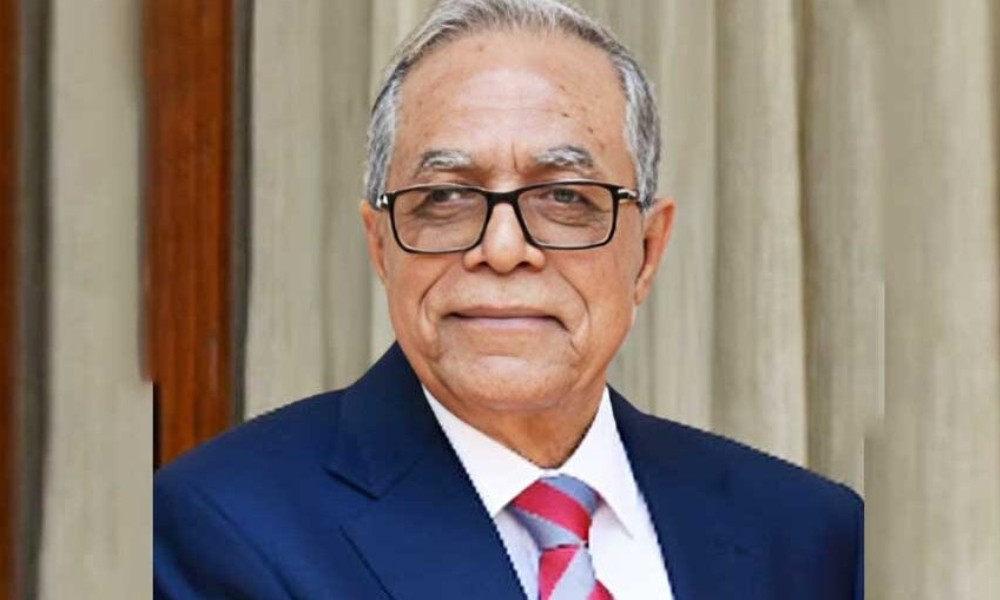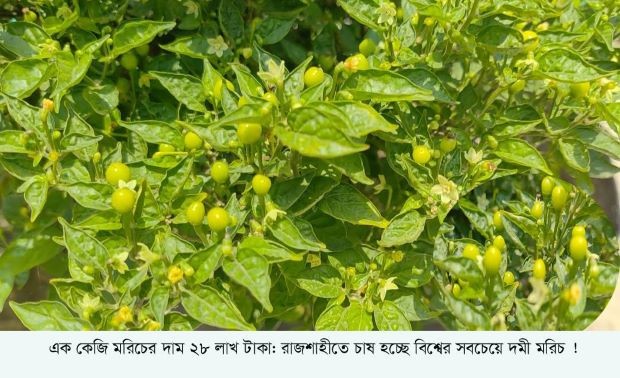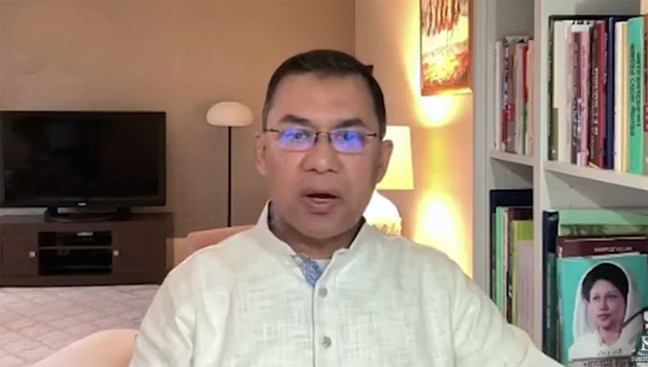সেলিম রায়হান : বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় সংকটের গভীরে। অর্থনৈতিক সংকট সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিশেষ করে দীর্ঘায়িত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির চাপ, দ্রুত-হ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, কম কর রাজস্ব উৎপাদন, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, রপ্তানির অস্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে কম রেমিটেন্স প্রবাহ, উচ্চ মাত্রার মূলধনের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় ও ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে কিছু দীর্ঘস্থায়ী, অন্যগুলো সম্প্রতি এসেছে। রাজপথে প্রধানবিরোধী দল বিএনপি একটি নিরপেক্ষ, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের তীব্র অনিশ্চয়তা ও সংশ্লিষ্ট জটিলতা থেকে রাজনৈতিক সংকটের উদ্ভব ঘটছে, দাবি মেনে না নিলে আগামী নির্বাচন বয়কট করবে। অপরিবর্তিত অভিযোগ রয়েছে যে বর্তমান সরকারের অধীনে বিগত দুটি নির্বাচন ব্যাপকভাবে অপূর্ণ ছিল, যেখানে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল কম।
সমস্যাটি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে রাজনৈতিক সমঝোতা ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে ভেঙে যায়। এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উপর ব্যাপক পক্ষপাতমূলক অবিশ্বাসের ফলস্বরূপ সম্ভবত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আপাত ‘নিরপেক্ষতা’ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল, বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের সব ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দল হেরে যায়। এছাড়াও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে গভীর বিদ্বেষ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্তে ইন্ধন যোগায়। অন্যান্য অনেক ঘটনা যা এই শত্রুতাকে উদ্দীপিত করেছিল, তার মধ্যে একটি নির্ধারক ছিল তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের উপর ২০০৪ সালের আগস্টে গ্রেনেড হামলা, যার একটি শক্তিশালী অভিযোগ ছিল যে এই জঘন্য হামলাটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল। তারপর থেকে উভয় রাজনৈতিক দলের কৌশল ছিল ‘অপরকে দমন করা’।
অর্থনৈতিক ফ্রন্টে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে গুরুতর দুর্বলতা সত্ত্বেও অতীতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনাটিকে ‘বাংলাদেশ প্যারাডক্স’ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক মানের সামগ্রিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। আমি পূর্বে যুক্তি দিয়েছিলাম যে এটি কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছে। কারণ দেশটি কিছু ‘বৃদ্ধি-বর্ধক পকেট’ তৈরি করতে সফল হয়েছে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের যা প্রধান প্রবৃদ্ধি চালকদের চাহিদা পূরণ করে, যেমন তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি, বাংলাদেশিদের কাছ থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ। বিদেশে অভিবাসী শ্রমিক। রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর মীমাংসা-বিশেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এই দুটি বৃদ্ধির চালককে নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে মীমাংসা অটুট ছিল।
তাহলে আমাদের এখন এমন সংকট কেন? এগুলো অতীতের অনিবার্য ফলাফল, অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃদ্ধি-বর্ধক পকেট থেকে উচ্চ লভ্যাংশ গ্রহণের, যা একটি স্ফীত স্বাচ্ছন্দ্য অঞ্চল তৈরি করেছিল, আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নত করতে কিছুই করেনি। ফলস্বরূপ যখন বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি চালকদের থেকে লভ্যাংশ শুকিয়ে যেতে শুরু করে ও অর্থনীতি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে শুরু করে, তখন সঠিক সময়ে সঠিক নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা দেখা দেয়। সমস্যাটি বাংলাদেশের ‘মিশ্রিত শাসনের’ প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, যা দুর্বল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, একটি দুর্বল নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, ব্যবসায়িক খাতের অভিজাতদের একটি অংশের দ্বারা রাষ্ট্র দখল বন্ধুদের আধিপত্যের সঙ্গে জড়িত।
একটি ‘মিশ্রিত শাসন’ কী? বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন ডিগ্রির মিশ্রিত শাসন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির দুটি বিপরীত দিকের সংমিশ্রণ নিয়ে গঠিত হতে পারে, একদিকে ‘উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র’ অন্য দিকে বন্ধুদের আধিপত্য। একটি মিশ্র শাসনের উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের ব্যবহার, দারিদ্র্য হ্রাস করার প্রচেষ্টা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তৈরির জন্য প্রবৃদ্ধির চালক বাড়ানো, উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন দরিদ্রদের জন্য সামাজিক পরিষেবা সম্প্রসারণ।
ফলস্বরূপ এমনকি যখন সংস্কারের নীতিগুলো গৃহীত হয়, সেগুলো বেশিরভাগ কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। সরকার সেগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। নীতি পক্ষাঘাতের কারণে সময়মতো সমালোচনামূলক অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে ব্যর্থতার ফলে অর্থনীতি ও সমাজের জন্য উচ্চ ব্যয় হতে পারে। বাংলাদেশে সংস্কার বিরোধী জোটের বহিঃপ্রকাশ ও এর ফলে ব্যাংকিং খাত, কর খাত, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, আইনি ব্যবস্থা ও আরও অনেক কিছুতে দেখা যায়। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়টি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে চলেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রয়োজন হলেও, সমালোচনামূলক অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ডোমেইনগুলোতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে আরও জোরালোভাবে অনুভূত হচ্ছে।
ব্যাংকিং খাতে বেসরকারি ও সরকারি ব্যাংকের ওপর যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃথক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করতে হবে। বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পূর্ণ ও স্বাধীন কর্তৃত্ব দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত যারা আর্থিক নীতি, বিনিময় হার নীতি ও বৈদেশিক রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে কোনো রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে না থেকে। প্রাইভেট ব্যাংকে ক্রোনিদের প্রভাব কমাতে ব্যাংকিং খাতের আইন সংস্কার করতে হবে। এছাড়াও বড় ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কর্তৃপক্ষ যদি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চায় তবে ব্যাংকিং খাতের আইনি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।
কর খাতে একটি সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত দুর্নীতি হ্রাস করা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে দুটি কাজে বিভক্ত করতে হবে। ব্যাপক কর ফাঁকি কর অব্যাহতি হ্রাস করার লক্ষ্যে নীতি ও আইন সংস্কার করা দরকার। অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা বা ত্বরান্বিত করার জন্য রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজন। বাংলাদেশে এর জন্য একটি সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শিল্প নীতির প্রয়োজন হবে যেখানে নন-আরএমজি সেক্টরগুলোকে কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা প্রদান করা হবে। আরএমজি সেক্টরের জন্য, সেখানে শ্রম অধিকার ও কাজের অবস্থার সমস্যাগুলো যথাযথভাবে সমাধান করা দরকার। পাবলিক ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্টে, বৃহত্তর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক ক্ষমতার উন্নতি ভাড়া চাওয়ার সুযোগ কমাতে পারে। আইন ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সরলীকরণ, দায়িত্বের ওভারল্যাপ দূর করা, সমস্ত স্কেল ও সময়সীমার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণমানকে উন্নত করবে।
উল্লেখ্য ভূ-রাজনৈতিক গতিশীলতার পরিবর্তনের কারণে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে কয়েকটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাংলাদেশ একটি ছোট উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তার ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভালোর জন্য বড় বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে সুসম্পর্ক থেকে কোনো বড় বিচ্যুতির কারণে অবাঞ্ছিত বাহ্যিক চাপ আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করতে পারে। বাংলাদেশের মিশ্র শাসনের সংকট মোকাবেলায় সংস্কারবিরোধী জোট ভেঙে নীতিগত পক্ষাঘাত ঠিক করতে হবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পরে, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শুরুর সম্ভাবনা নির্ভর করবে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতা জোটের অভিনেতাদের মধ্যে সংস্কারের জন্য সমর্থন জোগাড় করতে পারবে কি না।
লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এর নির্বাহী পরিচালক।
সূত্র : ডেইলি স্টার। অনুবাদ : মিরাজুল মারুফ