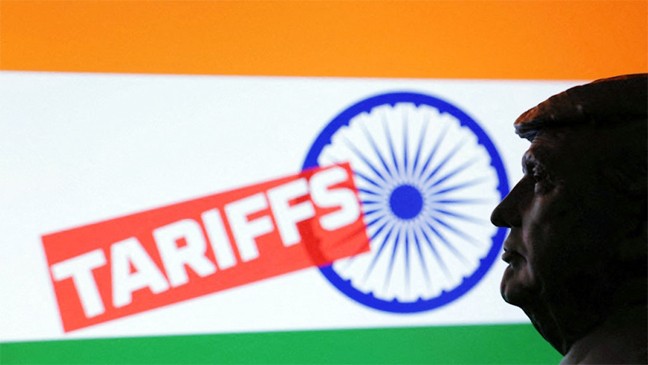ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে আরব নেতাদের মুখোশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানি শাসন–পরবর্তী যে আরব রাষ্ট্রগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা এ অঞ্চলের নিজস্ব অধিবাসীদের জন্য নয়, ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষায় গঠিত। সম্প্রতি মিডল ইস্ট আইয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ এবং ‘চ্যান্সেলরস চেয়ার’ পদে অধিষ্ঠিত উসামা মাকদিসির লেখা এক নিবন্ধে এমন মতামত তুলে ধরা হয়েছে।
নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯১৮ সালে, ওসমানি শাসন–পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এটি স্বীকার করে ব্রিটিশ ভারতের একজন কর্মকর্তা লিখেছিলেন, ‘পুরোনো স্লোগান এখন অচল। আমাদের নতুন পথ বেছে নিতে হবে; যা মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। কাজটি সম্ভব, তবে তার জন্য কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। 'আরব মুখোশ' হয়তো আমাদের পূর্বপরিকল্পনার চেয়ে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হতে পারে।’
১৯১৯ সালের তথাকথিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সময় ব্রিটিশরা বুঝে যায়, ব্যাহত প্রতীয়মান ‘স্বনির্ধারণীর’ এ যুগে নিজেদের আধিপত্য আর সরাসরি চাপিয়ে দিতে পারবে না তারা। তাই তাদের আধিপত্য আড়াল করতে দরকার ‘স্থানীয় কর্তৃত্ব’ নামের এক মুখোশ।
কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, যেমন টি ই লরেন্স ভাবতেন, তারা আরবদের সহায়তা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের অহংকার চরিতার্থ করছেন। কিন্তু তারা মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই সেবক ছিলেন।
এই সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে চাইছিল; অন্যদিকে দাবি করছিল, ওসমানি শাসন–পরবর্তী নতুন এ স্বাধীনতার যুগকে তারা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছেন।
ব্রিটিশরা ওসমানি শাসকদের উৎখাতে আরবদের সহায়তা করেছিল। ১৯১৬ সালে হাশেমি নেতা শরিফ হোসাইন ইবনে আলিকে সমর্থন ও অর্থসহায়তা দিয়ে আরব বিদ্রোহে উসকানি দেয় তারা। হাশেমিরা আগে ওসমানিদের সেবা করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের পক্ষে চলে যায়।
এ ‘আরব মুখোশ’ ছিল ব্রিটিশদের ‘পরোক্ষ শাসন’ নামে এক পুরোনো কৌশলেরই নতুন সংস্করণ—যেমনটা আফ্রিকায় চালু করেছিল তারা। এখানেও সেই ছাঁচে নতুন একটি ব্যবস্থা গড়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনো প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্যোগ রুখে স্থানীয় শাসনের নামে নিজেরাই শাসন চালিয়ে যাওয়া।
পরোক্ষ শাসন
ব্রিটিশরা ওসমানি শাসকদের উৎখাতে আরবদের সহায়তা করেছিল। ১৯১৬ সালে হাশেমি নেতা শরিফ হোসাইন ইবনে আলিকে সমর্থন ও অর্থসহায়তা দিয়ে আরব বিদ্রোহে উসকানি দেয় তারা। হাশেমিরা আগে ওসমানিদের সেবা করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের পক্ষে চলে যায়।
ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি স্বাধীন আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি শরিফ হোসাইনকে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তবে এ বিশাল এলাকায় সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব তারা কখনোই দিতে চায়নি। শুধু চেয়েছিল, ওসমানিদের ঐক্য ভাঙতে।
আরবদের এখন এটা জানা—ব্রিটিশ ও ফরাসিরা গোপনে ঠিক করে রেখেছিল কীভাবে ওসমানিদের আরব ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। এ গোপন চুক্তির নাম সাইক্স-পিকো চুক্তি (১৯১৬), যা সরাসরি আরবদের দেওয়া ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ‘সাইকস–পিকো’ শব্দবন্ধ উপনিবেশবাদকে সামগ্রিকভাবে বোঝাতে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
আজকের আরব শাসকেরা নিজেদের কিছুটা কৌশলী ভূমিকা রাখতে পারেন। তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি অনুগত থেকে, বিশেষত ফিলিস্তিন প্রশ্নে জনমতের বিপরীতে গিয়েও। এ শাসকেরা কখনো পাশের দর্শক, কখনো সহচর, কিন্তু একবাক্যে বলা যায়, তারা এমন এক বহিঃশক্তির ছত্রছায়ায় টিকে আছেন, যে শক্তি মুসলিম ও আরবদের তাচ্ছিল্য করে।
এর ঠিক এক বছর পর ১৯১৭ সালে, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে একটি ‘ইহুদি জাতীয় আবাস’ প্রতিষ্ঠার সমর্থনে কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণা মূলত ফিলিস্তিনে ইউরোপীয় ইহুদিদের একটি জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ স্থাপন প্রকল্পকে সমর্থন করেছিল; যেখানে সে সময় ইহুদিরা ছিল জনসংখ্যার এক ছোট অংশ। অথচ ফিলিস্তিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব জনগণের জাতীয় অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছিল। এ ঘোষণা আরবদের অবজ্ঞাসূচকভাবে শুধু ‘ইহুদিবহির্ভূত সম্প্রদায়’ বলে উল্লেখ করে।
সাইক্স-পিকো ও বেলফোর ঘোষণার পর মুখোশ পাকা করার প্রয়াস
সাইক্স-পিকো ও বেলফোর ঘোষণার তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ক্ষুব্ধ আরবদের শান্ত করতে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা প্রকাশ্যে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তাদের লক্ষ্য ঘোষণা করে। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে তারা এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, তাদের উদ্দেশ্য হলো ‘তুর্কি নিপীড়নের’ অবসান ঘটিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা দেওয়া।
এ ঘোষণার (অ্যাঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ ডিক্লারেশন নামে পরিচিত) অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, মুখোশটিকে আরও পোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করা। এ মুখোশের মূল উপাদান ছিল এমন এক অনির্বাচিত স্থানীয় শাসক, যিনি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুগত থাকবেন; নিজের ভাগ্য ও পরবর্তী বংশকে ব্রিটিশ আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত মনে করবেন; ইহুদি উপনিবেশ গঠনে ব্রিটিশ সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবেন না; ফিলিস্তিন মুক্তির দাবিতে জনতার চাপ কমাতে হয় আশ্বাস, নয় দমন-পীড়নের পথ বেছে নেবেন। এসব শর্ত মেনে নিলে শুধু নামমাত্র স্বাধীনতা পাওয়া যাবে।
ইতিহাসবিদেরা দেখিয়েছেন, এ কাঠামোর সঙ্গে হাশেমি পরিবার যেমন মানিয়ে নিয়েছিল, তেমন অন্যান্য আরব রাজবংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেমন ইবনে সউদ ও মিসরের বাদশাহ ফুয়াদ। শরিফের দুই ছেলে—ফয়সাল ও আবদুল্লাহকে ইরাক এবং ট্রান্সজর্ডানে পুতুলশাসক হিসেবে বসানো হয়।
আরব-মার্কিন লেখক আমিন রিহানি তার ইরাকি রাজা ফয়সালের জীবনীতে লিখেছিলেন, ‘এ ধরনের শাসকদের হতে হতো উপনিবেশবাদের ক্রীড়ানক থেকেও একটু বেশি, কিন্তু স্বাধীন নেতা থেকে কিছুটা কম।’
এটাই ছিল ১৯২০-এর দশকের ‘আরব মুখোশ’। এর বিপরীতে, তুরস্কের মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক নেতৃত্বাধীন কামালপন্থী আন্দোলন পশ্চিমা বিভাজনের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন, গ্রিসের সঙ্গে জনসংখ্যা বিনিময়, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ নীতির অনুসরণ নিন্দিত হয়, তবু তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে বহুগুণ দৃঢ়।
নাকবার পরপরই নতুন প্রতিরোধ
১৯৪৮ সালের ‘নাকবা’ তথা ফিলিস্তিনি উৎখাতের পর মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক কর্মকর্তারা পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামেন। মিসরে গামাল আবদেল নাসের ও তার ‘ফ্রি অফিসার্স’ ব্রিটিশপন্থী রাজাকে উৎখাত করে ১৯৫২ সালে বিপ্লব ঘটান। ইরাকেও ১৯৫৮ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে হাশেমি রাজতন্ত্রের পতন হয়।
কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশদের স্থান নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। আর তারাই আবার গড়ে তোলে নতুন রূপের ‘আরব মুখোশ’।
দ্বিতীয় প্রজন্মের ‘মুখোশ’
আজকের ‘আরব মুখোশ ২.০’ প্রকৃতপক্ষে সেই পুরোনো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ছকেরই পুনরাবৃত্তি। তবে এবার তা যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো শর্তগুলোর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে, তেল রাজস্বের পাশ্চাত্যমুখী পুনর্বিনিয়োগ।
আজকের আরব শাসকেরা নিজেদের কিছুটা কৌশলী ভূমিকা রাখতে পারেন। তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি অনুগত থেকে, বিশেষত ফিলিস্তিন প্রশ্নে জনমতের বিপরীতে গিয়েও।
এ শাসকেরা কখনো পাশের দর্শক, কখনো সহচর—কিন্তু একবাক্যে বলা যায়, তারা এমন এক বহিঃশক্তির ছত্রছায়ায় টিকে আছেন, যে শক্তি মুসলিম ও আরবদের তাচ্ছিল্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায় মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সম্প্রসারণবাদী ইসরাইল।
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, অসলো ‘শান্তি প্রক্রিয়া’ ও তথাকথিত আব্রাহাম চুক্তি—সবই মার্কিন ছকে গড়া একধরনের আত্মসমর্পণ; যা ‘সহনশীলতা’ ও ‘সহাবস্থান’-এর মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। আরব দেশগুলো একের পর এক ছাড় দিচ্ছে, আর ইসরাইল তাদের দখল বাড়াচ্ছে। তবু এই সাম্রাজ্যিক ছকের বিরুদ্ধে এখনো প্রতিরোধ আছে—গাজা, লেবানন ও ইয়েমেনে।
কিন্তু যারা মার্কিন স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তারা এই প্রতিরোধকে অস্বীকার করেন এবং গণতান্ত্রিক মুক্তিকেও বাধা দেন। কেউ কেউ তো ইসরায়েলি দখলদারত্বে বিনিয়োগও করছেন। ‘আরব জাতীয়তাবাদ’ হয়তো বিলুপ্ত। কিন্তু ‘আরব মুখোশ’ এখনো রয়ে গেছে।
এ পাঠ একরকম পরিষ্কার। আগে যেমন ছিল, এখনো তেমন। এ মুখোশ কোনো মুক্তির পথ দেখায় না; বরং মুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি কখনো জনগণের জন্য নির্মিত হয় না—তাতে যত ভালো মানুষই আশ্রয় নিক। তবে উপনিবেশবাদের মতো এ মুখোশের স্থায়িত্বও চিরকাল নয়। এ মুখোশ টিকিয়ে রাখতে যে দমননীতি চালানো হচ্ছে, গাজায় চলমান গণহত্যার প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলি ঔপনিবেশিকতা নিয়ে জনমনে যেভাবে ক্ষোভ জমেছে, তাতে আরব নেতাদের মুখোশ আর কত দিন টিকবে, তা সময়ই বলে দেবে। সূত্র: মিডল ইস্ট আই