
মোজাফ্ফর হোসেন: বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদে মোটাদাগে দুটি সমস্যা আমার চোখে পড়ে। বাংলা সব শব্দের জোর করে ইংরেজি অনুবাদ করার চেষ্টা; দুই. একান্তই বাধ্য হয়ে কোনো বাংলা শব্দ ইংরেজি প্রতিবর্ণে রাখলে সেটা আইটালিক করে দেওয়া। বিষয়টি সমস্যা না মনে করলে সমস্যা না; কিন্তু আমি মনে করি অনুবাদ-রাজনীতির একটা বড় বিষয় হলো নিজের কিছু আইডেন্টিন্টি (ভাষিক ও সাংস্কৃতিক) ভিনদেশি ও অন্য ভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেমন ধরুন: বটি; ইংরেজি অনুবাদে বটি হিসেবেই থাকবে। মা/বাবাকে ফাদার-মাদার করার দরকার নেই। ম্যাটারনাল আন্ট না বলে, বাংলা মিস্টি শব্দ ‘খালা’ রেখে দেওয়ার পক্ষে আমি। লুঙ্গি, গামছা, বা বিড়ির মতো শব্দগুলোর ইংরেজি অনুবাদ হয় না। সংস্কৃতির মৌল বিষয় অনুবাদ করলে কিছু থাকে না। যেমন, রাজাকারকে আমরা ট্রেইটর করতে পারি, কিন্তু করলেই তো হবে না। রাজাকার শব্দের একটা ওজন আছে আমাদের ইতিহাসে। মসজিদ মসক্ হতে পারে, মোনাজাত/নামাজকে কেন প্রেয়ার করব? এ রকম শতশত শব্দের কথা বলা যাবে যেগুলোর অনুবাদ হয় না, বা হলেও অনুবাদে আমাদের সংস্কৃতির ওজনটা ধারণ করতে পারে না।
বর্তমানে কোনো কোনো অনুবাদক প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দ রাখছেন ইংরেজি প্রতিবর্ণে। কিন্তু অধিকাংশ আইটালিক করে দেন। আইটালিক করে দিলে খুব চোখে লাগে। হয়তো এক হাজার শব্দের মধ্যে একটা শব্দ আইটালিক, তখন সেটা এলিয়েন বা বিচ্ছিন্ন কিছু মনে হয়। বোঝা যায়, যে ভাষায় অনুবাদ করা হলো সেভাষার অংশ না। অথচ অনুবাদে সেই শব্দ রাখা মানে আমি কিন্তু সেই ভাষার অংশই করে তুললাম। আমরাই আবার যখন বাংলা ভাষার মধ্যে কোনো ইংরেজি শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণে ব্যবহার করি তখন কিন্তু আইটালিক করছি না। আমরা ধরে নিচ্ছি বাংলা ভাষার সকল পাঠক ইংরেজি শব্দটা বোঝেন। কিন্তু আমার বাংলা শব্দটা বিদেশি পাঠক বোঝেন না। এখন আইটালিক করে দিলেও কিন্তু বুঝবে না। বুঝতে হলে ইন্টারনেটে যেতে হবে। তবে অধিকাংশ সময় কনটেক্সটই অর্থ করে দেবে। কোনো অনুবাদক চাইলে বইয়ের শেষে গ্লোসারি দিতেই পারেন। না দিলেও এই ইন্টারনেটের যুগে এসে অসুবিধা দেখি না।
আফ্রিকা/লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদে প্রচুর লোকাল শব্দ থাকে, অধিকাংশ ইটালিক করা থাকে না। আমাদের বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাঠকের পড়তে তো অসুবিধা হচ্ছে না। এই অসুবিধা না হওয়ার একটা বড়ো কারণ লাতিন আমেরিকা/আফ্রিকার ইংরেজি সাহিত্য সেই ঐতিহ্য তৈরি করে দিয়েছে। চিনুয়া আচেবের মতো লোকাল-কণ্ঠস্বর যখন ইংরেজিতে লেখেন তখন অনেক স্থানীয় শব্দ অলরেডি ইনসার্ট করে দেন ইংরেজি ভাষার মধ্যে। কথাটা ভীষণভাবে খাটে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নাইপল-রুশদি থেকে শুরু করে ঝুম্পা লাহিড়ি, রহিনটন, ভারতী, অমিতাভ, কিরণ-অনিতা প্রমুখ লেখকরা ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য (বা ভারতীয় সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ভার্সন) রচনার মধ্য দিয়ে প্রচুর হিন্দি/উর্দু/সংস্কৃত শব্দ ইংরেজি ভাষার অংশ করে তুলেছেন। ফলে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকদের অনেক শব্দের যথার্থ ইংরেজি থাকলেও গ্রহণ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। বাংলাদেশি ইংরেজি সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এই সুবিধাটা আমাদের অনুবাদকরা পাবেন। আমাদের দেশের গল্প, আমাদের ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় যত বেশি রচিত হবে তত বেশি আমাদের শব্দ/ভাষা/সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠবে। বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ তখন আরো সহজ হয়ে যাবে। অনুবাদককে বোধগম্যতা নিয়ে ভাবতে হবে না।
সকালে আরিফ আনোয়ারের ‘দি স্ট্রম’ উপন্যাসটি পড়তে পড়তে কথাগুলো মনে আসল। আরিফ ভাই প্রচুর বাংলা শব্দ নিয়ে এসেছেন এই উপন্যাসে। ইংরেজি প্রতিবর্ণে তো আছেই, বাংলা বর্ণমালাও ব্যবহার করেছেন অনেক জায়গায়। বইটি কানাডা থেকে প্রকাশ করেছে হারপারকলিন্স। আরিফ আনোয়ার এই আত্মবিশ্বাসটা পেয়ে থাকতে পারেন কায়সার হক স্যারের কাছ থেকে। কায়সার হক স্যার নিজের মৌলিক রচনা কিংবা অনুবাদে সমানভাবে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। নিয়মিত অনুবাদকদের মধ্যে আবদুস সেলিম স্যার, ফকরুল আলম স্যার, হারুনুজ্জামান স্যার-সহ নতুন অনুবাদকদের কেউ কেউ সেটা করেন। আর কিছু না, এই আত্মবিশ্বাসটুকুই দরকার, আর এটা এমনি এমনি আসবে না, এর সঙ্গে একটা রাজনীতি জড়িয়ে আছে, পলিটিক্স অব ট্রান্সলেশন। লেখক: কথাসাহিত্যিক
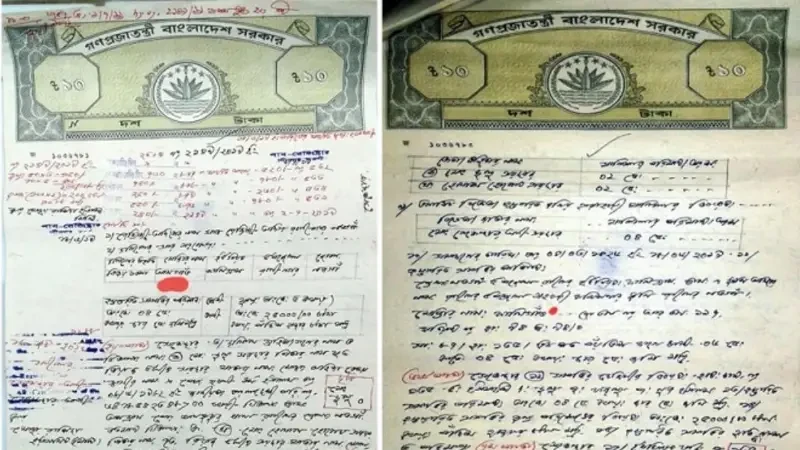







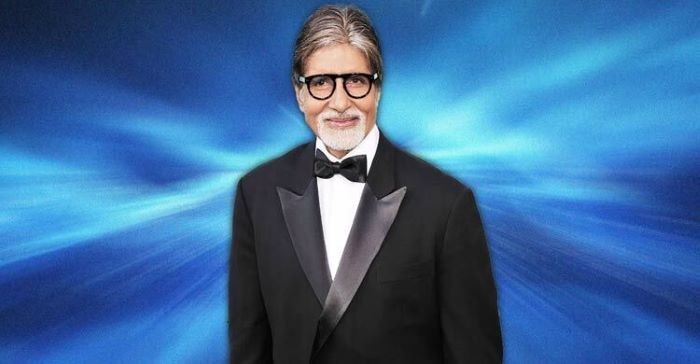




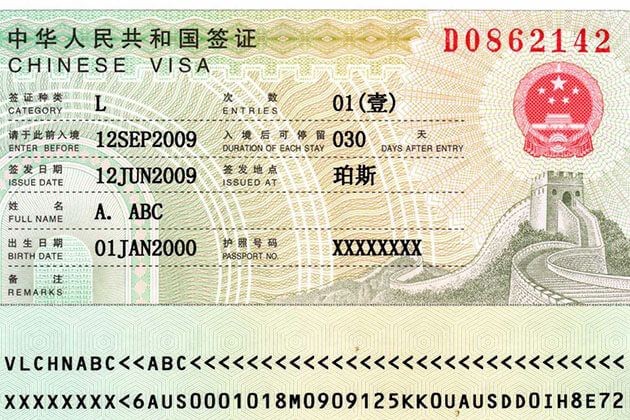







_School.jpg)


