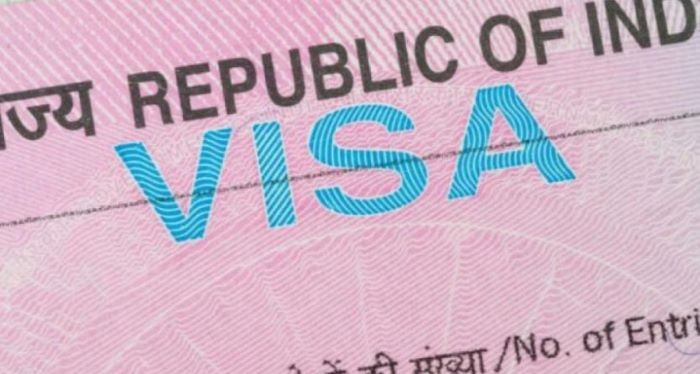অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭টি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এই ১৭টির মধ্যে একটির সামান্য বা নন-জিরো ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর আছে। বাকি ১৬টির মধ্যে ২০১০ সাল থেকে ৫টির কোনো ইস্যু বের হয় না।১টির কোনো ওয়েবলিংক নেই। আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ সাইন্স এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ স্ট্যাটিসটিক্স আজ প্রায় যথাক্রমে ৬৮ বছর এবং ৫২ বছর যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। এসব জার্নাল প্রকাশিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা খরচ ব্যতীত কোনো লাভ কি হচ্ছে? শুধুই কি টাকা খরচ? শ্রম ঘণ্টার অপচয় না? কাগজেরও অপচয়। লাভতো হচ্ছেই না উল্টো ক্ষতি হচ্ছে অনেক। কি রকম ক্ষতি জানতে চান? এই জার্নালগুলো হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্টিকেল মেনুফ্যাক্টচারিং মেশিন ছাড়া কিছুই নয়। অনেকে আবার অসংখ্য আর্টিকেল প্রসব করে নিজেকে বড় বিজ্ঞানী প্রমাণের জন্য লিখে দেন দেশি বিদেশি জার্নালে আমার শতাধিক আর্টিকেল আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে শতাধিকের অধিকাংশই নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্বেজ জার্নালে। চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে তারা আবার এমন নিয়ম করেছে যে ওখানে আর্টিকেল প্রকাশ করতে অথরদের অন্তত একজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে। পৃথিবীতে মোট প্রায় ৩৪১০০ জার্নাল প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে ৬০শতাংশই প্রকাশিত হয় ‘প্রফেশনাল সোসাইটি’ যেমন আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স ইত্যাদি থেকে। বাকিগুলো প্রকাশিত হয় বড় বড় পাবলিশিং কোম্পানি থেকে যেমন ঊষংবারবৎ, ঝঢ়ৎরহমবৎ ইত্যাদি কোম্পানি। আর খুবই খুবই স্বল্প সংখ্যক জার্নাল প্রকাশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও পাবেন না বললেই চলে যেখানে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালের নিজেরা এডিটোরিয়াল বোর্ডে থেকে জার্নাল প্রকাশ করে সেখানে নিজেদের শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে আর্টিকেল প্রকাশ করায় এবং সেগুলো ব্যবহার করে প্রমোশন নেয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে ৫০ এরও অধিক গবেষণা সেন্টার। এগুলোতে যদি সত্যিকারের গবেষণা সেন্টার হতো তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব রেংকিংয়ে অন্তত ২০০-র মধ্যে থাকতো। অথচ এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য টাকা বরাদ্দ দিতে হয়। এসব গবেষণা সেন্টারগুলোর অধিকাংশই এক্ষণি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এগুলো গবেষণা সেন্টারের নামের কলঙ্ক। তাছাড়া জার্নালগুলোও এক্ষণি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এগুলোও জার্নাল নামের কলঙ্ড়। ৫০ বছরেরও বেশি বছর থেকেও যদি কোনো উন্নতি করতে না পেরে থাকে ৫০০ বছরেও হবে না। এসব গার্বেজ জার্নাল থাকার কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সহজে গবেষণা পত্র প্রকাশ করে সহজে প্রমোশন পেয়ে অধ্যাপক হয়ে যাচ্ছেন। ফলে তারা ভালো মানের গবেষণা করার জন্য যেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় সেটা হতে হয় না। এই না হওয়ার কারণে দেশে ভালো মানের গবেষক তৈরি হচ্ছে না। বরং গবেষক নামের অভিনেতা তৈরি হচ্ছে। নিজেদের একেকজন বড় বড় গবেষক হওয়ার ভান করে বেড়াচ্ছেন যা নতুন প্রজন্মের মাঝে সংক্রামিত হচ্ছে। তাই এসব জার্নাল ও গবেষণা সেন্টার বন্ধ করে বরং শিক্ষকদের ভালো মানের জার্নালে প্রকাশ করলে প্রণোদনা দানে ব্যবহার করা যায়। বুয়েট সম্প্রতি একটি নিয়ম করেছে। ভালো মানের জার্নালে প্রকাশ করলে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিচ্ছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্প্রতি একটা নিয়ম করেছে কিন্তু সেটা কেবল অনলাইন জার্নালে প্রকাশ করলে যেই প্রকাশনা খরচ লাগে সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে। গবেষকরা কোনো রিওয়ার্ড পাচ্ছে না। আমাদের সময় এসেছে কিছু ভালো কাজ করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়িয়ে আগামী প্রজন্মকে গবেষণামুখী করার। উন্নত হওয়ার এটাই সবচেয়ে সেরা পথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো জার্নাল থেকে কোনো আর্টিকেল প্রকাশ করে কোনো শিক্ষককে আজ পর্যন্ত দেখেছেন একটি স্ট্যাটাস দিয়ে খুশির বার্তাটি সবাইকে জানাতে? কখনো না। যাক এটুকু লজ্জাবোধ যে আছে। ভালো একটি জার্নালে একটি আর্টিকেল ধপপবঢ়ঃবফ হলে পরে যেই আনন্দ আছে তার প্রকাশ মাঝে মধ্যে ফেসবুকে আমরা দেখি। একটি ভালো মানের গবেষণাপত্র প্রকাশ একটি সন্তান জন্ম দানের আনন্দের মতো যেটা ওইসব গার্বেজ জার্নালে প্রকাশ করলে ভেতর থেকেই আসে না। এগুলো বন্ধ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টাকা সাশ্রয় হতো এবং গবেষণার মান বাড়তো। লেখক : শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়