
বণিক বার্তা: ডা. এএম শামীম। ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। স্বাস্থ্যসেবা খাতে গ্রুপটি অবদান রাখছে মূলত চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ উৎপাদনের মাধ্যমে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান, ভূমিকা ও ওষুধ শিল্পের আগামীর সম্ভাবনা নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি আমাদের সময়.কমের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো-
গত পাঁচ দশকে স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিধি বেড়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কতটুকু?
স্বাধীনতার পর সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে শয্যা সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭ হাজার। এখন তা দেড় লাখে দাঁড়িয়েছে। তখন ১৭ হাজার মানুষের জন্য একটি শয্যা ছিল। আর এখন এক হাজার মানুষের জন্য একটি শয্যা রয়েছে। তখন ১৪ হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে চিকিৎসক ছিলেন একজন আর এখন ১ হাজার ৬০০ মানুষের জন্য একজন রয়েছেন। এভাবে বিবেচনা করলে স্বাস্থ্যসেবায় অবকাঠামো থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। স্বাধীনতার আগে ৯০ ভাগ স্বাস্থ্যসেবাই ছিল সরকারের তত্ত্বাবধানে। আর ২০২১ সালে এসে দুই-তৃতীয়াংশ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এসেছে। এখন বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রায় ৯০ ভাগই বেসরকারিভাবে হচ্ছে। ৯০ দশকের শেষে বেসরকারিভাবে প্রথম ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠান যাত্রা করে। সে সময় থেকে একটি অবকাঠামোতেই রোগ নিরীক্ষণ, চিকিৎসকের বিশেষায়িত সেবা, ফার্মেসির সুবিধা বেসরকারিভাবে শুরু হয়। মূলত ওই সময় থেকেই এক ছাতার নিচে সব ধরনের সেবা পেতে শুরু করে দেশের মানুষ। আগে প্রতিটি বিশেষায়িত সেবার জন্য মানুষকে আলাদা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হতো। আবার একটা সময় ছিল যখন সব ধরনের পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি পাওয়া যেত না, রোগ নিরীক্ষণের জন্য বিদেশে যেতে হতো। যেসব পরীক্ষার জন্য একসময় প্রচুর টাকা খরচ হতো, সেসব পরীক্ষা এখন দেশে প্রতিদিন শত শত হয়। এখন বাংলাদেশের যেকোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রোগ নিরীক্ষণের প্রতিবেদন বিশ্বের বড় প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রহণ করে।
আগে কিন্তু এমন ছিল না। সরকারি চিকিৎসকরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সময় শেষে ১-২ ঘণ্টার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে আসতেন। এখন দেশে ১০০ শয্যার বেসরকারি হাসপাতালই রয়েছে প্রায় ২০০টি। ১৪ হাজার নিবন্ধিত বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল রয়েছে। আর অনিবন্ধিত রয়েছে আরো প্রায় সাত হাজার। এসব মিলিয়ে স্বাধীনতার ৫০ বছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসেবায় বেশি ভূমিকা রাখছে। দ্বিতীয়ত, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবাগুলো আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাই। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ বেশির ভাগ সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যায়। মধ্য ও উচ্চবিত্তরা বেসরকারি হাসপাতালে আসেন। তবে এর পরও আমাদের খুশি হওয়ার তেমন কিছু নেই। কারণ স্বাস্থ্যসেবা এখনো অনেক মানুষের নাগালের বাইরে। সব হাসপাতালের মান এক নয়। তবে আমরা বলতে পারি, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার মতো বা নেয়ার মতো হয়েছে।
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা ও সন্তুষ্টি কতটুকু? এসব প্রতিষ্ঠান মানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যয়ের বোঝা বাড়িয়েছে কিনা?
আমাদের দেশের বাজেটের প্রায় ৫ শতাংশ বরাদ্দ স্বাস্থ্যসেবায় রয়েছে। এতে জনপ্রতি ১ হাজার ২০০ টাকা বরাদ্দ থাকে। এটা যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানুষের নিজ পকেট থেকে ৭০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ হয়। আবার মানুষ মাসের অন্য সব খরচের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখলেও নিজের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কিন্তু কোনো বরাদ্দ রাখে না। ফলে পরিবারের কারো জন্য জরুরি স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হলে বেশির ভাগ সময়ই অর্থের সংকট দেখা যায়। কারণ আমাদের মানসিক প্রস্তুতি নেই, আমরা প্রতি মাসে ২ হাজার টাকাও স্বাস্থ্যসেবার জন্য জমা রাখি না। সেজন্য স্বাস্থ্যবীমাও প্রয়োজন। পাশের দেশ ভারতেও কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ মানুষের স্বাস্থ্যবীমা রয়েছে। এতে আপনি কিছু টাকা দেবেন, স্বাস্থ্যবীমার প্রতিষ্ঠান কিছু দেবে। পাশাপাশি সরকার কিছু দিলে ভালো একটি স্বাস্থ্যসেবার খরচ পাওয়া যাবে। বেসরকারি সেবা ব্যয়সাপেক্ষ, এটা ঠিক। এখানে যদি ভারতের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে দেখবেন একই রকম। থাইল্যান্ডের সঙ্গে এক-চতুর্থাংশ ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তুলনা করলে এক-দশমাংশ।
আমি মনে করি, স্বাস্থ্যসেবায় রোগীর পক্ষের বাড়তি খরচ কমাতে হলে স্বাস্থ্যবীমা, স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যক্তির সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারি ব্যয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা জরুরি।
বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয় সরকার নির্ধারিত নয়। এ সুযোগটা বেসরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে কিনা?
এখন মুক্তবাজার অর্থনীতি। একটি সাধারণ এক্স-রে মেশিন ২ লাখ টাকায় কিনতে পারবেন। তবে এতে রোগী যে রেডিয়েশন পাবে তাতে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে। একই সঙ্গে নিরীক্ষণ নিখুঁত হবে না। আমরা যে এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করি তা কিন্তু ৩-৪ কোটি টাকা দাম। এ মেশিনের প্রতিটি এক্স-রেতে ৪০০ টাকা নেয়া হয়। একই মেশিনে এক্স-রে করতে সিঙ্গাপুরে ৮ হাজার টাকা নেয়া হয়। আর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দাম কেন নির্ধারিত থাকবে? সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তেমন সুবিধা পাই না। হাসপাতালটির অনুকূলে ব্যাংকঋণ রয়েছে। সেখানে কিন্তু আমরা সুদের হারে ছাড় পাইনি।
পোশাক শিল্পে বা তথ্যপ্রযুক্তিতে যে প্রণোদনা সুবিধা দেয়া হয়, তেমন কিছু বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পায় না। জমি কেনার ক্ষেত্রে বা যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে অন্যান্য খাতের মতো সুবিধা দেয়া হয় না। বেসরকারি হাসপাতালে ২ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা চিকিৎসকের বেতন দেয়া হয়। বেসরকারি হাসপাতালে ভালো মানের আসবাব, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকতে হয়। অপেক্ষার জন্য সময় ব্যয় না করেই মানুষ চিকিৎসা নেয়। ভালো অবকাঠামো, যন্ত্রাংশ থাকতে হয়। উচ্চমানের সেবা চাইবেন আর মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন, তাহলে সেটি হবে বিপরীতমুখী।
উচ্চমূল্যের স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা সবার নেই। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের শতভাগ আস্থা এখনো অর্জিত হলো না কেন?
স্বাস্থ্যসেবা সংবেদনশীল। এখানে মানের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৬০০ টাকা নেয় আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৩০ হাজার টাকা নেয়। সেখানে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগকারীদের সুবিধা না দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করার কথা কেন বলবেন? সিঙ্গাপুরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিতে ৪ লাখ টাকা খরচ করতে পারেন, একই বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় এখানে ২০ হাজার টাকা দেবেন না? অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞের অভাব থাকে। সেখানে ন্যূনতম অর্থে চিকিৎসার সুযোগ নেই। এ বিষয়গুলো নিয়ে বিরোধিতার কিছু নেই। আমরা বলব, হাসপাতালের শ্রেণীবিন্যাস করা হোক। কোন হাসপাতালে কোন মানের চিকিৎসা হয়ে থাকে, সেটি নির্ধারণ করা থাকুক। আপনি এ্যাপোলো, ইউনাইটেড, স্কয়ার, ল্যাবএইডে যে চিকিৎসা পাবেন, তা মফস্বলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাবেন না। সেখানে একটা এক্স-রে যদি ৬০ টাকায় হতে পারে, আমরা তো সেটা দিতে পারব না। আমাদের মেশিন মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের মানের। একই সঙ্গে আমাদের রেডিওলজিস্টও আন্তর্জাতিক মানের।
বছরে ১০-১২ লাখ মানুষ বিদেশে চিকিৎসার জন্য যায়। তাদের সব মিলিয়ে কিন্তু ৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। গত দুই বছরে এসব মানুষ বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারেনি, দেশে চিকিৎসা নিয়েছে। বিশ্বমানের চিকিৎসা পাওয়ায় সেই অভাব দেখা যায়নি। মৃত্যুরও খবর নেই। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যতই সমালোচনা করা হোক করোনায় মৃত্যু ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো হয়নি।
মূল্য নির্ধারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সরকারকে সহযোগিতা করছে না এমনটি শোনা যাচ্ছে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা মানুষের আর্থিক সক্ষমতার মধ্যে আনতে সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কী?
আমরা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথা বলেছি। সরকার মান উন্নয়নে কাজ করতে পারে। প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে নানা কার্যক্রম করতে পারে। হাসপাতালগুলো চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা তার জন্য পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে। একটা শক্তিশালী স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করতে হবে।
ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যু হয় এমনটি বিভিন্ন সময় বলা হয়। কিন্তু কখনই চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা দেন না। একটা অস্ত্রোপচারে ১০০ জনের মধ্যে একজন মারা যায়। এক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসা বলা যায় কি? এ রকম হলে তো চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে। আবার রোগীর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের মতামত দেয়। কেউ অস্ত্রোপচারের পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেয়। পরে আবার মামলাও করে।
আমাদের মান নিয়ন্ত্রণে আসতে হবে, স্বাস্থ্য কমিশন বা পরিষদ করতে হবে, ডেন্টাল ও মেডিকেল কাউন্সিল শক্তিশালী করতে হবে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে সমর্থন করতে হবে। আমরা তো এদেশেরই মানুষ। স্বাস্থ্যসেবার আয়ের অংশ তো আমরা বিদেশে পাঠাই না। ভালো লোকগুলোই স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। আবার আমাদের মধ্যে শাহেদ, সারবিনা আছে। তাদের বিষয়েও সতর্ক হতে হবে।
সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি। এসবে চিকিৎসক, নার্স, শয্যাও বেশি। সরকারি আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার স্বাস্থ্যসেবার মান ভালো বলে আপনি মনে করেন?
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। আমি তো সবার দায়িত্ব নিতে পারব না। যদি প্রথম ৩০০ বা ৪০০ প্রতিষ্ঠানের কথা বলি তাহলে বলব, অবশ্যই সরকারির চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ভালো। বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য মানুষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসে। সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। গ্রামীণ পর্যায়ে পৌঁছতে হলে আপনাদের কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?
এটা দুঃখের বিষয় যে, আমরা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা দিতে সমর্থ হইনি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে আরো মানসম্মত করতে হবে। আমরা তো বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা। আমাদের তেমন বিনিয়োগের সুযোগ ছিল না। আমরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এতটুকু এসেছি। আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই। রাজধানীতেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের ইতিহাস বেশিদিনের নয়। ভারতে অনেক প্রতিষ্ঠান ১০০ বছর বয়সী, তারা কিন্তু অনেক আগেই শুরু করতে পেরেছে। আমাদেরও সেই সময়টা প্রয়োজন।
আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাই।
সারা দেশে আমাদের ডায়াগনস্টিকের ৩০টি শাখা রয়েছে। আমরা এটাকে প্রতিটি জেলায় নিয়ে যেতে চাই। জেলাগুলোয় ভালো ডায়াগনস্টিক সেন্টার নেই, ভালো চিকিৎসক নেই, ভালো পরীক্ষাও হয় না। আমরা যখন বগুড়ায় শাখা খুললাম তখন আশপাশে আরো ভালো প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছে। এটা ভালো বিষয়। ল্যাবএইড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পর ভালোমানের আরো প্রায় ৫০টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমরা বিশেষায়িত সেবা দিচ্ছি। ক্যান্সারের চিকিৎসাও শুরু করে দিয়েছি। জটিল চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। চট্টগ্রামে একটা হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করছি। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য রাজধানীতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের বিনামূল্যে সেবা দেয়া হবে। আমরা সেখানে ভর্তুকিও দেব। আমরা চাই আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আমাদের ১৫০০ শয্যার চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে ৬০টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থাকবে।
আমাদেরও একটা দুঃখ যে সবাই চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে সরকারি একটা সুবিধা চাই। এ করোনার সময় চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের ৬০ শতাংশই ওষুধে খরচ হয়েছে। এখানে সরকার যদি ওষুধগুলো রোগীর নামের বিপরীতে বিনামূল্যে দিত, তাহলে আমরা কম মূল্যে সেবা দিতে পারতাম। আমি বলব, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান কখনই প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক। ৩০ বছর পর দেখবেন হাজার হাজার মানসম্মত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যাবে। আগামীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোই স্বাস্থ্যসেবায় নেতৃত্ব দেবে।
প্রতিষ্ঠান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানের হেরফের হবে কিনা?
মানের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কারণ মানুষ জানে, কোথায় কম সময়ে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যসেবাটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মানুষের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকে। আমরা তো একদিনের জন্য ব্যবসা করি না। বাংলাদেশের বাজারে ফরমালিন দেয়া মাছ, রাস্তায় যানজট, পত্রিকায় ভালো খবর নেই, বাতাসে সিসা, এখানে কোনো চিকিৎসা হয় না—এসব কথা আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ৩০ বছর আগে নিজের দেশেই বাইপাস সার্জারি করান। যেন তার দেশের মানুষ চিকিৎসার ওপর আস্থা রাখতে পারে। আমাদেরও দেশের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ১০টার মধ্যে একটা খারাপ ঘটনা ঘটে। তাহলে আমরা কেন একটা খারাপ ঘটনা নিয়ে পড়ে থাকব? ৩০০ জনের অস্ত্রোপচার হলে তিনজনের মৃত্যু হয়। সেই তিনজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না। চেষ্টা করতে হবে এ মৃত্যুর সংখ্যা যেন আরো কমিয়ে আনা যায়। ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা থাকলে বিনিয়োগকারীরা আসবেন না।
আপনি ওষুধ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এ খাত অনেক এগিয়েছে। এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে কিনা?
ওষুধ শিল্প নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করে। গর্ব করার কারণও রয়েছে। দেশের প্রয়োজনীয় ওষুধের ৯৮ ভাগই আমরা নিজেরা উৎপাদন করি। আমাদের দেশে ওষুধের উৎপাদনমুখিতা ৭০ বছরের। আমাদের ওষুধের মান অত্যন্ত ভালো। দামের কথা বললে, যে অ্যান্টিবায়োটিক ৬০ টাকায় কিনছি, ফাইজারের তৈরি সে ওষুধই ৮৫০ টাকায় বিক্রি হয়। যে প্যারাসিটামলটা আপনি ৩ টাকায় কিনছেন, সেটা অন্যান্য দেশে ৮০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।
আমাদের সতর্ক হতে হবে ভেজাল ওষুধের বিষয়ে। ওষুধের জন্য কোল্ড চেইন বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখতে হবে। বাংলাদেশে দেড় লাখের বেশি ফার্মেসির মধ্যে এক লাখের বেশি ফার্মেসিতে এসি নেই। অনেক ফার্মেসির ওপরে টিনের চাল। এসব ওষুধের দোকানে সাদা ওষুধের বোতল গরমে হলুদ হয়ে যায়। এসব সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এসবের কারণে ৯৪ ভাগ ওষুধই কিন্তু কাজ করে না।
দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ওষুধ আইন ও ওষুধ নীতি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে। এক্ষেত্রে অনৈতিক সুযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে থাকে বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?
বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ওষুধ আইনটি যুগান্তকারী। সেখানে বলা হয়েছে, কিছু অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম সরকার নির্ধারণ করবে। পরে এর সংখ্যা কমানো হয়েছে। কোনো ওষুধ তিনটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করলে তা বিদেশ থেকে আমদানি করার সুযোগ নেই। সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন করা ওষুধের দাম ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দেয়।
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করা দামই তো ঔষধ প্রশাসন নির্ধারণ করে দেয়। তারা তো কমিয়ে নির্ধারণ করে না।
বিষয়টি সঠিক নয়। তাদের একটি নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্যানেল রয়েছে। তারা যে দাম নির্ধারণ করে দেয় তাই আমরা মান্য করি। এখানে আমি বলব ওষুধ শিল্পে কিছু অপচর্চা রয়েছে। ব্যবস্থাপত্রে যারা ওষুধ লিখবেন তারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের থেকে সরাসরি উপঢৌকন নেবেন না। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে আইন রয়েছে। কোনো ওষুধের সমর্থনের জন্য বিভিন্ন সেমিনার, বিদেশে যাওয়া এগুলো চিকিৎসকরা সরাসরি করতে পারেন না। ওষুধের বিষয়ে স্বচ্ছ আইন করা গেলে ওষুধের দামও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে।
ওষুধ শিল্পের জন্য সরকার যে এপিআই পার্ক তৈরি করছে, সেটা কতটুকু কার্যকরী হবে বলে আপনি মনে করেন?
সরকার ওষুধ শিল্পের আরো বিকাশের জন্য কাজ করছে। সরকার যে পার্ক স্থাপন করছে, সেটা ওষুধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অনেক সহযোগিতা করবে। এতে কাঁচামালের দাম কমবে। ওষুধের দামও কমে আসবে। এটা এখনো চালু হয়নি। এটা কার্যকর হতে আমার মনে হয় আরো ২০ থেকে ৩০ বছর সময় লাগবে। এটা যখন পুরোপুরি কার্যকর হবে, তখন আমাদের দেশে ওষুধের দাম কমবে।
সাক্ষাৎকার: বণিক বার্তা ইউটিউব চ্যানেল সৌজন্যে





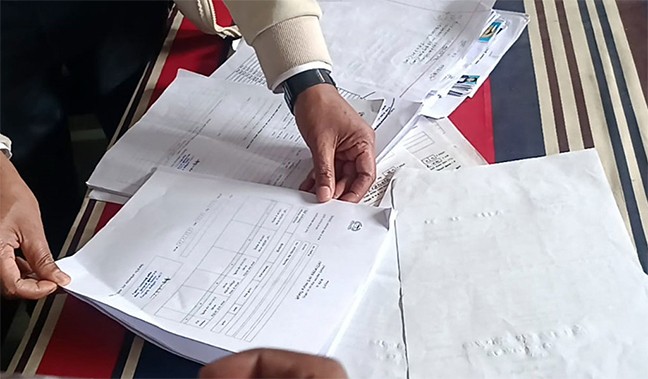

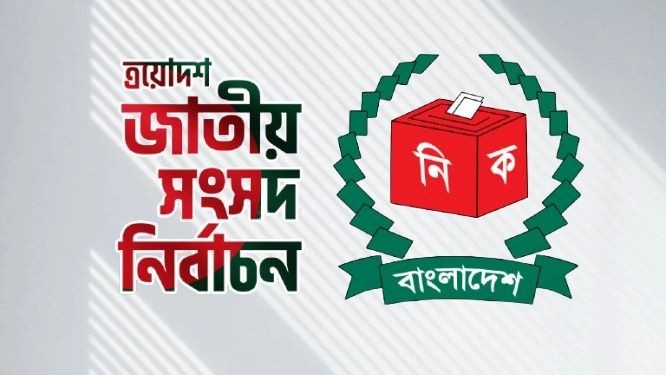


.jpg)







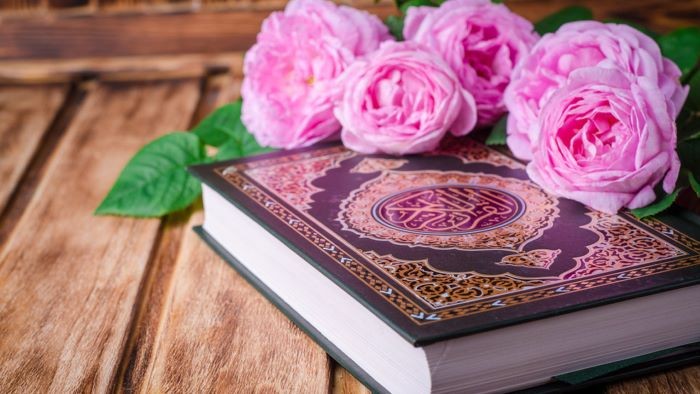

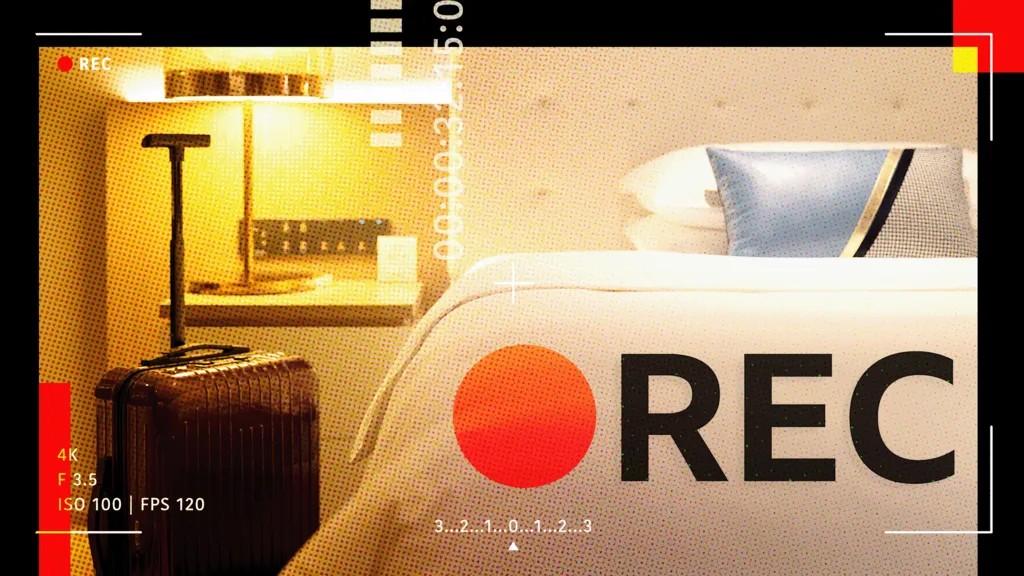


_School.jpg)








