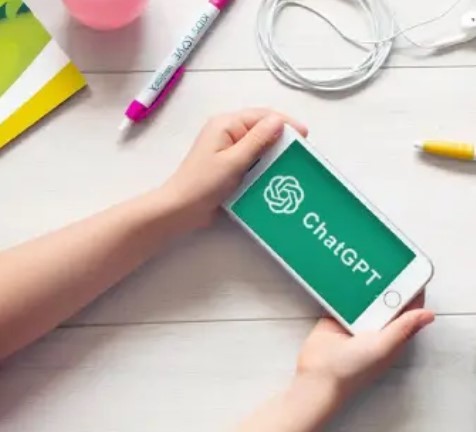মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন: প্রকৃতির গতি প্রকৃতিকে বুঝতে হলে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব জায়গায় রেখে বুঝতে হয় এবং প্রকৃতির কাছে আসতে হয়। প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের খেলা মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এক আম্ফান আর যশের তাণ্ডব দিয়ে আমরা তা আঁচ করতে পারি প্রকৃতির অবিনাশী শক্তি এখনো লুকিয়ে আছে প্রকৃতির অন্তঃস্রোতে। অন্তস্রোতে বাঁধা প্রদান করলেই সে এক গা দিয়ে যায় তখন আমাদের একটু টনক নড়াচড়া দিয়ে উঠে। প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করে, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মকে ভেঙে মানুষ নিজেদেরকে যতই সুখী করতে চেয়েছে ততোই সুখের সিঁড়ি থেকে মানুষ নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।
রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ আক্রমাণত্মক মরণোন্মুখ নখ খামছি পড়েছে চট্টগ্রামের সিআরবি'র উপর। রাষ্ট্র চরিত্র যখন পাবলিক থেকে প্রাইভেটাইজেশনের দিকে এগোয় তখন জনসাধারণের জীবন এবং জীবীকা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কর্পোরেটকোম্পানিগুলোর স্বার্থ। প্রাইভেট হাসপাতালের নামে একটা রক্তচোষা প্রতিষ্ঠাণ নির্মাণ করে মানুষের লক্ষ লক্ষ লিটার অক্সিজেন সাপ্লাইকারী শতবর্ষী গাছ কেটে ফেলে হাসপাতাল নির্মাণের পায়তারা যখণ রাষ্ট্রের কোন নিয়মনীতি না মেনে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মেঘা প্রজেক্ট চলে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমাদের রাষ্ট্র চরিত্রের মধ্যেই এমন একটা বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে যা প্রাণ প্রকৃতির ভূমিকার সাথে অসংগতিপূর্ণ।
রাষ্ট্রের অসংগতিপূর্ণ চরিত্র মাঝে মাঝে জানান দেয় আমার- তোমার জীবন স্বাভাবিক থাকবে নাকি বিপর্যস্ত হবে? আমাদের জীবন এবং সার্বিক স্বাস্থ্য প্রাণ প্রকৃতি ব্যতীত কখনো স্বাভাবিক সুস্থ থাকতে পারে না।বিজ্ঞান আমাদেরকে সচেতন করছে এই বলে যে,প্রাণ প্রকৃতি গাছ পালা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের জীবন বিলুপ্ত হওয়া অবধারিত।আধুনিক সভ্য জগতে বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে রীতিমতো বিধ্যাঙ্গুল দেখিয়ে রাষ্ট্রের কালো থাবা কাজে লাগিয়ে কর্পোরেট গাছখেকোর দল চিবিয়ে খেতে চায় সিআরবিকে। সিআরবির শতবর্ষী শির উঁচু করে দাড়িয়ে থাকা মাতৃবৃক্ষগুলো যেন তারা হিংস্র নখরে আঁচড়ে উপড়ে ফেলতে চায়।উপড়ে ফেলতে চায় শতবর্ষী গাছ গুলোর মাটিতে ভেদ করে থাকা হাজার হাজার মাইল প্রসারিত মূল,শেকড়, শাখা-প্রশাখা।
চট্টগ্রাম শহরের একমাত্র বুকভরে শ্বাস নেয়ার প্রাণকেন্দ্র বলা যায় এই সিআরবিকে। নগরের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত পেয়েছে এই স্থানটি। শহরের এমন কেউ নেই যে এই স্থানে এসে একবার হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়নি। "ইউনাইটেড হাসপাতাল পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে সিআরবিতে যে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল ও ১০০ আসনের মেডিকেল কলেজ নির্মাণের চূড়ান্ত করেছে। (তথ্য সূত্র প্রথম আলো)
প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, পরিবেশ, পাহাড় ধ্বংস করে সিআরবিতে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ নির্মাণ চট্টগ্রামবাসী চায় না। এসবের নামে শুরুতে কর্তন করা হবে গাছ, পরবর্তীতে তা বর্ধিত করে ধ্বংসযজ্ঞ চলবে। চট্টগ্রামবাসীর দাবী" যদি হাসপাতাল করতে হয় করুক। অনেক খাস জমি রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জমির পরিমাণ সাত হাজার ৭০১ একর। এর মধ্যে ২১৫ একরই বেদখল। এসবে রেলের কোন খবর নেই। তারা মেতেছে সিআরবি ধ্বংসের কাজে। নগরীর পাহাড়তলী, টাইগার পাস, খুলশী, আমবাগান, কদমতলী, আইস ফ্যাক্টরি রোড, ফয়'স লেক এলাকায় রেলের জমিতে গড়ে উঠেছে পাকা ভবন, পার্ক ও বিপণিবিতান। এর কুফল আমরা পাচ্ছি।"
৮ জুলাই জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪৮টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সামনেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়তে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে সবুজায়ন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন।আবার দেশের অভ্যন্তরে প্রাণ প্রকৃতি ধ্বংস নদী দখল হাট দখল ঘাট দখল,পাহাড় দখল, শতবর্ষী বৃক্ষ কর্তণ, বনাঞ্চল ধ্বংক দখলসহ অসংখ্য লুটপাট দুর্নীতি সমাজ রাষ্ট্রে সমান তালে চলছে।
অথচ কিছুদিন আগে পরিবেশের কথা বিবেচনায় নিয়ে ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে তার প্রতিফলণ হিসেবে কোন সময়োপযোগী গ্রাম শহর নগর বন্দর সাজানোর পরিকল্পনা নেই কোথায়ও।বরং কর্পোরেটরা সরকারকে ভাগিয়ে নিয়ে দখল করছে আমাদের প্রাণ প্রকৃতি। সুফল ভোগ করছে সমাজের উপর তলার গুটিকয়েক ব্যক্তিবর্গ কিন্তু কুফল ভোগ করছে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। ইউনাইটেড প্রাইভেট হসপিটাল সমাজের কোন শ্রেণীকে চিকিৎসা দিবে সেই খবর বাঙালি ভালোভাবে জানে।
মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য টানার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তাতে মানুষের জীবন বিষাক্ততায় পূর্ণ হয়েছে। এই পার্থক্য তৈরির সংস্কৃতি শুরু হয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে জীবিকার “উপায়” রূপে পেতে চেয়েছে মানবগোষ্ঠী। প্রকৃতি কখনো মানুষের “লক্ষ্যে” পরিণত হতে পারেনি। অথচ বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষের সাথে প্রাণীকূলের যতটুকু পার্থক্য রয়েছে তা শুধুই সংস্কৃতিগত এবং মাত্রাগত, গুণগতভাবে তেমন নয়।
একটা সময়ে বলা হত- শুধু মানুষই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণ হলো গ্যালাপ্যাগজ (Galapagos) নামক এক প্রজাতির কাঠঠোকরা পাখি গাছের ফাটল থেকে পোকামাকড় বের করার জন্য ফণীমনসা গাছের কাঁটা ব্যবহার করে। বিজ্ঞানী জেইন গুডাল (Jane Goodall) আবিস্কার করেন, তানজানিয়ার জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি জলে পূর্ণ সিক্ত হবার জন্য গাছের পাতা চিবিয়ে স্পন্জ তৈরি করে এবং পোকামাকড় ধরার উদ্দেশ্যে গাছের পাতা ছিঁড়ে সাজিয়ে রাখে।
ভাষা নিয়ে মানুষের গর্বের শেষ নেই! পরে দেখা গেল শিম্পাঞ্জি ও গরিলা মূক ও বধিরদের প্রতীকী ভাষা শিখেছে। প্রমাণ রয়েছে যে, তিমি ও ডলফিনের নিজস্ব জটিল ভাষা রয়েছে। আমাদের দেশে বাবুই পাখির তাল গাছের পাতায় সূক্ষ্ণ ঘর বোনার দৃশ্য কার না মনে পড়ে যা গোটা পৃথিবীর মাধ্যার্কষন শক্তির বিরুদ্ধে ঝড়বৃষ্টিতেও টিকে থাকে! আদিমকালে মানুষ যখন অন্যায় করা এবং অন্যায় ভোগ করার অভিজ্ঞতা প্রথম লাভ করে তখন তারা এই উপলব্ধিটাও করেছিল যে, দ্বিতীয়টি ভোগ করা ব্যতীত প্রথমটি ভোগ করা সম্ভব নয়।
তখন তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসায় উপনীত হয়েছিল, অন্যায় করা বা অন্যায় সহ্য করা কোনোটিতেই লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা ও উচ্চতর গণতন্ত্র আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, যা আইনসম্মত তা সর্বদা ন্যায়সম্মত নাও হতে পারে। অন্যায় কর্মকে ন্যায়সম্মত করা অন্যায় এবং এর ভয়াবহ দিক হচ্ছে অন্যায়কারীর শাস্তি ভোগ না করা। মানুষ এবং প্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য। এদের পার্থক্য নিরূপণে উঠেপড়ে লাগা মানেই হচ্ছে বৈচিত্র্য ধ্বংস করার পায়তারা করা।বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা মানুষ অন্য মানুষের জন্যও ভয়ংকর হতে পারে। কারণ অন্য মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন তার কাছে অসহ্য লাগে। প্রাণীর সামর্থ্য মানসিক ও শারীরিকভাবে অপরিণত বা সমপর্যায়ে নেই বলে তাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্য আচার-আচরণ করা যদি নৈতিক হয়, তাহলে আমাদের নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।
আমরা এমন এক নৈরাজ্যবাদী দেশে বসবাস করি যেখানে প্রতিটি মানুষ প্রথা প্রতিষ্ঠান দল সংগঠন রাজনীতি এবং রাষ্ট্র প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত ভক্ষন করে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে।এমনই এক বিবেকহীন রাষ্ট্রে আমরা আছি যেখানে প্রাণ প্রকৃতি গাছ পালা রক্ষার্থে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ আসতে হয়। হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত রক্ষা গাছপালা রক্ষা পায় না।। প্রকৃতিকে বাদ দিয়েছে বৈষয়িক মানুষ,পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র,একই সাথে বিভিন্ন দল মতের মতাদর্শ।
প্রতিটি গাছপালা প্রাণ-প্রকৃতি বাঁচার অধিকার পৃথিবীর মানবকূলের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ নৈতিকতার ভিত্তি যদি এই হয় যে, অন্যেরা আমার প্রতি যতক্ষণ না পর্যন্ত অপ্রীতিকর কাজ করবে আমিও সে পর্যন্ত তাদের প্রতি অপ্রীতিকর কাজ করা থেকে বিরত থাকবো। তাহলে যেকোন প্রাণীকূলের বিরুদ্ধে গাছ পালার বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর কাজ করার আমার কোন রকম যুক্তিই থাকতে পারে না। নিরীহ মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে তো নয়ই। নিরীহ ডলফিনের দল যখন খেলা করে তখন তাকে আঘাত করা অন্যায়। আবার নদীতে হাঙর যখন আমাকে আক্রমণ করবে তখন নিজেকে রক্ষার জন্য তাকে আঘাত করা আমার পক্ষে অনৈতিক নয়। যদিও সুপ্রাচীণ ধর্মগ্রন্থগুলো বিশ্বাস করে যে, “ঈশ্বরই অ-মানব প্রাণীকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করেছেন।”(জেনেসিস ১,২৯,এবং ৯,১-৩)।
আমার নিজস্ব জীবনধারণের ইচ্ছার মধ্যে যেমন দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আকুল আকাঙ্ক্ষা আছে তেমনি বিলুপ্ত হয়ে যাবো এই ভেবে ভয়ও আছে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে পোষণ করার মধ্যেই রয়েছে পরমানন্দ। আবার বেঁচে থাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আঘাতই হল বেদনা। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, মানব জাতির বাইরে যে জীবজগৎ- তারা নিজেরা বেঁচে থাকার উপলব্ধি ব্যক্ত করতে পারুক বা না-ই পারুক, সকলের সমভাবে বেঁচে থাকার সার্বজনীন অধিকারকে আমি শ্রদ্ধা করি। এটাই নৈতিক মানদণ্ড।
সকল প্রকার জীবনের প্রাণ প্রকৃতির প্রতিই শ্রদ্ধা- এই মতবাদটির সঙ্গে যাঁর নাম সম্ভবত সবচেয়ে বেশী জড়িত, তিনি হচ্ছেন আলবার্ট শোয়াইটজার (Albert Schweitzer)। “Civilization of Ethics” গ্রন্থে তিনি বলেন, “জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সযত্নে লালন করাই ভালো; জীবনকে ধ্বংস করা এবং নিবৃত্ত করাই মন্দ…..” অর্থাৎ একজন মানুষ শুধু তখনই প্রকৃতভাবে নৈতিক যখন সে সব ধরণের জীবনকে সাহায্য করার জন্য তার উপর অর্পিত দুর্বার চাপকে হাসিমুখে মেনে নিতে সক্ষম।
যখন সে নিয়মের বাইরে হলেও যেকোন প্রাণ-প্রকৃতিকে আঘাত করা পরিহার করে চলে। সে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে না ঐ প্রাণীটি তার সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য কি না? তার কাছে জীবন মানেই পবিত্র। যদিও এই পবিত্রতা ধর্মীয় মানবতাবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। এখানে পবিত্রতা মানেই সর্বত্র জীবন, অযথা হস্তক্ষেপবিহীন জীবন, অস্তিত্বশীল ইহজাগতিক জীবন।
দার্শনিক পিটার সিঙ্গার তাঁর “Applied Ethics” গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, “যে বরফ স্ফটিক সূর্য আলোতে ঝলমল করে সে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে না,কোন গাছের পাতা সে ছিঁড়ে না,কোন ফুল বিচ্ছিন্ন করে না, এবং চলার সময় কোন কীট পতঙ্গ যাতে পায়ের নিচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ন না হয়, সে দিকে সে যত্নবান। গ্রীষ্মের কোন সন্ধ্যায় সে যদি দীপালোক দ্বারা কাজ করে তাহলে বরং সে তার টেবিলের উপর ঝলমলে এবং পাখাসহ নির্জীব পতঙ্গের পর পতঙ্গ উড়ে এসে পড়া দেখার চেয়ে জানালা বন্ধ করে দূষিত বাতাস গ্রহণ করতে অধিকতর পছন্দ করে।” (অনুবাদকঃ ড. প্রদীপ কুমার রায়)
পৃথিবীতে আনন্দ বৃদ্ধি করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে; একটি হচ্ছে বর্তমানে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিদের আনন্দ বৃদ্ধি করা: অন্যটি হচ্ছে আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করবে এমন সত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আনন্দের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে যদি আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিতকারীদের হত্যা করা মন্দ হয়, তাহলে আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছে এমন সত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করাই শ্রেয়। অধিকতর সন্তানের জন্ম দিয়ে যদি আমরা আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারতাম তাহলে আমরা একাজটি ভালোভাবেই করতাম, যদিও অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক সমাজ এ কাজকে জটিল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে।
ঠিক তেমনি অধিক আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে এমনতর মানবেতর প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাও আনন্দের ব্যাপার। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুৎপাদনশীল বধির বাকপ্রতিবন্ধী বিকলাঙ্গ একটি মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে যেমন আদালতের সমস্ত আইন ঐ নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে ঠিক তেমনি উৎপাদনশীল এবং জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য রক্ষাকারী নিরীহ মানবেতর প্রাণীটি যার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি মনুষ্য জগতের কোনরকম ক্ষতির কারণ নয়, তাকে হত্যা করা কত বড় অন্যায় সেই যুক্তিকেই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী করে।
সকল জীব ও জগতের বাঁচার পরিবেশ তৈরি করে দিতে আমাদের মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তির যথেষ্ট উন্নয়ন উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। মানবেতর নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে যদি অন্য একটি মানবেতর প্রাণীর দ্বারা তার শূন্যস্থান পূরণ করা যায় বা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় এবং এই করে প্রতিস্থাপনকারী মানবেতর নিরীহ প্রাণীর জীবনের মূল্য যদি হত্যাকৃত নিরীহ মানবেতর প্রাণীর মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে আত্মসচেতনহীন মানবেতর নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করা অন্যায় নাও হতে পারে।