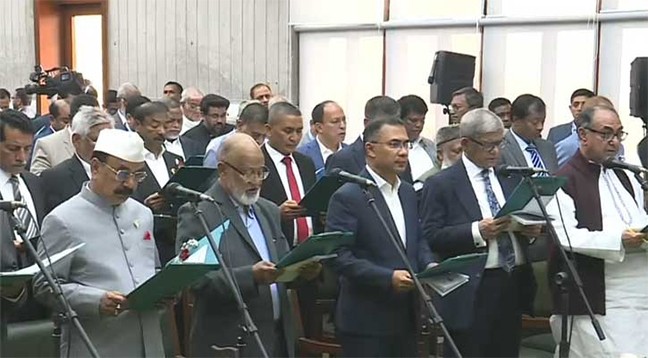ভূঁইয়া আশিক রহমান : [২] বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের জিডিপির লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা কখনো এক হয় না, কখনো এক হবেও না।
[৩] এ বছরের হিসাব শেষ হতে চললো, এখনো পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব আমরা পাইনি। সে কারণে নতুন করে বিশ^ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে [৪] আগে আমরা শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম, এখন সীমান্ত নিয়েও ভাবতে হচ্ছে, যা অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত।
[৫] ভ্যাকসিনেশনের অর্থায়নে কোনো সংকট না থাকলেও ভ্যাকসিনেশনের যোগান এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বড় সংকট
[৬] করোনার দ্বিতীয় ধাপ চলছে, তৃতীয় ধাপও হয়তো আসবে। সামনে কোরবানির ঈদ, দেশজুড়ে মানুষের যাতায়াত বাড়বে এ ধরনের পরিস্থিতিতে অর্থনীতি সচল রাখতে পারাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।
[৭] বিশ্ব ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের আগামী অর্থবছরে জিডিপি হবে ৫.১ শতাংশ, সরকার বলছে ৭.২ শতাংশ। আসলে প্রাক্কলনের হিসাবটা কারও সঙ্গে খুব একটা মিলে না। আগামী অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি গতবছর থেকে বেশি হবে, সেটি সরকার যেমন বলছে, আবার বিশ্ব ব্যাংকও বলছে। অর্থাৎ অর্থনীতি কোন দিকে যাচ্ছে সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ^ব্যাংকের মিল আছে।
[৮] অন্য বছরের তুলনায় এবার হিসাবটা একটু ভিন্ন। অন্যান্য সময় যেটা হতো শুধু প্রাক্কলনটাই ভিন্ন হতো। যে অর্থবছর পার হয়ে যাচ্ছে, সেটির আসল হিসাব-নিকাশটা একই থাকতো। পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের হিসাবটাই সকলে ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন এটা নিয়েও ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। গতবছর পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে যে হিসাব বের করেছে, অর্থাৎ ৫.২ শতাংশের সঙ্গে বিশ^ব্যাংকের মিল ছিলো না। এজন্য নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না প্রকৃত হিসাবটা আসলে কতো।
[৯] এ বছরের হিসাব শেষ হতে চললো, এখনো কিন্তু পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব আমরা পাইনি। সে কারণে নতুন করে বিশ^ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। গড় হিসাব করা হয় এ বছর কতো আগামী বছর কতো এর পার্থক্যটা হিসাব করে এ বছরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। এ বছরের হিসাবটা আগে সবার এক থাকতো। এখন ভিত্তিটাও ভিন্ন। যে ভিত্তির ওপর হিসাবটা ঠুকছেন, সে ভিত্তিটা এক নয়। যার জন্য নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বাজেটের সঙ্গে অর্থ বিভাগের যে সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেটি তো অর্থবিভাগের করা। অর্থবিভাগের তো জাতীয় আয় হিসাব-নিকাশের সক্ষমতা নেই, তাদের হিসাব রাখার কথাও নয়।
[১০] পরিসংখ্যান ব্যুরো গত একবছর ধরে যা বলছে, তা বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবের সঙ্গে মিলছে না। সেটা একটা কারণ এই ব্যবধানের। আরেকটা হলো, বিশ্ব ব্যাংক যে কম বলছে, সেটা আসলে বাংলাদেশকে নিয়ে বিস্তারিত ভেতরে কিছু বলেনি। বলা আছে, শুধু রিপোর্টের একটা অংশে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভিন্ন অর্থনীতিগুলো কতোটা ঘুরে দাঁড়াবে? ওরা বলছে যে, উন্নত দেশগুলোর রিকোভারি বেগবান হবে। তার কারণ হচ্ছে ধনী দেশগুলোতে ভ্যাকসিনেশনটা খুব দ্রুত হচ্ছে।
[১১] আগামী দুয়েক মাসের মধ্যে তাদের জনগণের বড় একটা অংশকে ভ্যাকসিনেট করে ফেলবে। যেসব দেশের ভ্যাকসিনেশন দুর্বল তাদের অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে অনেক সময় লাগবে। বাংলাদেশ তো সেসব দেশের পর্যায়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণের মাত্রা কেমন হবে সেটার ওপর নির্ভর করবে আমাদের অর্থনীতির চাকা কতোটা ঘুরবে। আগে তো আমরা শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন সীমান্ত নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। কুড়িগ্রামে করোনা পজিটিভ শতভাগ। যেটি অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত। যেখানে মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ভুগছে, সেখানে নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে করবে? এ অনিশ্চয়তাকে বিবেচনায় নিয়ে আসলে বিশ^ব্যাংক প্রতিবেদনটি করেছে বলে আমার মনে হয়।
[১২] বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে বড় যে খাত ভোক্তা ব্যয়। ভোক্তা ব্যয় কতোটা রিকোভার করছে। ওরা বলছে যে, ভোক্তা ব্যয় রিকোভারি ধীরগতির হবে। বাংলাদেশের ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া এখনো ঠিক সচল না। শুরু হয়েছে, আবার থেমেও গেছে। বাজেটে বলা হয়েছে, ৮০ শতাংশ লোকের ভ্যাকসিনেশন করা হবে। কিন্তু সেটা কবে হবেÑ ২০২১ সাল, নাকি ২০২২? সে নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই। ভ্যাকসিনেশনে আমাদের অর্থায়নে কোনো সংকট নেই। আমাদের সংকট হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের যোগান ও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
[১৩] যেসব দেশ ভ্যাকসিনেশন পর্যায়ে এগিয়ে আছে তাদেরও প্যান্ডেমিক পর্যায়ে মাথাপিছু আয় যতো ছিলো সেটা ২০২২ সালের আগে ফিরে যেতে পারবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয়ে গেছে, সবকিছু খুলে দিয়েও আমেরিকায় প্যান্ডেমিক পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ভাইরাসের অনিশ্চিয়তা রয়েছে। ভ্যাকসিনেশন পুরো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অনিশ্চয়তা কাটবে না। সে কারণেই বিশ^ব্যাংক ৫.১ শতাংশ জিডিপির কথা বলেছে। ওরা জানুয়ারিতে একটা হিসাব দিয়েছিলো অর্থবছর ২১-২২ নিয়ে, সেখান থেকে আপগ্রেড হয়েছে প্রায় দেড় শতাংশের মতো। তাতে মনে হয়, আগে তারা যতোটা নিরাশ ছিলো, এখন তারা কিছুটা আশাবাদী।
[১৪] আমরা যেহেতু ভাইরাস থাকবে কী থাকবে না, সে নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছি। এর মধ্যে এখনো লকডাউন চলছে। অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ বন্ধ। আন্তর্জাতিক ভ্রমণও চাইলে অবাধে করা যায় না। ফলে সেক্ষেত্রে প্রাক্কলনটা কতো হবে, সেটা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। করোনা পরিস্থিতিতে আমার ধারণা হচ্ছে, যতোটা পারা যায় অর্থনীতিকে সচল রাখা, সেটাই হবে বড় অর্থনীতি। সচল রাখাটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে বা আয় হারিয়ে ফেলেছে, তারা কেনাকাটা করতে পারছেন না, তাদের ক্রয়ক্ষমতা যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে তা অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখবে।
[১৫] প্রবৃদ্ধি কতো হলো না হলো, সেটা আমাদের ভাগ্যের ওপরে। করোনার দ্বিতীয় ধাপ চলছে, তৃতীয় ধাপ আসবে। সামনে কোরবানির ঈদ, লোক সমাগম বাড়বেÑ এ ধরনের পরিস্থিতিতে অর্থনীতি সচল রাখতে পারাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। যারা জীবিকা সংকটে আছে, তাদের জীবিকার যোগান দিতে পারাইটাই হবে বড় সফলতা।
[১৬] এবারের বাজেটকে মোটা দাগে ব্যবসাবান্ধব বাজেট বলে ফেলছি। কিন্তু এটা তো সব ধরনের ব্যবসার জন্য নয়। সবগুলো বড় ব্যবসা এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে মূলধনের ব্যবসা। এগুলোর কোনোটাই শ্রমনিবিড় ব্যবসা নয়। যেটা হবে বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে, তাদের কর খরচ কমবে। কিন্তু এর ফলে তারা কতোটুকু উৎপাদন বাড়াবে। উৎপাদন বাড়ালে কর্মসংস্থান কতোটা বাড়বে? কিছু হয়তো বাড়বে। শ্রমনিবিড় ব্যবসা হচ্ছে হচ্ছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মতো ব্যবসা। তাদের জন্য তো তেমন কিছু নেই। অনুলিখন : তানিমা শিউলি।