
শিবলী হাসান : মিয়ানমারের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হবে না মর্মে উল্লেখ করে মিন অং হ্লাং বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন বলে ঘোষণা দেন, একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণভাবে ছড়িয়ে-ছিটেয়ে থাকা নাগরিকদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলমান থাকবে বলে জানানো হয়। সেনাপ্রধানের এমন বক্তব্যে নতুন করে অনেকেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আশা দেখছেন। যদিও রোহিঙ্গাবিরোধী সেন্টিমেন্ট নিয়ে তাদের ওপর গণহত্যা চালানো সেনাবাহিনী সেটা বাস্তবতায় রূপ দেবে কি না তা সময়ই বলে দেবে! মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাস মানেই সেনা আধিপত্যের ইতিহাস। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ৫০ বছরের বেশি সময় থেকেছে সেনাশাসনের অধীনে। ক্ষণিক গণতন্ত্রের আড়ালে সামরিক ক্যু হয়েছে বারবার। তাই গত ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে যে সামরিক অভ্যুত্থান হলো, তাতে বিচলিত হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ নেই, এটা তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু এবারের সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে আলাদা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলো বাংলাদেশে অবস্থান করা বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা, যাদের প্রত্যাবাসনের জন্য দীর্ঘ সময় থেকে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তাই এবারের অভ্যুত্থান ঠিক কী কারণে এবং এর পরবর্তী ফলাফল কী হতে পারে, তা নিয়ে চারদিকে নানা জল্পনা-কল্পনা চলমান। নানামুখী আলোচনায় চীন-ভারতের অবস্থান এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রশ্নে লাভ-ক্ষতির হিসাবটাও ঘুরেফিরে আসছে।
গত বছরের নভেম্বর মাসে মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যেখানে ৩২২টি আসনই যথেষ্ট, সেখানে দলটি ৩৪৬টি আসন পায়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ মিলিয়ে ১ হাজার ১১৭ আসনের মধ্যে এনএলডি পায় ৯২০টি। যার ফলে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের একক কর্তৃত্ব চলে যায় সু চির হাতে। এ থেকেই শুরু সেনা-সু চি দ্বন্দ্ব। কেননা সেনাবাহিনীর সমর্থক দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) মাত্র ৭১ আসন পায়। অথচ ২০১৫ সালের নির্বাচনেও যেখানে ইউএসডিপি পেয়েছিল ১১৭ আসন। আর এত কম আসন নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশে ন্যূনতম সেনা আধিক্যতাও যে এবার থাকছে না, তা স্পষ্টতই বুঝতে পারে সেনাবাহিনী। অথচ মিয়ানমারের সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, ইউএসডিপি একটু বেশি আসন পেলে অং সান সু চির সঙ্গে দর-কষাকষি করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন। কিন্তু ফলাফল যে এত খারাপ করবে তাদের দল, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি। ফলে শুরু হয় নতুন রাজনীতি, নতুন দর-কষাকষি। এই সম্পূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে নজর ছিলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এবং তারা স্পষ্টত বুঝতে পারছিলো, আবারো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে মিয়ানমারে। গত কদিন ধরেই সামরিক ক্যু হবে বলে অনেক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আশঙ্কা প্রকাশ করছিলো। অবশেষে তা-ই হলো।
এবারের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে কি শুধুই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, নাকি ভিন্ন কিছুও রয়েছে! এই প্রশ্নের উত্তরে গেলে সেখানেও আসবে রোহিঙ্গা গণহত্যা! আমরা সবাই জানি, রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে গাম্বিয়া। এই মামলার শুনানিতে এসে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি তখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সেনাবাহিনীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। গোটা বিশ্ব যে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছে, সু চি তা একবাক্যে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এবারের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সু চির দল জেতার পর ভবিষ্যতে একই সমর্থন অব্যাহত থাকবে কি না, সে শঙ্কা দেখা দিয়েছে সেনাবাহিনীর মাঝে। কেননা জেনারেল মিন অং হ্লেইং আগামী বছর অবসরে যাওয়ার কথা, আর অবসরে গেলে তিনি ও অন্য জেনারেলদের রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে চলমান আন্তর্জাতিক বিচারে সু চি আর সুরক্ষা না-ও দিতে পারেন। ভবিষ্যতে মিয়ানমারের বেসামরিক সরকার পশ্চিমা শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে যদি অপরাধী জেনারেলদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে দেয়, তবে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তাদের। কেননা, ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত রোহিঙ্গা গণহত্যার জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে দায়ী বলে উল্লেখ করেন। এই আশঙ্কা থেকেই এবারের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।
সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে, তা আলাদা গুরুত্ব পায়। যেহেতু ঘটনা মিয়ানমারে, তাই জিও স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতিতে চীন ও ভারতের অবস্থান এখানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সহজ ভাষায় যদি বলি তবে এই অভ্যুত্থানের লাভ-ক্ষতির হিসাব অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বিবৃতিতে ফুটে ওঠে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় চীন বলেছে, ‘মিয়ানমারে যা ঘটেছে তা লক্ষ করেছি আমরা, আর পরিস্থিতি আরো বোঝার প্রক্রিয়াতে রয়েছি। চীন মিয়ানমারের এক বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী। আমরা আশা করছি, মিয়ানমারের সব পক্ষ সংবিধান ও আইনি কাঠামোর অধীনে যথাযথভাবে তাদের পার্থক্যগুলো সামাল দিতে পারবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।’ এই বক্তব্য কিন্তু চীনের সেনাঘেঁষা নীতিকে আরেকবার প্রমাণিত করলো। আবার এটাও সত্য, চীন যেহেতু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিয়ানমারকে রক্ষা করে আসছে, তাই এবারের উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও মিয়ানমার সেনাবাহিনী পশ্চিমাদের খড়্গ থেকে বাঁচতে চীনের ছায়াতলে আসবে। আর চীন যেহেতু বঙ্গোপসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মরিয়া, তাই মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে এ ক্ষেত্রে নিজেদের কাছে নির্ভরশীল করে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা নেবে। অপরদিকে ভারত মিয়ানমারের অবস্থায় উদ্বেগ জানিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কথা বলেছে। ভারত এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, ‘মিয়ানমারের গণতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়ে সব সময় সমর্থন জানিয়ে আসছে ভারত। আমরা বিশ্বাস করি, আইন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’ সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দিয়ে চীন এই অঞ্চলে শক্তিশালী হলে ভারতের জন্য তা নিশ্চয়ই অশ্বস্তির এবং উদ্বেগের। তবে এই উদ্বেগ শুধু যে ভারতের তা কিন্তু না। দক্ষিণ চীন সাগর পরিস্থিতি এতে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এ নিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে এই সমস্যার ফল আমাদেরও ভোগ করতে হবে।
ইষৎ সংক্ষেপিত। পুরো লেখাটি পড়ুন সারাক্ষণ ডটকমে। লেখক: ব্লগার ও নারী অধিকারকর্মী

















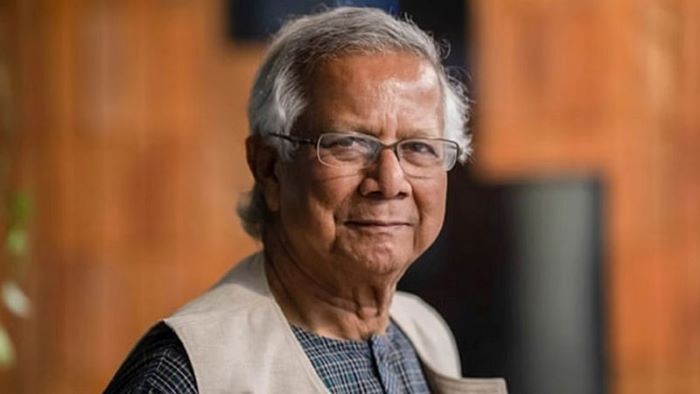

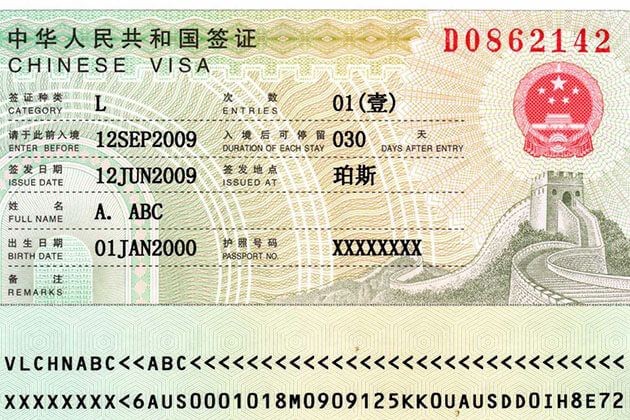



_School.jpg)






