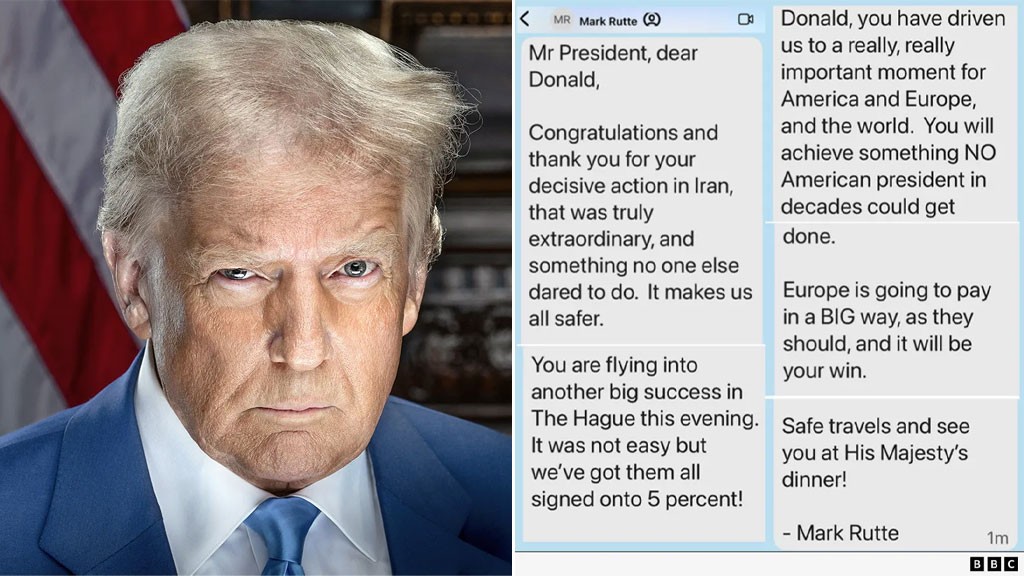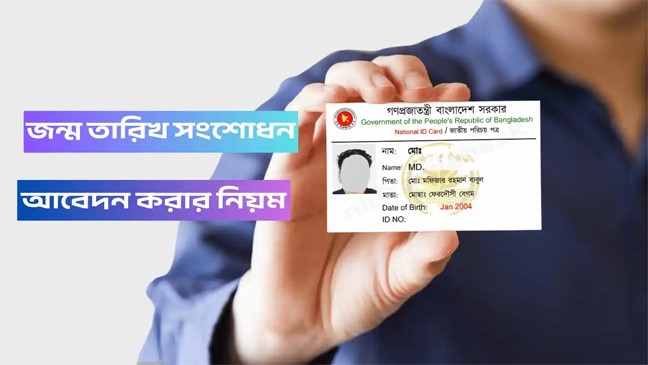গরীব নেওয়াজ: ভাষাতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর ভাষা সমূহের শব্দকোষ ও ব্যাকরণের বিশেষ সম্পর্ক কিংবা আদিরূপের মধ্যে যে বিশেষ সাদৃশ্য বা মিল দেখতে পাওয়া যায়—তা পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করেছেন যে, পৃথিবীর ভাষাসমূহ কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। এ আদি উৎসবগুলোকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ বলে। পৃথিবীর ভাষাসমূহকে ১২টি বংশে বা গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ইন্দো-ইউরোপীয়, সেমীয়-হামীয়, বান্টু, ফিন্নো-উর্গীয় বা উরালীয়, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, ককেশীয়, দ্রাবিড় , অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশীয়, এস্কিমো এবং আমেরিকার আদিম ভাষাগুলো। অবশ্য কারও-কারও বিশ্লেষণে ভাষা বংশের সংখ্যার ভিন্ন-ভিন্ন রকম হিসাবও পাওয়া যায়। কারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এ ১২টি ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এ ভাষাবংশ হতেই প্রাচীন কালের সমৃদ্ধ সংস্কৃত,
গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। আর ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, রুশ, বাংলা, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি আধুনিক বিশ্বের প্রধানতম ভাষাগুলো এরই বংশজাত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্ব হতে পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকার কারণে মূল ভাষা হতে বিশ্লিষ্ট হয়ে ১০টি প্রাচীন ভাষার উদ্ভব হয়।
যাদের ‘শতম’ ও ‘কেন্তুম’ নামে দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। শতম গুচ্ছের ভাষা হচ্ছে : ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাভিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয় শাখা। আর কেন্তুম গুচ্ছের ভাষা হচ্ছে : গ্রিক, ইটালিক বা লাতিন, কেলটিক, টিউটনিক বা জার্মানিক, তোখারীয় ও হিত্তীয় শাখা। শতম গুচ্ছের ইন্দো-ইরানীয় শাখা পরবর্তীকালে দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে একটি যায় ইরানে, অন্যটি আসে ভারতীয় উপমহাদেশে। এ দ্বিতীয় শাখাটিকেই বলে ভারতীয় আর্য ভাষা। ভারতীয় আর্য ভাষার সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে তিনটি স্তর বা যুগে ভাগ করা হয়েছে। যথা [১] প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, [২] মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা, [৩] নব্য ভারতীয় আর্য।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বৈদিক : ভাষাপ্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ হতে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল সাহিত্যিক ও কথ্য। বৈদিক ভাষা হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ। একে ছান্দোশ ভাষাও বলা হয়। এ সাহিত্যিক ভাষার আবার দুটি রূপ ছিল। একটি প্রাচীনতর, যেটাতে ধর্মসাহিত্য ঋগে¦দ রচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ আধুনিক বিশেষজ্ঞই এ আদি বেদ ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব এগারো কি দশ শতকে প্রণীত হয় বলে নির্দেশ করেছেন। এটা হলো সে সময় যখন ঋগ্বেদের প্রাচীন স্ত্রোত্রগুলো প্রথম রচিত ও সংগৃহীত হয়। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী পুঁথিগুলো অর্থাৎ পরবর্তী সংহিতা, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব আট থেকে ছয় শতকের মধ্যে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের লিখিত প্রবন্ধ সংকলনের বিশ্লেষণে জানা যায় যে, ঋগে¦দের নানা সূক্ত একদা রচিত হয়েছিল একালের উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে। কিছু-কিছু পণ্ডিত আরও সুনির্দিষ্ট করে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলাকে নির্দেশ করেছেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ঋকবেদীয় আর্য ভাষা ছাড়াও আর্য ভাষার আরও কিছু রূপ ছিল যা সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।
সংস্কৃত ভাষা ও পাণিনি : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অপেক্ষাকৃত নবীনতর রূপটি হচ্ছে, পাণিনি অনুশাসিত সংস্কৃত ভাষা। একসময় সাধারণ মানুষের কাছে বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় এ ভাষা নানাভাবে বিকৃত হচ্ছিল। স্থানীয় ভাষার সংমিশ্রণে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে। যুগগত পরিবর্তনকে বিকৃতি মনে করে পাণিনি ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে ভাষার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভাষার স্বাভাবিক নিয়মগুলোকে আবিষ্কার ও সূত্রবদ্ধ করেন। এভাবে সূত্রবদ্ধ করে পাণিনি ভাষার ভেতরকার কাঠামোটি সকলের সামনে হাজির করেছেন এবং তাঁর উত্তরকালের জন্য একটি মানভাষা সৃষ্টি করেন। সংস্কারের মাধ্যমে সৃষ্ট বলেই একে সংস্কৃত বলা হয়েছে যার অর্থ পরিশীলিত ও শুদ্ধ।
অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ : পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করেন তার নাম অষ্টাধ্যায়ী। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ায় এ নামকরণ। অষ্টাধ্যায়ী সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। অনেক ভুল ধারণা রয়েছে এ ব্যাকরণ সম্পর্কে। এ গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোটামুটি ৩৯৮০টিযার রচয়িতা পাণিনি। ১৪টি মাহেশ্বর-সূত্র ধরলে সূত্রসংখ্যা ৩৯৯৪টি। এ ১৪টি সূত্র পাণিনির আগে থেকেই ছিল। ‘অথ শব্দানুশাসনম্’ এ প্রারম্ভিক উক্তিটি ধরলে সংখ্যাটি হয় ৩৯৯৫। কয়েক ‘শ বছর পর কাত্যায়ন এতে কিছু সংযুক্ত করেন। পাণিনি যেখানে যা কিছু লক্ষ করেননি, অথবা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি, এবং এ সময়ের মধ্যে ভাষার যে পরিবর্তন হয়, সেসব আপডেট করে কাত্যায়ন তা একেকটি পাণিনি সূত্রের অধীনে সংযোজন করেছিলেন। এ সংযোজনগুলোকে বলে ‘বার্ত্তিক’। বলা বাহুল্য, বার্ত্তিক যুক্ত হয়েছে প্রসঙ্গের প্রয়োজন অনুসারে, অনেক পাণিনি সূত্রের জন্য কোনো বার্ত্তিক প্রয়োজন হয়নি। কাত্যায়নের পর খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি যখন অষ্টাধ্যায়ীর ওপর মহাভাষ্য রচনা করেন তখন কাত্যায়নের বার্ত্তিকগুলো তাতে অন্তর্ভূক্ত হয়। কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি কেউই পুরো অষ্টাধ্যায়ী আলোচনা করেননি।
সে কাজটি করেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বামন ও জয়দিত্য, তাঁদের গ্রন্থের নাম ‘কাশিকাবৃত্তি’। এ গ্রন্থই অতি সরল সংস্কৃত গদ্যে পাণিনির প্রতিপাদ্য বস্তু বিশ্লেষণ করে উদাহরণ-সহ সমগ্র অষ্টাধ্যায়ী স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে। পাণিনি ব্যাকরণ বুঝতে হলে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। কাশিকাবৃত্তিতে কাত্যায়নের বার্ত্তিকগুলো উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে। পাণিনি দিয়েছিলেন ‘সূত্র’ [aphorism, formula, theorem], ‘বার্ত্তিক’ হলো notes, ‘ভাষ্য’ হলো commentar, এবং ‘বৃত্তি’ হলো সূত্রের উদাহরণযুক্ত paraphrase. এ হলো সাদা কথায় পাণিনি সূত্র, কাত্যায়নের বার্ত্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং জয়দিত্য-বামনের ‘কাশিকাবৃত্তি’র মধ্যকার সম্পর্ক। পাণিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। একমাত্র তাঁর ব্যাকরণই কালের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি হলো এককালিক বর্ণনামূলক [discriptive]। তিনি শুধু প্রাচীন ভারতের নয়, পৃথিবীর প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। পাণিনির আবির্ভাবকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। কারও মতে ২৪০০, কারও মতে ৫০০, কারও মতে ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার ও অন্যদের মতামত অনুসারে মোটামুটিভাবে বলা যায়, পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পালি ভাষার ব্যবহার ও রামায়ণ রচনার সময় হিসাবে নিলে মনে হয় পাণিনির সময়কাল আরও এক-দুই ‘শ বছর আগের হবে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সাত বা আট শতক হবে। জানা যায়, একসময় উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে নাটোর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পাণিনি চর্চা হতো।
ব্রিটিশ আমলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ড. অফধস কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধান রিপোর্টে এ সম্পর্কে জানা যায়। এরজন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দেও ৩৮টি পাঠশালা ছিল [ছাত্র সংখ্যা ৩৯২]। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠশালার সংখ্যা কমে ২৯টি হয় [ছাত্র সংখ্যা ২৩২]। একসময় পাণিনি চর্চা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। Devadatta Joardar যার চেয়ে আর কারও অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ এবং বাংলা ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বেশি পাণ্ডিত্য আছে বলে আমার মনে হয় না, তিনি এসব তথ্য দিয়ে বলেছেন, পাণিনি চর্চার শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ১২০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। এতক্ষণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মূল রূপ বৈদিক ভাষা এবং তার সংস্কারকৃত রূপ ‘সংস্কৃত ভাষা’এবং পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। ফেসবুকে ১৮-৩-২৪ প্রকাশিত হয়েছে।