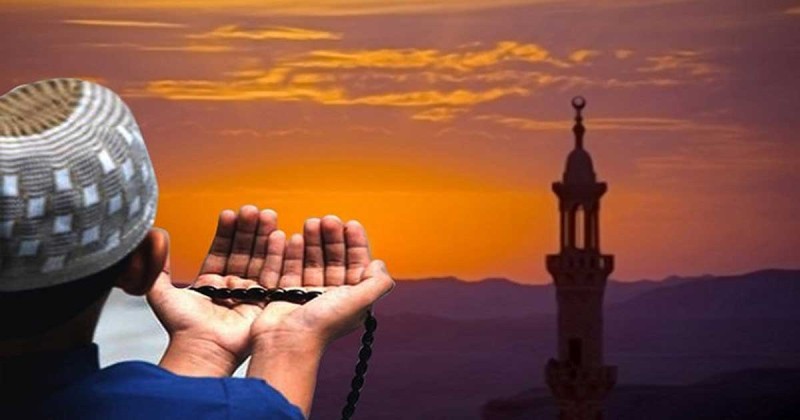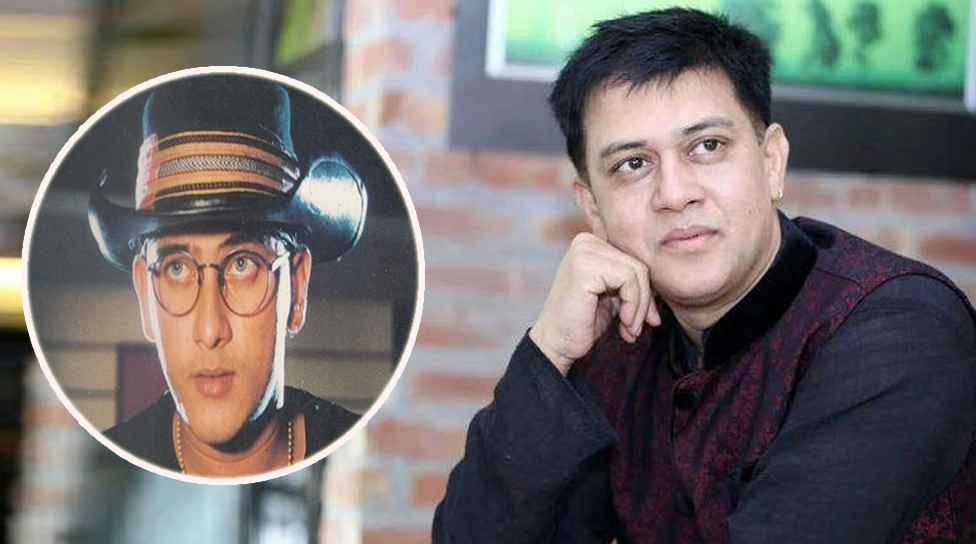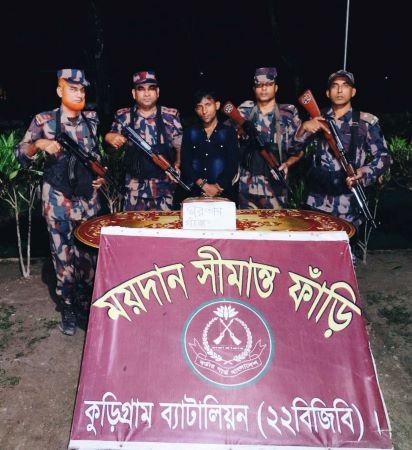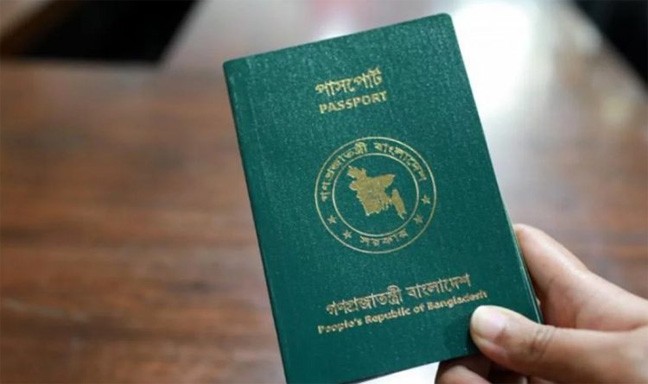চট্টগ্রাম বন্দরকে দুর্নীতিমুক্ত করার পাশাপাশি দক্ষতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে দেশে ব্যবসার পরিবেশের উন্নতির মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং আমদানি-রপ্তানি সহজীকরণ করার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। টিবিএসকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাতকারে ডিফেন্স ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন এবং হালাল অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া, চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে অগ্রগতিসহ দেশে ব্যবসা-বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে পরিকল্পনা ও অগ্রগতির তথ্য উঠে এসেছে এতে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন টিবিএস এর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান।
দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের কনটেইনার টার্মিনালে পরিচালনার জন্য বিদেশি অপারেটর নিয়োগ নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে? এরপরঅ বিদেশি অপারেটরদের নিয়োগের উদ্দেশ্য কী?
আশিক চৌধুরী: বিদেশি অপারেটর নিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো মূল লক্ষ্য হলো একটি দুর্নীতিমুক্ত এবং উচ্চ কার্যক্ষমতা সম্পন্ন লজিস্টিক সিস্টেম তৈরি করা। গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হলে এন্টি-করাপশন নিশ্চিত হবে এবং সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। বিদেশি অপারেটরের মাধ্যমে পোর্ট পরিচালনার হলে বাংলাদেশি কর্মী এবং ম্যানেজমেন্ট টিম দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
আমাদের ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন অভিযোগ করে আসছিলেন যে, পোর্টে ব্যাপক দুর্নীতির মুখে পড়েন তারা। আর একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অপারেটর নিয়ে আসা হলে তা দুর্নীতি রোধে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ বিশ্বমানের অপারেটরের জন্য সুনাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এখানে এক টাকা এদিক-ওদিক করার কথা ভাববে না। ফলে অনৈতিক প্রক্রিয়ার সুযোগ খুব কম থাকবে। আমার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এন্টি-করাপশন। বিশ্বমানের অপারেটর আনার মাধ্যমে দুর্নীতিপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ করা সম্ভব হবে।
বিশ্বমানের একটি বন্দর ছাড়া বাংলাদেশ উৎপাদন-হাব হতে পারবে না। আমাদের বৈশ্বিক র্যাঙ্কিং এখনো কম, কারণ বন্দর পরিচালনায় আমাদের অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্ব অভাব রয়েছে। আমরা এমন অপারেটর চাই যারা আধুনিক উপকরণ ও অনুশীলন দিয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন বের করতে পারবে। বিদেশি অপারেটররা কিন্তু পোর্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে না। তারা শুধু অপারেট করবে, পোর্ট আমাদের মালিকানাতেই থাকবে।
কেন আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার (যৌথ উদ্যোগ) করছি না, মানে পুরোপুরি বিদেশি প্রতিষ্ঠান কেন?
এটি পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্প। পিপিপি কাঠামোর অধীনে জয়েন্ট ভেঞ্চার করা সম্ভব। যেমন নেদারল্যান্ডসের এপিএম-এর সঙ্গে পতেঙ্গার লালদিয়া কন্টেনার টার্মিনালের প্রজেক্টটি একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার। সেখানে একজন লোকাল অপারেটর আছেন, যিনি মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডার।
তবে দক্ষতা হস্তান্তর মালিকানার মধ্য দিয়ে নয়, ব্যবস্থাপনায় হয়। এপিএম বাংলাদেশে অপারেট করলে সেখানে ৫,০০০ মানুষ কাজ করবে, তার মধ্যে হয়তো মাত্র পাঁচজন বিদেশী থাকবে। বাকি ৪,৯৯৫ জন বাংলাদেশী। তারা পোর্ট অপারেট করতে শিখবে। আমাদের লেবারও শিখবে, ম্যানেজমেন্ট টিমও শিখবে। হয়তো এই ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে কিছু লোককে এপিএম রটারডাম বা ক্রোয়েশিয়ার পোর্টে (প্রশিক্ষণের জন্য) পাঠানো হবে। ১০ বছর পরে হয়তো, তারা নিজেই অপারেশন পরিচালনা করতে পারবে। ফলে মূল প্রশ্নটা মালিকানার নয়, মূল প্রশ্ন হচ্ছে আমরা শিখছি কি-না? জয়েন্ট ভেঞ্চার না হলেও শেখার সুযোগ থাকবে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
দেশি উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ অভিযোগ করেন বিডা শুধু বিদেশি বিনিয়োগকারীর জন্য কাজ করছে। এই মন্তব্যে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?
এফডিআই কম হলে বিডা খুব খারাপ, এফডিআই বেশি হলে বিডা দারুন কাজ করছে–- এই মানদন্ডে বিডাকে মাপা হয়। সেখান থেকেই সমস্যাটা শুরু। এ কারণে মনে হয় আমরা মনে হয় শুধু এফডিআই- এর পেছনে দৌড়াচ্ছি।
এই বছরের শুরুতে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে ৩২টা পয়েন্ট চিহ্নিত করে- আমরা সেগুলা সমাধান করার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক বছরে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড–এনবিআরের সাথে অনেক কাজ করেছি। এনবিআর নিয়ে ফরেন ইনভেস্টরদের চেয়ে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ অনেক বেশি ছিল। তাদের অনেকগুলো ইস্যু আমরা রিজলভ করার চেষ্টা করেছি। অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর বলে একটা জিনিস চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা পার্শিয়াল বন্ডেড ওয়ারহাউজিং চালু করেছি। এই শেষোক্তটির সুবিধা বাংলাদেশের এসএমইগুলো পাবে। এটা তো আসলে বিদেশি কোম্পানিরা অতোটা পাবে না। বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি করতে আমরা খুব ক্যাটাগরিক্যালি চিন্তা করেছি।
তাই বিডা সবসময় বিদেশিদের জন্য কাজ করছে—এটা সঠিক নয়। আমরা নিয়মিত দেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য কাজ করি।
বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে? তিনটি মূল পয়েন্ট কী?
প্রথমত, বাংলাদেশের আছে বর্ধিত দেশীয় বাজার। বিভিন্ন বিদেশি স্টাডিতে আসছে যে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম ভোক্তাবাজার হবে, যা অনেক বিদেশি সংস্থার জন্য আকর্ষণীয়।
দ্বিতীয়ত, আমাদের তরুণ এবং প্রশিক্ষণযোগ্য জনশক্তি দীর্ঘমেয়াদি কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।
তৃতীয়ত, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান আকর্ষনীয়। এখান থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে ২০০–২৫০ কোটি মানুষের বাজারে পৌঁছানো সম্ভব, যা বড় এক লজিস্টিক সুবিধা দেয়।
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এশিয়া হবে বিশ্বের গ্রোথ ইঞ্জিন। এসব পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আমাদের গল্পটি খুব ভালোভাবে সাজানো সম্ভব হলে সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার কোনো শেষ নেই। এটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং বিনিয়োগকারীদের সেই বিশ্বাস দিতে হবে যে, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো রাখব।
একটি 'বিশেষায়িত ডিফেন্স ইকোনমিক জোন' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এবিষয়ে বিডা, বেজা কী কাজ করছে; সেখানে কোন কোন দেশ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে?
এটা বেজার প্রকল্প এবং ব্যক্তিগতভাবে আমারও খুব প্যাশনের (আগ্রহের)। বেজা তিনটি স্পেশাল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে।
এরমধ্যে প্রথমটা হচ্ছে- ফ্রি ট্রেড জোন (মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল) প্রতিষ্ঠা। এজন্য একটি ন্যাশনাল কমিটি করেছি। তারা একটি প্রতিবেদন জমাও দিয়েছে, খুব দ্রুত আমরা সেই রিপোর্ট উপদেষ্টা পরিষদে উত্থাপন করব। জোনটি কোথায় করা হবে, সেজন্য আমরা একটি জায়গা ঠিক করেছি। এটি অনেক বড় একটি ইস্যু হবে। কারণ আমাদের দুবাই, সিঙ্গাপুরের মতো ফ্রি ট্রেড জোন তৈরি করতে হবে। যেসব বিদেশি কোম্পানি পিউরলি এক্সপোর্ট-ওরিয়েন্টেড ফোকাস, তারা আসলে আমাদের জটিল কাস্টমস সিস্টেমের মধ্যে অপারেট করতে চান না।
দ্বিতীয়টি হচ্ছে, একটি হালাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। এটি নিয়ে আমরা মালেশিয়ার সরকারের সঙ্গে দেখা করব, তাদের সহযোগিতা চাব।
আর তৃতীয়টি হচ্ছে, বিশেষায়িত ডিফেন্স ইকোনমিক জোন। এটি আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর একটি ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে, বাণিজ্যিক যুক্তি আছে। আমার ফোকাসটা আসলে বাণিজ্যিক। এটা নিয়ে আমরা পলিসি লেভেলে কাজ করছি। পলিসি চূড়ান্ত হলে নির্বাচনের পরে আগামী সরকার জোনটি ঘোষণা করবে। জোনে কোন ধরনের ব্যবসা হবে, কোন দেশের সাথে তারা সহযোগিতা করবে, সেটা তখন সিদ্ধান্ত নেবে।
বেশকিছু বন্ধুপ্রতীম দেশ আছে যারা আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরা এখনো পুরোপুরি ঠিক করিনি যে, এক দেশের সঙ্গে করব—নাকি একাধিক দেশের সঙ্গে একযোগে করব। তবে আমাদের একটি শর্টলিস্ট আছে, বেশ কয়েকটি দেশের আমাদের কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে হয়তো আমরা কিছু টেকনিক্যাল সাপোর্ট নেব। এরপরে অবশ্যই প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি গড়ে তোলা হবে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ সরকার এই ব্যাপারে কী করবে? আমার দুইটি উত্তর আছে। প্রথমটি, আমি জেনুইনলি মনে করি যে জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট একটি সেকেন্ডারি ইস্যু। যে ক্ষমতায় আসবে, তার জন্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল সিকিউরিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুখের খবর হচ্ছে, এটা নিয়ে আমি বড় দলগুলো সবার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। এখন পর্যন্ত তাদের ফিডব্যাক খুবই পজিটিভ।
চীনের সহযোগিতায় একটি ড্রোন কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। এবিষয়ে পরাশক্তিগুলোর দিক থেকে আমাদের কোন ধরণের সংকটে পডার আশঙ্কা আছে কি-না?
একদমই না। আমরা তো কোন ধরণের নিউক্লিয়ার পাওয়ার হওয়ার চেষ্টা করছি না অথবা কোনো আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছি না। আমি মনে করি না কিছু ড্রোন উৎপাদন করা কোনো রিয়েকশন ট্রিগার করবে।
ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশ একটি নিরপেক্ষ অবস্থান রেখেছে — পূর্ব বা পশ্চিম উভয়ের দিকে ঝোঁকেনি। সেই ভারসাম্য আগামী দিনেও বজায় থাকবে। আমরা সবার সঙ্গে কাজ করতে রাজি। যেটা অংশীদার আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, আমরা তাদের সঙ্গে থাকব।
সমালোচনা সত্ত্বেও সরকার কেন ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনালকে স্থানীয়ভাবে নিকোটিন পাউচ উৎপাদনের অনুমোদন দিচ্ছে?
আইন বলছে, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ বৈধ ব্যবসা। যারা বলছেন এই অনুমোদন দেওয়া উচিত ছিল না— তাঁরা অফকোর্স নিজেদের বিবেক থেকে বলছেন, এবং তাদের বলার অধিকার আছে। কিন্তু সরকারের একটি নীতি, একটি ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, এবং এটি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যদি আমি ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করি, এবং প্রতিটি নীতিনির্ধারক একইভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সরকার যেভাবে কার্যকর হওয়া উচিত— সে রূপে আর কাজ করবে না।
বিনিয়োগে প্রধান বাধাগুলো কী এবং সেই বাধা দূর করতে আপনারা কী করছেন?
বিনিয়োগ বাধার তো শেষ নেই—বিরাট একটা লিস্ট। বাংলাদেশে ব্যবসা করা আসলে খুব জটিল, তবুও এখানে উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগকারীরা যেসব সমস্যার কথা জানাচ্ছেন, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। আমরা যে ৩২টি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলাম, তার মধ্যে ২১টা সমাধান করেছি। বাকিগুলো নির্বাচনের আগে শেষ করার চেষ্টা করছি।
একটা উদাহরণ দেই, আমি বিডা'য় যোগ দেওয়ার প্রথম সাত দিনের মধ্যেই ইয়াং ওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এসে বলেছিলেন, 'আমার দুইটা ফ্যাক্টরি—একটা ভিয়েতনামে, একটা চট্টগ্রামে। কিন্তু আমি অর্ডারটা আগে ভিয়েতনামেই দিই, কারণ ভিয়েতনাম থেকে পণ্য ইউরোপে পৌঁছাতে যত সময় লাগে, বাংলাদেশ থেকে যেতে তার চেয়ে বেশি সময় লাগে। বন্দর উন্নত না করলে এক্সপোর্ট ইকোনমি ঠিক হবে না।' এই বিষয়টায় আমরা অনেক মনোযোগ দিচ্ছি।
ব্যবসায়ীদের আরেকটি বড় উদ্বেগের জায়গা হলো অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। তাঁরা সবাই বললেন, এতগুলো সংস্থা, এত মন্ত্রণালয়— ব্যবসা শুরু করতে একটা জায়গায় গিয়ে এত দপ্তরে ঘুরতে হয়, খুব কনফিউজিং ব্যাপার।
তাই আমরা ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন সেবাগুলোকে একীভূত করছি। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস—এই সব সংস্থার কর্মকর্তারা বিডার ভবনে বসেন, যাতে বিনিয়োগকারী আসলে অন্তত প্রথম ধাপে এক জায়গাতেই সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন।
আমার মনে হয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি আর ২০২৬ সালের জানুয়ারি—এই দুই সময় তুলনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ বা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের মাপকাঠিতে, আমরা সম্ভবত ভালো মার্ক পাব।
সাম্প্রতিক সময়ে দেশে একটি বিনিয়োগ সম্মেলন হয়েছে। সেখানে অংশ নেওয়া কিছু দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেখান থেকে কেমন বিনিয়োগ এসেছে?
আমরা সেখান থেকে বিদেশি বিনিয়োগের একটা পাইপলাইন তৈরি করেছিলাম। আমাদের যেসব আরএম (রিলেশনশিপ ম্যানেজার) আছেন, তাদের মাধ্যমে আমরা পুরো পাইপলাইনের সাইজ রাফলি ১.৮ বিলিয়ন ডলার হিসেবে নির্ধারণ করেছিলাম। সেই পাইপলাইনের মধ্যে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার আমরা আশা করছি ম্যাটেরিয়ালাইজ (বাস্তবায়িত) হবে।
গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে, সাধারণত বিনিয়োগ পাইপলাইনে বাস্তবায়নের রেশিও থাকে ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। আমাদেরটা এখন প্রায় ১৬ শতাংশের মতো, যা নট এ ব্যাড মেটেরিয়ালাইজেশন রেট। আমরা আশা করছি, এই নাম্বারটা আমরা ল্যান্ড করাতে পারব—শুধুমাত্র এই কনফারেন্স থেকেই। আমার মনে হয়, সম্মেলনটি আমাদের দেশের জন্য একটি চমৎকার ফলাফল দিয়েছে।
জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নিয়ে জানতে চাই। বিশেষ করে চায়নিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল -এর কাজ অনেকদিন ধরেই ঝুলে আছে। এই বিষয়ে অগ্রগতির পরিকল্পনাটা কী?
চাইনিজ ইকোনমিক জোন আমাদের প্রায়োরিটি প্রজেক্ট। আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি, চীনারা যেহেতু নিজেরা ডেভেলপার হিসেবে থাকবে, তাই তারা খুব দ্রুত কাজ শেষ করতে পারবে। কারণ এটা জি-টু-জি উদ্যোগ, এবং চীনা বিনিয়োগকারীদের আমাদের দেশে একটা বড় পুল বা নেটওয়ার্ক আছে। তারা যখন দেখবে, চীনের জন্য আলাদা একটা জোন তৈরি করা হয়েছে, তখন তারা বিনিয়োগে আরও আগ্রহী হবে।
তাছাড়া, তাদের ভেতরের সংযোগ ও অ্যাকসেস খুব শক্তিশালী, যা আমাদের এখনো সে স্তরে পৌঁছায়নি। কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের আশা, আমরা ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্টটা নির্বাচনের আগেই সাইন করতে পারব। যদি সেটা করতে পারি, তাহলে গ্রাউন্ডব্রেকিংও নির্বাচনের আগেই শুরু হয়ে যাবে।৬০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
সূত্র: দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড বাংলা




.jpg)

 10.11.2025.jpg)