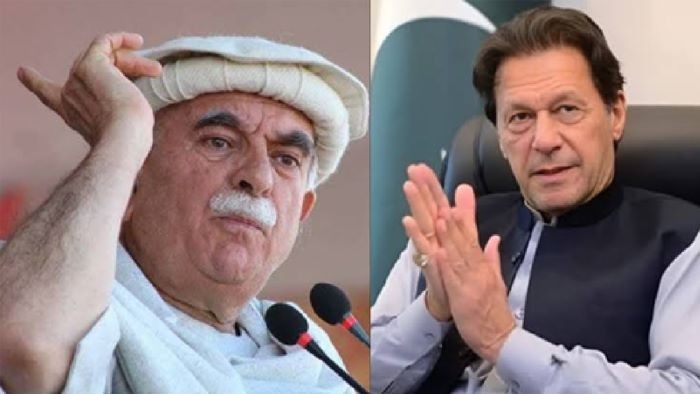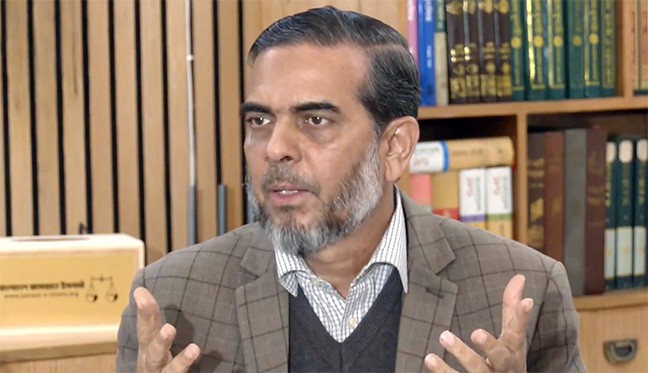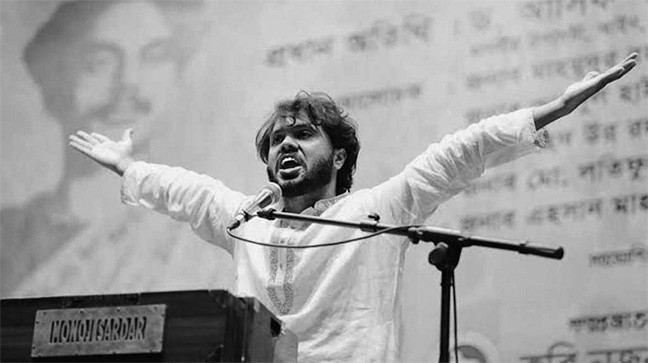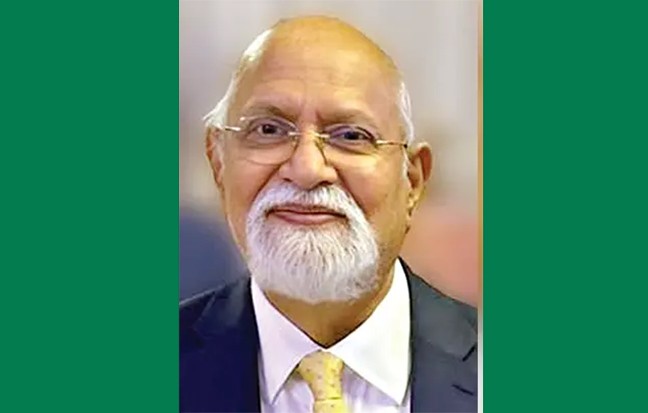মহিউদ্দিন কাউসার: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্তমান যে পুরোনো ভবনটি, সেটির জন্ম ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্মের ঠিক ৪২ বছর আগে। তখন এটি ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সচিবালয়। চিকিৎসক কিংবা রোগী নয়, ভবনের করিডরজুড়ে তখন পদচারণ ছিল কেতাদুরস্ত আমলাদের।
১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, তখন ভবনটির কর্তৃত্ব আসে তাদের কাছে। ভবনটি মুখর হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীদের পদচারণে।
তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভবনটি আবারও হাতবদল হয়। তখন এটি চলে যায় আমেরিকান মিলিটারিদের হাতে। ছাত্র-শিক্ষকদের বদলে ভবনটিতে শুরু হয় সৈনিকদের বুট-চারণ। আর সে সময়ই সেখানে যাত্রা শুরু হয় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ‘আমেরিকান বেস হাসপাতাল’-এর।
সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে সেটিই আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে হারিয়ে যাওয়া প্রস্তাবটি বিশ্বযুদ্ধের পর আবার আলোর মুখ দেখে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ শুরু করে তার স্বপ্নযাত্রা।
দুই হাজার শয্যার এই মেডিকেলে প্রতিদিন প্রায় তিন থেকে চার হাজার রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় শত শত হবু চিকিৎসককে।
ঢাকা মেডিকেলের দীর্ঘ ৭৬ বছরের ইতিহাস শুধুই তো দেশের রোগগ্রস্ত মানুষের পাশেই দাঁড়ানোর নয়, এ দেশের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণেও এর রয়েছে গৌরবময় অংশগ্রহণ। এই মেডিকেলের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যদের সাথে নিয়ে ৫২ এ একবুক তেজ নিয়ে মেডিকেলের বর্তমান জরুরি গেট—তখন যেটি আমতলা ছিল—সেখান থেকে ১৪৪ ধারা ভাঙেন। ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র এম আই চৌধুরী, সিদ্দিক, আসগর, জসিম, ফরিদুল হককে মেনে নিতে হয় কারাবন্দিত্ব। স্টেথোস্কোপ কাঁধে ঝুলিয়ে ঢাকা মেডিকেলের ছাত্ররাই রাতের আঁধারে হোস্টেল চত্বরে নির্মাণ করেন বায়ান্নর প্রথম শহীদ মিনার।
আপনি নিশ্চয়ই শামসুর রাহমানের ‘আসাদের শার্ট’ কবিতাটি পড়েছেন।
‘গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের/
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়...।’
১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে নিহত আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে প্রথম মিছিল বের করেছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের একঝাঁক তরুণ ছাত্র-চিকিৎসক। সেই ‘আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।’
একাত্তরে এই কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও সেবিকারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অপরিসীম মমত্ব নিয়ে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মেডিকেলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার জন্য নাম বদলে ভর্তি করা হতো। নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাকে পিষ্ট করে তাঁরা নিরাপত্তা দিয়েছেন দেশমাতৃকার অস্ত্রধারী প্রহরীদের।
এ কাজ সমন্বয় করতেন ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীমরা। আলবদররা তাঁদের ছাড়বে কেন? ছাড়েনি। নির্মমভাবে তাঁদের মতো এই মেডিকেলের আরও অনেক ছাত্র-শিক্ষককেও বি পি মেশিন ছেড়ে মেশিন গান চালাতে চালাতে জীবন দিতে হয়েছে যুদ্ধের মাঠে। গর্বে ভরে উঠে মন যখন জানতে পারি, মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দ্বিতীয় নারী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ছিলেন একজন ডিএমসিয়ান।
নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন তো সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে এই মেডিকেলের সাবেক ছাত্র ও শিক্ষক ডা. মিলন হত্যার পর থেকেই। বিভিন্ন দুর্যোগেও দেশের মানুষের পাশে অতন্দ্র সেবা নিয়ে এগিয়ে যান এখানকার শুভ্র অ্যাপ্রোন পরা মানুষগুলো।
৭৬ বছরের পথচলায় এই ঢাকা মেডিকেল জন্ম দিয়েছে দেশের প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রতিষ্ঠান ‘সন্ধানী’র। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অযুত স্বপ্ন নিয়ে, আরও একটু ভালোভাবে বাঁচার আকুতি নিয়ে যেখানে ছুটে আসেন।
এখান থেকে বছরের পর বছর শত শত চিকিৎসক দেশ তো বটেই, দেশের বাইরেও বিশ্বের নানা প্রান্তে ছুটে যাচ্ছেন চিকিতসা সেবার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে। যে মশালে ৭৬ বছর ধরে আলো জ্বেলে দিচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মানবিক ব্যর্থতা আছে, আছে অনেক সীমাবদ্ধতা—এসব তুচ্ছতা ছাই হোক। সেই ছাই থেকে জন্ম নিক ফিনিক্স পাখির, আশার আলোর।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র হিসেবে এখান থেকে আমরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই পাইনি, পেয়েছি অসংখ্য রোগী দেখার সুযোগ, সেই সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমাদের দেখিয়েছে মহান এক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আজও আমাকে মনে করিয়ে দেয়, চিকিৎসাতো একটি পেশা বটেই , পেশার সাথে সাথে এটি মানবসেবার এক মহান ব্রতও।
.jpg)

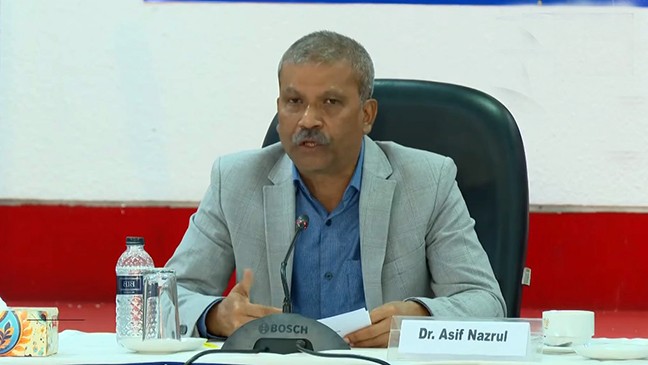


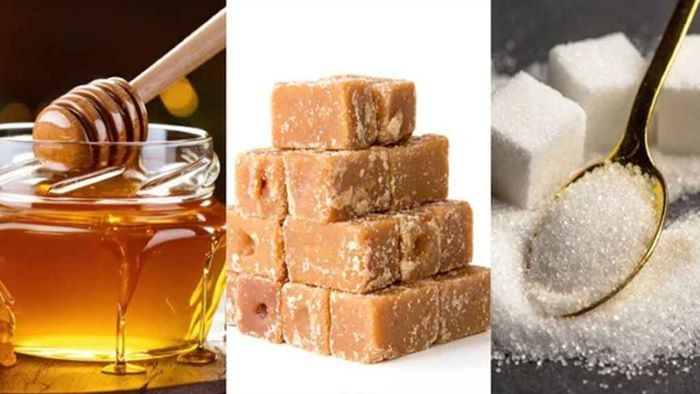
-696a0725b720e.jpg)



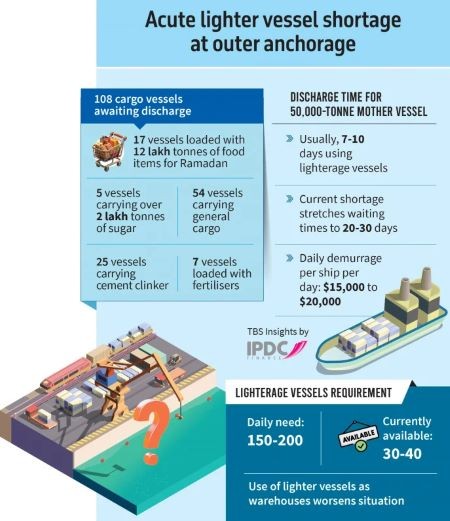


-696a32dfc81c4.jpg)