
স্বকৃত নোমান: [২] স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়ন আসলে কতোটা হলো? সৈয়দ আবুল মকসুদ : এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের আগে বুঝতে হবে উন্নয়ন বলতে আমরা কী বুঝি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট পাকা করা, বড় বড় ইমারত তৈরি, রাস্তায় দামি যানবাহন চলাচল প্রভৃতি যদি উন্নয়ন হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপি বাড়ার হার মন্দ না। বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেট প্রতি বছরই বাড়ছে। অর্থনীতিবিদরা বলবেন এগুলোই উন্নয়ন। জাতীয় উন্নতি অগ্রগতি বলতে আমি শুধু এসবকেই উন্নয়ন বলব না। একটি স্বাধীন দেশের উন্নতি বলতে আমি এর চেয়ে আরও কিছু বেশি জিনিসকে বুঝি। বহু পরাধীন জাতি অর্থনৈতিকভাবে খুবই ভালো থাকে। ষাটের দশকে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের আমলে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন যথেষ্ট হচ্ছিল। শিল্প, কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। শিক্ষার মান ছিল এখনকার চেয়ে অনেক ভালো। প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম করছিলাম। কারণ গণতন্ত্র ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের খবরদারি ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো। তাদের একটি তাঁবেদার ছিল বাঙালিদের মধ্যে। সুযোগ-সুবিধা সেই অল্পসংখ্যক মানুষই ভোগ করত। তারা করাচি লাহোর পিণ্ডিতে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। তারা ছিলেন অতি সুখে। অধিকাংশ মানুষ রাষ্ট্র থেকে কোনো সুবিধা পেত না। এ দেশের মানুষ চাইত এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে তারা নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, একটি উদার আধুনিক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ছিল প্রত্যাশিত। সে জন্যই মানুষ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে। জীবন দেয়। নারী সম্ভ্রম দেয়। কিন্তু সীমাহীন রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত হলো, তা জনগণের কাক্সিক্ষত দেশ নয়। রাষ্ট্র দুর্নীতিতে ডুবে গেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ শাসকরা এবং তাদের সহযোগীরা নির্লজ্জের মতো লুণ্ঠন করছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের লেশমাত্র নেই। শিক্ষার মান বলে কিছু নেই। সরকারি দলের ক্যাডার হলে দশ-পাঁচটা খুন করে পার পাওয়া যায়। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যে যতো বেশি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, ততো চুরি-চামারি। কাগজে লেখালেখি হয়। শাসকরা তাতে কর্ণপাত করেন না। ৪০ বছরে তৈরি হয়েছে একটি নষ্ট সমাজ। মানবিকতার লেশমাত্র নেই। একে আমি উন্নয়ন বলব না।
[৩] স্বকৃত নোমান : দেশে দুই ধরনের উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে। কেউ অনেক বেশি ধনী, কেউ অনেক বেশি গরিব। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তো ছিল বৈষম্যহীন সমাজ গঠন। তার তো বাস্তবায়ন হলো না। এই বৈষম্যমূলক উন্নয়নের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?
সৈয়দ আবুল মকসুদ : স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা আছেন, ব্যক্তিগতভাবে তারা অনেকে সংগ্রামী রাজনীতিক। পাকিস্তান আমলে জেলজুলুম সহ্য করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে সৎও। সজ্জনও বটে। কিন্তু তারা কেউই জানেন না একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কীভাবে চালাতে হয়। সংবিধানে গণতন্ত্রের কথা আছে। রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা নেই। সমাজতন্ত্রের কথা মূলনীতিতে রাখা হয়েছে কী কারণে আমার বোধগম্য নয়। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র স্বাধীনতার এতো বছরে একদিনের জন্যও ছিল না। তা হলে ওটা রাখার মানে কী? জনগণকে ভাওতা দেওয়া। মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করাকে শাসকরা নাম দিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কমিউনিস্ট নেতারা অন্ধের মতো সরকারের দালালি করতে লাগলেন। তারা বলতে পারতেন শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক-বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করে একটি নষ্ট রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সেখানে বসানো হয়েছে হয় অদক্ষ অনভিজ্ঞ লোকদের অথবা চোরচোট্টা। দেশটা না হলো সমাজতান্ত্রিক, না হলো পুঁজিবাদী। একটা জগাখিচুড়ি পাকানো হলো। রাষ্ট্রীয় সম্পদ শাসক দল ও তাদের চাটুকাররা লুটপাট করতে লাগল। যার বাড়িতে ঠিকমতো বাজার হতো না, রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন করে ছয় মাসের মধ্যে সে হলো লাখোপতি। ওই ধারায় রাষ্ট্র চলায় একটি বিরাট ধনী শ্রেণি তৈরি হয়েছে। তাদের সংখ্যা দেশের জনগণের ৮/১০ ভাগ। ৭০ ভাগ মানুষ অতি গরিব না হলেও খুবই কষ্টে আছে। নিন্মমধ্য শ্রেণির মরণদশা। একটি নিকৃষ্ট বৈষম্যমূলক সমাজ তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষের কাজ নেই। শিক্ষার্থীরা কয়েক কোটি বেকার। তাতে নানা অপরাধ করার প্রবণতা বাড়ছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৯০ ভাগ সাধারণ মধ্যশ্রেণি ও কৃষক-শ্রমিকের পরিবারের মানুষ। তাদের আশা ছিল একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। একটি মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। শাসকরাও সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র চলে গেল লুটেরাদের দখলে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিলো। দেশি-বিদেশি শোষণে ও চক্রান্তে আজ সমাজে উদ্বেগজনক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সমাজে গণবিস্ফোরণ ঘটে। বেশি দিন মানুষ অন্যায়-অবিচার সহ্য করে না। স্বৈরাচারী শাসকের দুর্গে মানুষ এক সময় আঘাত হানবেই।
[৪] স্বকৃত নোমান : বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্রের চাইতে ব্যক্তির কর্তৃত্ব বেড়েছে, বাড়ছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের চাইতে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব বাড়ছে। এটি কেন হচ্ছে? সৈয়দ আবুল মকসুদ : আমাদের রাষ্ট্রের কোনো নীতি-আদর্শ নেই। কোনো স্থায়ী সিস্টেম গড়ে ওঠেনি। কয়েকটি দল মিলে একটা লুটেরা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। তারা ভাগবাটোয়ারা করে দেশ চালাচ্ছেন। প্রত্যেক দলেরই একজন করে নেতা আছেন। দলে তিনিই সব এবং সেই দল যখন ক্ষমতায় যায়, একা হোক বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে হোক, তখন দলীয় নেতাই দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে যান। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত, রীতিনীতি সব একদিকে, আর দলীয় প্রধানের ইচ্ছা-অনিচ্ছা একদিকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নেতারা পরস্পরের সহকর্মী। কিন্তু বাংলাদেশে তা নয়। অন্যান্য নেতা শীর্ষনেতার ভৃত্য। তিনি যা হুকুম করেন, যে ব্যাপারে যা ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তারা জো হুকুম বলে তা তালিম করেন। মহাজোটের ছোট দলগুলোর নেতাদের আচরণ ও কাণ্ড দেখে করুণা হয়। স্তাবকতা ও ব্যক্তিহীনতার একটা সীমা থাকে। নিজের পেটটা ভরলেই তারা খুশি। দেশ ধ্বংস হোক। মানুষ যে তাদের ঘৃণা করে এটা তারা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু পরোয়া করেন না। কারণ নেতার তোয়াজ করে ভাগ্যটা তো গড়ে নিচ্ছেন। ছেলেমেয়ের জন্যে লন্ডন আমেরিকায় বাড়ি কিনছেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে যা হবে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানেও তাই হবে। এখন আর বাংলাদেশে কেউ নিজের মেধা-যোগ্যতার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন মনে করছে না। বড় কর্তার পাদুকা বহন করার মধ্যেই নিজের ভাগ্য গড়ার পথ বেছে নিচ্ছে।
[৫] স্বকৃত নোমান : রাষ্ট্র জনস্বার্থ দেখার চাইতে ব্যক্তিস্বার্থকেই বড় করে দেখছে। এর প্রকৃত কারণ কী? সৈয়দ আবুল মকসুদ : জনস্বার্থ আবার কী? পাঁচশ কোটি মানুষ মরলেই বা কি? ব্যক্তিস্বার্থই তো আসল। এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা জনগণের বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না। দেশের উপকারে আসবে না। কিন্তু ওই প্রকল্প থেকে হাতিয়ে নেয়া যাবে শ শ কোটি টাকা। নষ্ট রাষ্ট্রে জনগণ বলে কিছু নেই। ব্যক্তির লাভটাই প্রধান। ফুলবাড়ির বিশ লাখ মানুষ মরে তো মরুক। তারা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হোক। সেখানকার পরিবেশ ধ্বংস হোক। উত্তরবঙ্গ যেটা দেশের খাদ্যভাণ্ডার সেটা মরুভ‚মি হোক। কারও কিছু যায় আসে না তাতে। কয়লা তুলে বিদেশে রপ্তানি করে কয়েক শ’মানুষ কোটি কোটি টাকার মালিক হলেই তো হলো।
[৬] স্বকৃত নোমান : সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই অগণতান্ত্রিকতা দেখা যায়। এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ যদি ব্যাখ্যা করেন...। সৈয়দ আবুল মকসুদ : ওই সংবিধানের কথাটা বলবেন না। একটা দেশের সংবিধান বলে একটা বই থাকতে হয় বলে ওটা আছে। এবং ওটার মধ্যে কি লেখা আছে না আছে তাতে শাসকদের আমলাদের কি যায় আসে। পরিবারে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নেই, পাড়ার ক্লাবে নেই, কোনো সংঘ সমিতিতে নেই, রাষ্ট্রে গণতন্ত্র হবে কি করে? আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির কথা আমরা বলি। এক নেতাই তাদের দলে বসে আছে বহু বছর ধরে। তা থাকলে দোষ কী? ছোট দল, যাদের জনগণের মধ্যে কোনো সমর্থক ও প্রভাব নেই, তাদের কি অবস্থা? এক একটি দলের সভাপতিকে মনে হয় তারা দলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার-সিইও অর্থাৎ প্রধান নির্বাহী। নেতা নন। একটি নষ্ট সমাজ, নষ্ট রাষ্ট্র ও নষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। রাজনীতিকদের মধ্যে যাকে দেখা যায় টাকা-পয়সার ব্যাপারে সৎ, তার আবার মাথায় কিছু নেই। বোকার মতো মান্ধাতার আমলের কথা আউড়ান। সৃষ্টিশীলতার লেশমাত্র নেই। দূরদর্শিতা নেই। বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, বিচার বিশ্লেষণ করার কোনো ক্ষমতা নেই, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। বাধাধরা গদের বাইরে কোনো নতুন উন্নত ধারণা দিতে পারেন না। কোনো ভালো ইস্যুকে জনপ্রিয় করার ক্ষমতা নেই। গোলটেবিলে বক্তৃতা দেন। টিভি চ্যানেলে ছবি দেখা যায়। ওতেই খুশি। রাজনৈতিক নেতার দায়িত্ব অনেক বড়। সে দায়িত্ব কেউ পালন করছেন না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নেতাদের আগ্রহ নেই। ক্ষমতার আগ্রহটা প্রবল। ক্ষমতায় যারা যেতে পারেন না তারা সরকারের সমালোচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই করে গণতন্ত্র চর্চার পথ একটি কানা গলিতে গিয়ে ঠেকেছে।
[৬] স্বকৃত নোমান : পৃথিবীব্যাপী মানব-সভ্যতা অনেক এগিয়েছে। মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার চাইতে এখন আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে আগে মারামারি, তারপর মীমাংসা। এর সমাজতাত্তি¡ক ব্যাখ্যা কী? বাঙালির এই উগ্র স্বভাব কি আগে থেকেই ছিল?
সৈয়দ আবুল মকসুদ : বাঙালি একটি বিবদমান জাতি। কোনো প্রশ্নেই আলোচনা করে মীমাংসায় পৌঁছার স্বভাব বাঙালির রক্তে নেই। ব্যক্তিগত জীবনেও রাস্তাঘাটে, গ্রামেগঞ্জে এমনকি অফিস আদালতেও আস্তিন গোটানো, হাতাহাতি, মারামারি, মালকোচা মেরে অন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া তার স্বভাবজাত। অন্যকে গালাগালি করা তো বাঙালির প্রতিদিনের অভ্যাস। অন্যকে অপমান করার প্রতিভা বাঙালির অপার। মিথ্যা কথাকে বাঙালি খুব পছন্দ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমাজবিজ্ঞানীও বাঙালির স্বভাব বিশ্লেষণ করে তার ক‚লকিনারা করতে পারবেন না। তবে বড় বড় সংস্কারকরা জাতিকে সংশোধন করে উন্নততর পর্যায়ে নিতে পারেন। কনফুসিয়াস চীনের সমাজে তা করেছিলেন। ভারতবর্ষেও হিন্দুসমাজে গত দুই আড়াই হাজার বছরে অনেক মহামানব এসেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে তেমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেননি। মুক্তিযুদ্ধসহ এ পর্যন্ত বাঙালি যা অর্জন করেছে তা জনগণের সচেতন অংশের আত্মত্যাগের ফলে হয়েছে। রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। জাতি গঠিত হয়নি। কারণ আমাদের জাতির কোনো স্রষ্টা নেই। আপনাআপনি বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যেটুকু হওয়ার তাই হয়েছে। অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাঙালি নয়। সঙ্কর জাতি। নানা রক্ত বাঙালির শরীরে। দেখুন না রাস্তায় ৫০ জন বাঙালির ৩০ রকমের চেহারা। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। কেউ কালো, কেউ বাদামি। কেউ ধবধবে ফর্সা। কারও নাক উঁচু, কারও নাক বোঁচা। কারও চোয়াল চওড়া। কারও মাথা ছোট। কোনো থাই জাতির মধ্যে আপনি তা পাবেন না। ভিয়েতনামির মধ্যে পাবেন না। জাপানির মধ্যে পাবেন না। চীনাদের চেহারা-সুরত একরকম। কোরিয়া সবাই একই চেহারার। বাঙালি এক অন্যরকম জাতি। কোনো সংহতি নেই। দেখতে যেমন নানানরকম, স্বভাব-চরিত্র, মন-মেজাজও নানানরকম। কোনো ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছা তাই তার জন্যে কঠিন। ঠেলায় পড়লে অবশ্য অনেককিছু সে মেনে নিতে বাধ্য হয়।
[৭] প্রয়াত হলেন সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ। তাঁর এ সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০১২ সালে। ‘আলোচনা করে মীমাংসায় পৌঁছার স্বভাব বাঙালির রক্তে নেই’ শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। এখানে দেওয়া হলো দীর্ঘ সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ। পুরো সাক্ষাৎকারটি রয়েছে বিদ্যাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় স্বকৃত নোমানের ‘বহুমাত্রিক আলাপ’ বইয়ে।




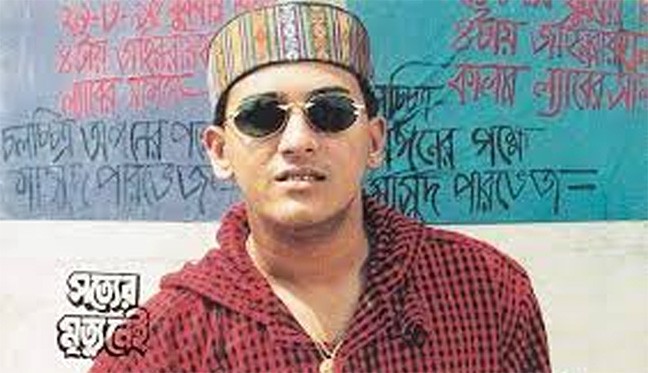






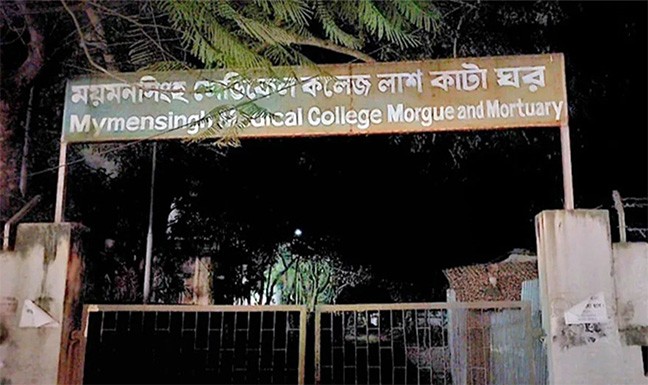







.jpg)












