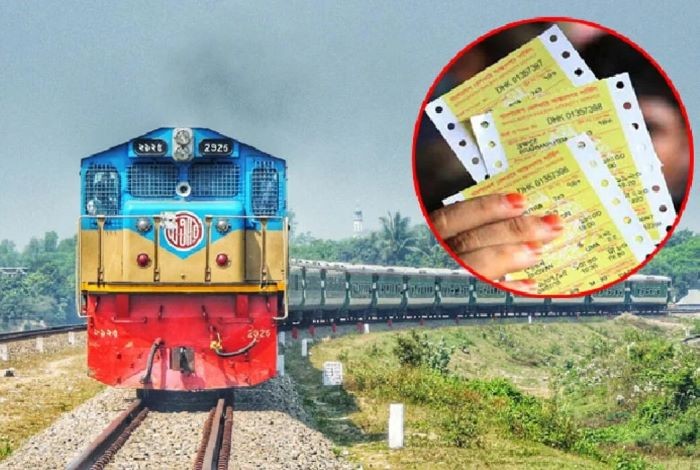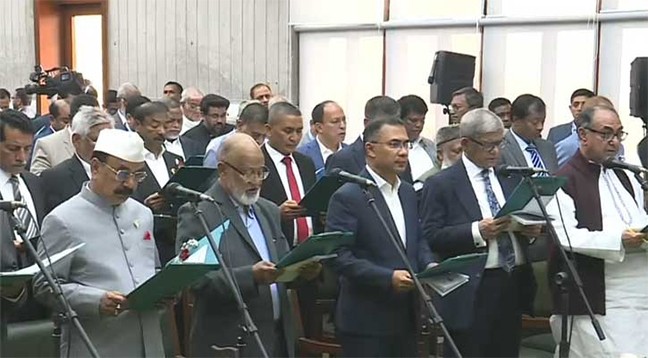কাকন রেজা : এক সময় মাদরাসা শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলতাম। ‘হুজুর’ বলে উপহাসের ভাষায় তাদের যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতো, তার বিপক্ষে বলতাম। বলতাম, শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশকে মূল¯্রােতের বাইরে রাখা হবে হঠকারিতা। তবে, বলার পর থাকতাম ভয়ে ভয়ে। এ দেশের একপাল কথিত ‘প্রগতিশীল’ আছেন, তারা না আবার গায়ের উপর উঠে পড়েন। ‘তকমা’ পাই ‘মূর্খ’ কিংবা তাদের ভাষায় মুখের সমমান ‘ইসলামিস্ট’-এর, দু’একবার পাইনি যে তাও নয়। কিন্তু হঠাৎ করেই দিন পাল্টেছে। যাদের অনেকেই ‘মূর্খ’ বা ‘ইসলামিস্ট’ ইত্যাদি তকমা প্রদানের সোল এজেন্ট ছিলেন, তারাই এখন উল্টো সুরে গাইছেন। তারাই আমার মতন ‘মূর্খ’দের আগের বলে আসা কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কথা বলছেন, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। খুবই আনন্দ লাগছে। মাশাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, বলতে ইচ্ছে করছে।
অনেকে বলতে পারেন, রাজনীতির ‘রিভার্স সুইং’য়ের কারণেই এমন বৈপরিত্যের ঘটনা। বলি, রাজনীতি আর বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রাজনীতিকরা কাজ করেন ক্ষমতায় যাবার স্বার্থে। কিন্তু যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্ম করেন, তাদের তো আর ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারটি নেই। রাজনীতির ব্যাপারে উদাহরণ দিই, হেফাজত যখন শাপলা চত্বরে অবস্থান নেয়, তখন খালেদা জিয়া তাদের সমর্থন দিয়েছিলেন। তখন তাকে জঙ্গিদের সঙ্গী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিলো। এখন অবস্থার পরিবর্তনে সব সুরই উল্টো। এটাই রাজনীতি। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে ‘শেষ কথা নেই’ বলে যে প্রবাদটি প্রতিষ্ঠিত, তার কারণেই অবস্থাটা এমন। সুতরাং যে বিষয়ের শেষ কথা নেই, তা নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো। বিশেষ করে তাদের, যারা রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন, অন্তত শারীরিকভাবে।
একজনের লেখা পড়লাম। তিনি কওমি মাদরাসা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন, ভালো ভালো কথা। কওমি সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে প্রয়োজনের যথার্থতাও ব্যাখ্যা করলেন। তার কথার সাথে আমার চিন্তারও কিছুটা মিল রয়েছে। কিন্তু এই মিলে গোল বাধালো, তার বছর দুয়েক আগের একটি লেখা। সেখানে তিনি কওমি মাদরাসাগুলোকে অশিক্ষার আধার বলেছেন। বলেছেন, এর মাধ্যমে ‘চরমপন্থা’র উদ্ভব ঘটছে। তার দু’বছর আগের লেখার সাথে হালের লেখার কোনই সাযুজ্য নেই। দর্শনগত মিল নেই। মানুষের চিন্তার পরিবর্তন ঘটতেই পারে। দর্শনগত বিশ্বাসও পাল্টাতে পারে। বিশ্বের অনেক বড় মানুষেরও বদলেছে। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে, বিশ্বাস বদলানোর ক্ষেত্রে আগে স্বীকার করা উচিত, আগের চিন্তা ভুল থাকার ব্যাপারটি। ব্যাখ্যা করতে হবে, কেনো ভুল ছিলো। ইচ্ছে হলো একটা বললাম, লিখলাম, ইচ্ছা হলো আরেকটা, এটা তো হতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির সাথে জড়িতরা গিরগিটি নন, অবস্থা অনুযায়ী রঙ বদলাবেন। তাদের চিন্তার উপর অনেক মানুষের ভাবনা ও কর্ম নির্ভর করে। তাদের রঙ বদল সেসব মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, বিপদগামী করতে পারে। সুতরাং অবস্থান বদলের ব্যাখ্যাটা জরুরি।
‘সংস্কার’ বিষয়ে অনেকে কথা বলেন। ‘সংস্কার’ বিষয়টি কিন্তু ধর্ম এবং কালচার দুটোইতেই রয়েছে। খুব সহজ উদাহরণ দিই, যারা গানের চর্চা করেন, তাদের প্রতিদিনের সকাল-বিকাল রেওয়াজ বাঁধা। তেমনি ধর্মেও নামাজ কিংবা পূজা বাঁধা। গানের রেওয়াজ হলো ‘কালচার’, ধর্মের নামাজ কিংবা পূজা। ‘কালচার’ বলে, গলাসাধা গলাশুদ্ধির জন্য, ধর্ম বলে উপাসনা আত্মশুদ্ধির জন্য। সুতরাং ধর্মীয় ‘সংস্কার’ নিয়ে যারা কথা বলেন, তাদের ভাবনায় থাকা উচিত, ‘সংস্কার’ সব কিছুতেই আছে, ধর্ম আর কালচারেও আছে।
‘সংস্কার’ হলো জীবনাচরিত। কদিন আগে ডকুমেন্টারি দেখলাম, ভারতের বিভিন্ন গোত্রের বিয়ের ধরণ নিয়ে। তারা এই পুরো ব্যাপারটিকেই ‘কালচার’ বলছেন। ‘কালচারে’র কাছাকাছি বাংলা হলো ‘সংস্কৃতি’ যার থেকেই ‘সংস্কার’ শব্দটির উদ্ভব। ‘কালচারে’র কাছাকাছি বললাম এজন্য যে, ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি এসেছে ‘সংস্কৃত’ থেকে। আর ‘সংস্কৃত’ কোনোকালেই এই উপমহাদেশের সম্পূর্ণ ‘সংস্কৃতি’ ছিলো না। যাহোক, সেই ডুকমেন্টারিতে দেখানো বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পুরোটাই ‘কালচার’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিয়ের মূল যে আনুষ্ঠানিকতা তা হলো, ধর্ম। দেবতাকে সাক্ষী মেনে, তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেই বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, এটা পরিষ্কার, ধর্ম ‘কালচারে’র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতএব যারা ‘সংস্কার’ বিষয়ে সেনসেটিভ, ‘সংস্কৃতি’ বিষয়ে উন্মুখ, তাদের বিষয়টি ভালোভাবে আত্মস্থ করা প্রয়োজন। আর এই আত্মস্থতা রাজনৈতিক কারণে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক কারণে। রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রয়োজনে হঠকারিতা থাকতে পারে, ছলনা থাকতে পারে, যাকে ‘কৌশল’ নামে অভিহিত করা হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো এমন কৌশল দোষের নয়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এই ‘কৌশল’ সম্পূর্ণত পরিত্যাজ্য।
লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট