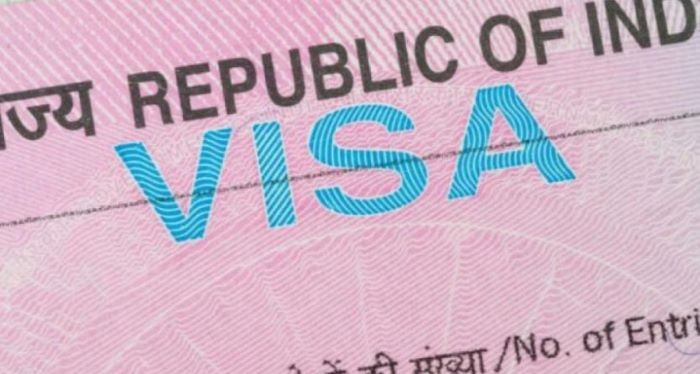কাকন রেজা : সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, সিপিডি বলছে, বাংলাদেশের বৈশ্বিক সক্ষমতা কমেছে। ১৪০টি দেশের মধ্যে গতবার ছিল ১০২-এ, এবার অবস্থান নেমেছে আরো একধাপ, অর্থাৎ ১০৩-এ। ১৭ অক্টোবর সিপিডি তাদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রে এমনটিই জানিয়েছে। গবেষণাপত্রে সিপিডি দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি মেনে নিয়েই বলেছে বৈশ্বিক সক্ষমতায় দেশটি পিছিয়েছে আরো এক ধাপ। আর অবনতি তথা পিছিয়ে পড়ার ১২টি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে সিপিডি’র গবেষণাপত্রে। এই ১২টি ক্ষেত্রের কথা বলার আগে মাথায় আসা প্রশ্নটি করে নেই, সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি মানেই সবক্ষেত্রে অগ্রগতি, এখানে পিছিয়ে পড়ার কথা আসে কিভাবে!
এখন বলি, দু’একটি করে হারাধনের ১০টি নয় সিপিডি’র ১২টি হারানো ছেলের কথা। অর্থাৎ যে কয়টি ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ, তাদের বিষয়ে। এর মধ্যে প্রথমটিই হলো ‘উৎপাদন বাজার’। উৎপাদন বাজারে যদি একটি দেশ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ে, তবে সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি ঘটে কোন পন্থায়? উৎপাদন বাজারে বিশ্বের ১৪০টি দেশের মধ্যে সিপিডি’র দেয়া তথ্যে আমাদের অবস্থান ১২৩তম। বোঝেন অবস্থা। এই অবস্থায় থেকে সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, অর্থনীতির কোন টার্মের সাথেই বা এমন উন্নতিটা যায়!
এরপর আসি ‘বাণিজ্যিক গতিশীলতা’য়। সারাবিশ্বের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে বাণিজ্যের গতিশীলতাকে নির্ভর করে। সিপিডি দেয়া তথ্য মতে আমেরিকা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার শীর্ষে রয়েছে। এরপরে রয়েছে, জার্মানি, সিঙ্গাপুরের মতন দেশগুলি। এখানে আমাদের অবস্থান ১২০তম। গতিশীলতায় যদি আমাদের অবস্থা এই হয়, তাহলে সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের গতি সীমাটি আসলে কোন লিমিটের? ‘শ্রমবাজারে’ আমাদের অবস্থান ১২৫তম। ১৪০টি দেশের মধ্যে যাদের শ্রমবাজার ১২৫-এ তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কতটা উল্লেখ করার মতো! অর্থনীতি তেমনটা না বুঝলেও সার্বিক উন্নয়নের সাথে শ্রমবাজারের সম্পর্কটা না বোঝার মতন অতটা গাড়ল নই। আমাদের অর্থনীতিবিদরা যদি এই সম্পর্কের সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির নতুন কোনো থিওরি উদ্ভাবন করেন, তবে তার কথা আলাদা। এরপরে বলা হয়েছ ‘শিক্ষা’ ও ‘অবকাঠামো’র কথা। এ দুই ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান যথাক্রমে ১১৬ ও ১০৯। শিক্ষার কথা না বলি, যা গেছে তা নিয়ে বলারও কিছু নেই। বলতে গেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ঘ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিলের দাবীতে অনশন করা সেই ছেলেটির কথা বলতে হয়। তবে অবকাঠামোগত বিষয়ে উন্নতির এত উপাখ্যান প্রতিদিন শুনি, তাতে ১৪০টি দেশের মধ্যে ১০৯ থাকাটা মেনে নিতে কষ্ট হয়।
১২টির মধ্যে আরেকটি ক্ষেত্রের কথা বলেছে সিপিডি তার গবেষণাপত্রে। সেটা হলো আলোচিত ‘আইসিটি’ ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটি তো আমাদের কাছে রীতিমত ‘মিথ’-এ পরিণত হয়েছে, অনেকটা গ্রিক পুরাণের মতন। এনিয়ে এতো কাহিনী রয়েছে এবং তা অবশ্যই অগ্রগতির আর উন্নতির। এমন ক্ষেত্রটির পিছিয়ে পড়ার তথ্য বিস্ময়কর।
সিপিডি’র তথ্যের সাথে উন্নতির প্রচলিত গল্প সত্যিই সাংঘর্ষিক। সিপিডি’র তথ্য যদি সঠিক হয়, তবে ‘শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই’, এমন প্রবাদটিও বিশ্বাস করতে হয়। বাংলাদেশে অনেক কৃতি অর্থনীতিবিদ আছেন, যারা হয়তো ভালো জানবেন সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রগতি বা উন্নতির সাথে উৎপাদন বাজার, বাণিজ্যিক গতিশীলতা, শ্রমবাজার, শিক্ষা, অবকাঠামো বা আইসিটি’র মতন বিষয়গুলি কতটা জড়িত। তারা হয়তো বলতে পারবেন, এসব বিষয়ের অগ্রগতি ছাড়া সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব কিনা, হলেও তেমন উন্নয়নের মন্ত্রটি কী। কারণ, মন্ত্র ছাড়া বাস্তব বা ইহলৌকিক কোনো পন্থায় এমনটা হওয়ার কথা নয়, সম্ভবও নয়। আর সম্ভব হলেও তা আমাদের মতন ‘সর্বসাধারণে’র বোধের বাইরে। সারসংক্ষেপে সান্তনার কথা বলি। বৈশ্বিক সক্ষমতায় সিপিডি’র ভাষ্যে ১৪০ এর মধ্যে আমাদের অবস্থান ১০৩-এ। অতএব আমরা সামনের ১০২টি দেশের কথা না ভেবে পেছনের ৩৭টি দেশের কথা ভাবি। কী দরকার অযথা কষ্ট পাবার। এক্ষেত্রে পায়ে জুতা না থাকার কষ্ট ভুলতে, পা না থাকা মানুষদের ফিরে দেখার গল্পটা স্মরণ করাই শ্রেয়তর। এমন গল্পটি আমাদের আপাত সান্তনার আশ্রায়ন প্রকল্প হিসাবে গ্রহণীয় হতে পারে। আর প্রকল্প মানেই তো নিশ্চিত উন্নতি। লেখক : সাংবাদিক, কলাম লেখক। সম্পাদনা : রেজাউল আহসান