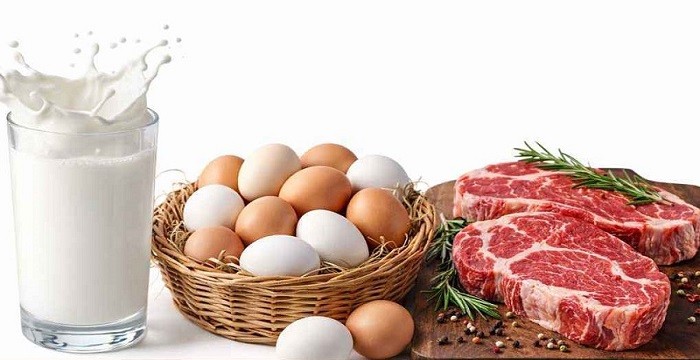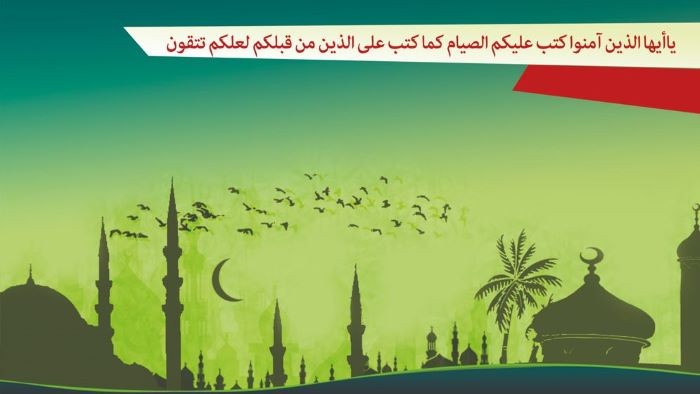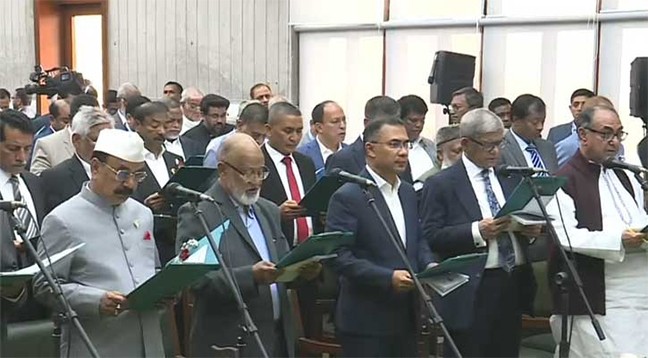আর রাজী: দস্যু-তস্কর-লুটেরাসঙ্ঘ যখন পর দেশের ভূমি গ্রাস করে দখলদারসঙ্ঘ বনে যায় তখন তাদের সেই দখল বজায় রাখতে যা যা করতে হয় তাই তাই করেছে বঙ্গভূমির বৃটিশ দখলদারসঙ্ঘ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অব্যহতভাবে লুণ্ঠিত ও চোষিত সম্পদ নিজ দেশে পাচারের জন্য তারা নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সেই সব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’। দখলদারদের স্বার্থ রক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা সমাজদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গকে সংক্রমিত করতে পারে। ব্রিটিশ লুটেরা-দখলদারদের সেই আকাক্সক্ষা পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের সবচে বড় সর্বনাশা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আজ এই দেশের যা কিছু দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনা তার সূতিকাগার এই বিশ্ববিদ্যালয়। এই অতি-নেতিবাচক মন্তব্য সবিস্তারে ব্যাখ্যার দাবি রাখলেও এই অংশে কেবল একটি উদাহরণ ব্যবহার করবো। সেই উদাহরণ বুঝতে অনেকটা সহায়তা করবে কেন এই পরিণতি হলো। আমরা জানি, ভাষা কেবল চিন্তার বাহনই না, চিন্তার স্মারকও বটে। মানুষের ভাষাই বলে দেবে তার চিন্তার শক্তি ও দুরবস্থার কথা এবং ইঙ্গিত দেবে তার ভবিষ্যতের। এই কথাটা প্রেক্ষাপটে রেখে আমরা বুঝতে চাইবো ‘ইউনিভার্সিটি’ ভাব-প্রত্যয়টি কীভাবে বাংলায় ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ অভিনামে আত্মস্থ হয়েছে এবং তার পরিণতি কী। যতোটুকু বুঝতে পারি, ‘বিদ্যালয়’ শব্দটা বাংলাভাষায় খুব বেশি দিন হয় চালু হয়নি। কলিকাতায় প্রথম স্কুল ‘সেন্ট থমাস স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৯ সালে। ১৮০০ সালে এসে হয় প্রথম কলেজ ‘ফোর্ট উইলিমাম কলেজ’, তার ১৭ বছর পর ‘হিন্দু কলেজ’ চালু হলে ‘কলেজ’ প্রত্যয়টা নিজেদের ভাষায় বুঝে নেওয়ার তাগিদ তৈরি হয়ে থাকবে। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতে কলিকাতার লেগেছিলো অর্ধশত বছরের বেশি। ১৮৫৭ সালে এসে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি’। অনুমান করি এই সময় কালেই ‘বিদ্যালয়’ শব্দটা বাংলাভাষায় পাট্টা গেড়েছে।
সে কালে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা করার দায় ছিলো বাংলা-না-জানা লুটেরা-দস্যু-দখলদার ইংরেজদের। দস্যুবৃত্তির সক্ষমতা যেহেতু তাদের ছিলো সুতরাং তাদের আজ্ঞা পালনের লোকের অভাব হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করছিলেন বাংলা-অপছন্দ-করা সংস্কৃত-পণ্ডিতরা। এই কাণ্ডে অনেক অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ তারা বাংলায় চালু করেছেন আবার সংস্কৃত নিয়মে নতুন বাংলা বানিয়েছেন। মনে রাখা দরকার, প্রাণের তাগিদে তারা এই কাজ করেননি, করেছেন আয়-উপার্জনের প্রেষণে। স্বভাষার স্বভাব তাদের বিবেচনায় রাখতে হয়নি। অনুমান করি, ‘বিদ্যালয়’ তাদেরই আমদানি। আমাদের গুরুগৃহ ছিলো, টোল ছিলো, চতুষ্পাঠী ছিলো, পাঠশালা ছিলো, বিহার ছিলো, মক্তব ছিলো; মাদ্রাসা ও জামিআর সঙ্গে অনেকের পরিচয় ছিলো কিন্তু ‘বিদ্যালয়’ ছিলো না। ‘বিদ্যালয়’ শব্দটা ব্যবহারের সূচনাকালে বিদ্যাপীঠ, বিদ্যামন্দির, বিদ্যায়তন ইত্যকার শব্দও ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছিলো কিন্তু কল্কে পায় ‘বিদ্যালয়’। বিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্য বিপুল। কিন্তু অনুবাদকদের কল্যাণে উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ‘বিদ্যা’ শব্দটা ‘শিক্ষা’র সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার বিভিন্ন শিক্ষামন্দির বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত হতে শুরু করে। এই তিন প্রতিষ্ঠানই দেয় বা দিতে চায় ‘শিক্ষা’ কিন্তু তাদের নাম- ‘বিদ্যালয়’!
যারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইংরেজি নামের বাংলা করছিলেন তাদের খুব ভালো করে ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকার সুযোগ ছিলো না। আবার যাদের জন্য তারা এই নামগুলোর বাংলা করছিলেন সেই দখলদার ইংরেজদেরও বাংলা ভাষা সম্পর্কে ভালো জানা-শোনা ছিলো না। এই সুযোগে গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালানোর মতো কিছু একটা বাংলা দাঁড় করালেই সে সময় চলে যাচ্ছিলো। সুতরাং স্কুলের বাংলা ‘বিদ্যালয়’ হলো, কলেজের বাংলা হলো ‘মহাবিদ্যালয়’। উল্লেখ্য, ‘নালন্দা মহাবিদ্যালয়’ সম্পর্কে পণ্ডিতদের (যারা একই সঙ্গে হিন্দু ও সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞ) নিশ্চয়ই শোনা বা পড়া ছিলো কিন্তু বৌদ্ধদের এই জ্ঞানপীঠকে যে ঠিক কোনো পরিচয়ে সনাক্ত করা যায় এবং/বা কোনো স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে দিকে মন দেওয়ার অবকাশ সম্ভবত তাদের ছিলো না। কোনো একটা ভাষা ব্যবহারের আদ্যোপান্ত অনুসরণের কঠিন পথে না হেঁটে কয়েকটা চুরি করা কথার আশ্রয় নিয়েই তারা মনে করেছেন খুব একটা জ্ঞানের কাজ সারা গেলো! অনেক ক্ষেত্রেই ভুলভাল একটা কিছু অনুবাদ করে দিলেই সমাজ-মানসে তা সহজে গৃহীত হয় না। কিন্তু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় হলো। ‘কেন হলো’ এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে কথাটা মনে ধরেছে সেটিও কম মন্দ নয়! বাংলায় ‘বিদ্যা’ শব্দটার একটি অর্থ চৌর্যশাস্ত্র বা চুরি। স্কুল কলেজগুলোয় তখন যা হচ্ছিলো এবং তা থেকে এদেশের বিদ্যার্থীরা যা নিচ্ছিলেন বা পাচ্ছিলেন তাকে চৌর্যশাস্ত্র বলাই সম্ভবত সমীচীন মনে করেছে তৎকালের জনমানস। সুতরাং স্কুল কলেজের বাংলায় ‘বিদ্যা’ শব্দটা আলয়ের পূর্বপদ হিসেবে জুড়ে গেলে আপত্তির কিছু দেখেনি এই ভাষার সাধারণ ব্যবহারকারীরা।
বঙ্কিম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথার সমর্থনে ‘বিদ্যা’ শব্দটার ব্যবহার দেখানো যায়- ‘সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।’ এটি বঙ্কিম থেকে নেওয়া বটে কিন্তু সত্য হচ্ছে, এটি এ সমাজে প্রবাদ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। তার মানে ‘বিদ্যা’ শব্দটাকে চৌর্যশাস্ত্র বা চুরি দিয়ে প্রতিস্থাপন করাটা এই সমাজমানসে আগে থেকেই প্রোথিত ছিল। নইলে সুধীন্দ্রনাথ কেন ‘মহাবিদ্যা’ শব্দটার এমন ব্যবহার করতে যাবেন- ‘হয়তো মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হতো’। না আমি ‘দশ মহাবিদ্যার’ কথা ভুলে যাইনি। ‘এতা দশ মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ’ বলে দেয় ‘দশ মহাবিদ্যা’র দশা সম্পর্কে বাঙালিমানস শত শত বছর ধরেই সচেতন ছিলো, তা সত্ত্বেও তন্ত্রমন্ত্রের বাইরে থাকা মানুষ বিদ্যা’র ব্যাঙ্গার্থকেই আপন করেছিলো যথা-অর্থ হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘ইউনিভার্সিটি’র বাংলা হিসেবে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ শব্দটা যখন চালু হলো তখনও সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করে নিলো। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় - এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন পরের ভাবের ঘরে চুরি করে বা নকল করে বানানো, তার ভেতরে কায়কারবার যা হয় সেসবও যেহেতু নকল করেই চলে, এ কারণেই সম্ভবত বাঙলার সাধারণ মানুষ তাদের ভাষায় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ তিনটি গ্রহণে আপত্তির কারণ দেখেনি। আর এতেই এই নামকরণের ভেতরে লুকিয়ে থেকে গেলো সে সময়ের পণ্ডিতদের কোনো একটা ভাবপ্রত্যয় বাংলায় অনুধাবন ও অনুবাদে যথেচ্ছাচারের ইতিহাস।
প্রথম যখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো তখন স্কুলের বাংলা করার দরকার হয়তো তেমন ছিলো না। কিন্তু যখন নিজেদের মতো করে হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ তৈরি করা গেলো তখন তার একটা জনবোধ্য বাংলা নাম অবশ্যই জরুরি হয়ে থাকবে। সুতরাং তখনই বাংলায় জন্ম নিয়ে থাকবে ‘বিদ্যালয়’ শব্দটি। বাংলা একাডেমি তার বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে ‘বিদ্যালয়’ শব্দটার প্রথম ব্যবহারের যে উদাহরণ দিয়েছে সেটি ১৮২৯ সালের বঙ্গদূত থেকে নেওয়া। বিদ্যার আলয় হচ্ছে বিদ্যালয়। কিন্তু বিদ্যা শব্দটার অর্থ হচ্ছে, ‘যাহার দ্বারা বিদিত হওয়া যায় তাহার আধার’ বা ‘যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়’। কার বা কিসের দ্বারা বিদিত হওয়া যায় বা জ্ঞান সাধিত হয়? উদাহরণ- শাস্ত্র বা বই দ্বারা। তার মানে, বিদ্যার ‘আলয়’ বা ধারক যদি কিছু থাকে সে শাস্ত্র বা বই। বই নিজেই ‘বিদ্যালয়’ কিন্তু ‘স্কুল’ তো বই নয় বা বিদ্যার আলয় নয়। সম্ভবত এ কারণে ‘বিদ্’ ক্রিয়ামূলে অসংখ্য শব্দ বাংলায় থাকলেও ‘বিদ্যালয়’ শব্দটা ঊনিশ শতকের আগে বাংলায় সুলভ হয়নি। কলেজ যেহেতু বিদ্যালয়ের চেয়ে গায়েগতরে অনেক অনেক বড় বা বিশাল দেখায় সুতরাং তার বাংলা হলো ‘মহাবিদ্যালয়’! (স্মরণ করুন, বাংলায় ‘মহাবিদ্যা’র একটি অর্থ চুরিবিদ্যা) কিন্তু অচিরেই যখন ‘ইউনিভার্সিটি’র সঙ্গে বঙ্গীয় পণ্ডিতদের পরিচয় ঘটলো এবং তার বাংলা করা জরুরি হয়ে দাঁড়ালো তখন তৈরি হলো বিপদ। ‘ইউনিভার্সিটি’ তো আরও আরও বড়, বেশ কিছু স্কুল-কলেজকেও সে পেটের মধ্যে রেখে দেয় কিন্তু ‘ইউনিভার্স’ তথা মহাজগতের ‘মহা’ তো এরই মধ্যে খরচ করে বিদ্যালয়ের আগে বসিয়ে দিয়ে কলেজের বাংলা ‘মহাবিদ্যালয়’ করা হয়ে গেছে, এখন বিদ্যালয়ের আগে কোন শব্দ বসিয়ে ‘ইউনিভার্সিটি’র বাংলা করা যায় সে নিয়ে নিশ্চয়ই ঝামেলা হয়ে থাকবে! শেষ পর্যন্ত ‘বিশ্ব’ শব্দটা বিদ্যালয়ের আগে বসিয়ে কাজ সারা হলো, আমরা পেলাম ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ অভিধাটি। যদিও ‘বিশ্ব’ শব্দটার ইংরেজি ‘ওয়ার্ল্ড’ হিসেবেই জারি ছিলো তারপরও ইউনিভার্সকে ‘ওয়ার্ল্ড’ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হলো।
বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা কীভাবে তৈরি হয়েছিলো তা ভাবলে বিস্ময় তৈরি হয়। ‘বিশ্ব’ কী বিদ্যালয়ের আগে বসে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ হয়েছে, না কী ‘আলয়’ শব্দটার পূর্বপদ হিসেবে ‘বিশ্ববিদ্যা’ বসিয়ে তা তৈরি হয়েছে? একই প্রশ্ন মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ওঠে। যদি ধরে নেই ‘বিদ্যালয়’ শব্দটার আগে ‘বিশ্ব’ যোগ করা হয়েছে তাহলে এটি পরিষ্কার যে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতরা তাদের ক্ষুদ্র ও অপরিণামদর্শী চিন্তা-বিশ্বের আলোকে ‘বিশ্ব’ শব্দটাকে একটা অবোধ্য ধারণার প্রতীক মাত্র ঠাউরে ছিলেন। বস্তুত, ‘বিশ্ব’ শব্দটা এতো অদ্ভুত অর্থ ধরে যে তা ক্ষুদ্র থেকে সুবৃহৎ সব কিছুকেই ধারণ করতে পারে। এই আমার যেমন একটা বিশ্ব আছে, পিঁপড়ারও একটা বিশ্ব আছে, পৃথিবীরও একটা বিশ্ব আছে, ব্রহ্মাণ্ডেরও একটা বিশ্ব আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কার বা কোন বিশ্বের আলয় আমাদের ‘বিশ্ববিদ্যালয়’? আর যদি ‘সর্ব্ব’ অর্থে ‘বিশ্ব’ শব্দটা বিদ্যার আগে বসানো হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে ‘মহা’ শব্দটা কী অর্থে বিদ্যালয়ের আগে যুক্ত হয়ে ‘মহাবিদ্যালয়’ হলো আর কেন তাহলে ইউনিভার্সিটির বাংলা মহাবিশ্ববিদ্যালয় হলো না? নিখিল, ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবিদ্যালয়ও অবশ্য হতে পারতো! সম্ভবত পশ্চিমে ‘কসমস’ শব্দটা একাডেমিক স্তর-বিন্যাসে কোনোভাবেই হাজির ছিলো না বলে ও যাত্রায় শব্দগুলো রেহাই পেয়েছে!
আবার যদি ‘বিশ্ববিদ্যা’ কথাটার সঙ্গে ‘আলয়’ জুড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় তাহলে স্মরণ করতে হয় যে, বাংলার আদি চিন্তকদের ভাবনায় যে চতুর্দ্দশ বা বত্রিশ বিদ্যা ছিলো তাতে ‘বিশ্ববিদ্যা’ বলে কিছু ছিলো না। এটিও অভিনব সৃজন, যা মহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে কিন্তু মহাবিদ্যাকে অতিক্রম করতে পারে না। অনুমান করি, শুরুতে গুরুতর ঝামেলা হয়নি বলে এই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শব্দত্রয়ী ক্রমাগত প্রচারিতই হয়েছে। কিন্তু যখন ইউনিভার্সিটি কলেজগুলো নিজেদের পরিচয় ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ’ হিসেবে দিতে গেলো তখন চোখ কুঁচকে গেলো তাদের। ‘ইডেন ইউনিভার্সিটি কলেজ’- এর বাংলা কীভাবে করবেন, ‘ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়’? কন্যার গর্ভে মাতার জন্মের ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া আয়েসসাধ্য বলে ইউনিভার্সিটি কলেজ- এর বাংলা আর পুরোটা করার চেষ্টা করেননি কেউ! এ আলোচনায় এই কথাটা উল্লেখ করা দরকার যে, ‘অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন।’ কিন্তু ইউনিভার্সিটির বাংলা হিসেবে ‘সর্ববিদ্যায়তন’ জনমান্য হয়নি। নিশ্চয়ই এর কিছু কারণ থেকে থাকবে। বিগত অন্তত আড়াই শ বছর ধরে শিক্ষিত-বাঙালির ভাব-ভাষা-চিন্তার জগতের প্রায় সব কিছুই চুরি করা। এ অবারিত চৌর্যবৃত্তির কারণেই বাংলায় শব্দসংক্ষেপণের কোনো বিধি না থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ‘ঢাবি’ এবং তার বিদ্যালি ছত্রধর এই আমার পরিচয় ‘ঢাবিয়ান’! এই ঢাবিয়ান শব্দটা এমনভাবে তৈরি যা গাধা ও ঘোড়ার সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া খচ্চরের কথা মনে করিয়ে দেয়!
কোনো একটা ভাব-প্রত্যয় সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে যখন সেই ভাব-প্রত্যয়টি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় তখন শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি- এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপ জানলেও তাদের মানসপ্রকৃতি না জেনেই দখলদার বৃটিশের সহযোগী শিক্ষিত-বাঙালিরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সেসব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তারা অনুকরণেও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে শিক্ষাক্রমের মধ্যবর্তী সোপানের ‘মহাবিদ্যালয়’ নামটি গ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের চুরি বা চৌর্যশাস্ত্র চর্চার পদছাপ রেখে দিয়েছেন। আর ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’ সেই মহাবিদ্যারই চূড়ান্ত প্রকাশ হয়ে উঠতে চেয়েছে। এই যে নকল করার বিদ্যা- এটিকেই স্বাভাবিক করে তুলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার সকল কিছুই নকল করা। এমন কী পাঠ্যসূচিগুলো পর্যন্ত নকল। আরও বিস্ময়কর হচ্ছে, অনুল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে তাদের সকল বিভাগের পাঠ্যসূচি আজও পরভাষায় লিখিত। এই মহাবিদ্যা চর্চাকারীরা দাস্যমনোবৃত্তির কারণে অনুমান করে, পরের ভাষা চুরি করেই তারা বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন পাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে তারা এই চুরি এতোটাই সিনাজুড়ির সঙ্গে করতে শুরু করে যে পুরো দেশের সকল প্রতিষ্ঠান আজ এই ব্যধিতে সংক্রমিত হয়ে গেছে।
বাংলাভাষার আজ যে অবনমন, যে অধস্তন দশা; তার সূতিকাগার ও রূপকার এই ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’। এই অভিনামকে অনুসরণ করে পরবর্তিতে তৈরি হয়েছে ‘উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়’। ‘ঢাকা’ থাকলে ‘উন্মুক্ত’ হতে দোষ কি! এভাবে পরের ভাষা আর পরের ভাবের ঘরে চুরি করাকে অতিস্বাভাবিক করে তোলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে বড় অর্জন ও অপরাধ। জ্ঞান নয়, শিক্ষা নয়, দীক্ষা নয় পরভাষায় অপরিণামদর্শী বিদ্যাচর্চার কলঙ্ককে সে মণিহার করে তুলতে চেয়েছে। এক অর্থে, আজকের বাংলাদেশের যে সর্বগ্রাসী অধঃপতন তার অন্যতম উৎস এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল নিজেই নষ্ট হয়নি, এ দেশের আর সবগুলো প্রতিষ্ঠান নষ্ট করেছে ঢাবি। অধিকাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত অক্ষম অসৎ পাচাটা প্রতিহিংসাপরায়ণ অহমসর্বস্ব শিক্ষিত-বাংলাদেশির জন্ম দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। শত বর্ষের অভিজ্ঞতায় সংশয়হীনভাবে এ কথা বলা যায়, খোলনলচে বদলে ফেলতে না পারলে পাচার ও প্রভুরঞ্জনের আদি ভূমিকার বদল হবে না ঢাবি’র। সেই বদলের অমিত আশা নিয়ে আজ এই ক্ষণে এই টুকু কেবল চাওয়া, দখলদার প্রভূদের ভাব আর ভাষার মহাবিদ্যা চর্চা থেকে বের হয়ে আসুক সে। আর নিদেন পক্ষে দেশের সংখ্যাগরীষ্ঠ মানুষের ভাষায় কথা বলতে শিখুক এই শিক্ষালয়।
লেখক : সহকারী শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



-6999794b2a09a.jpg)