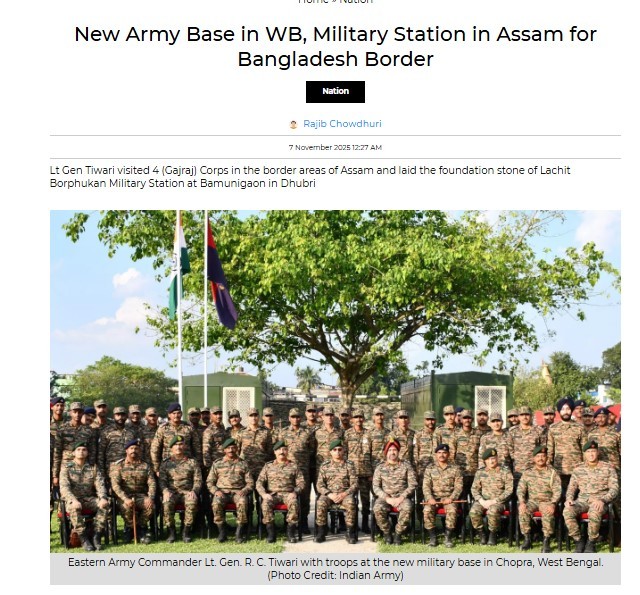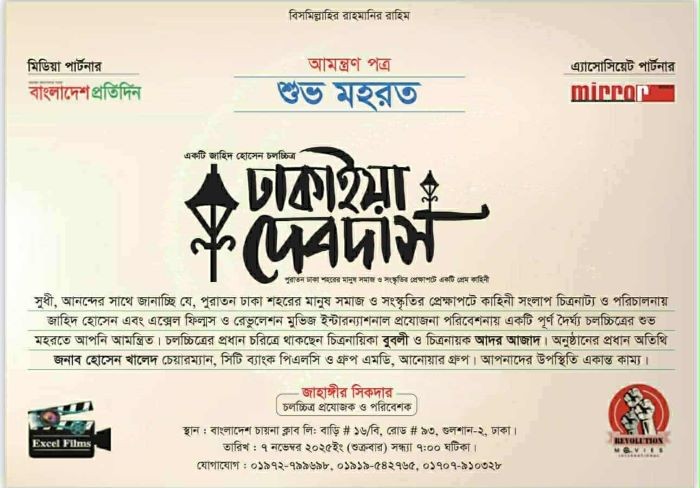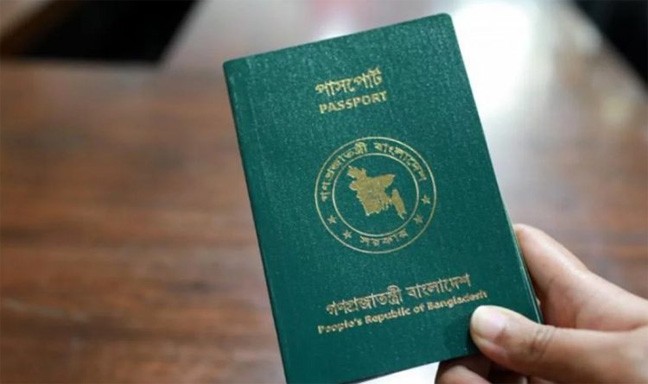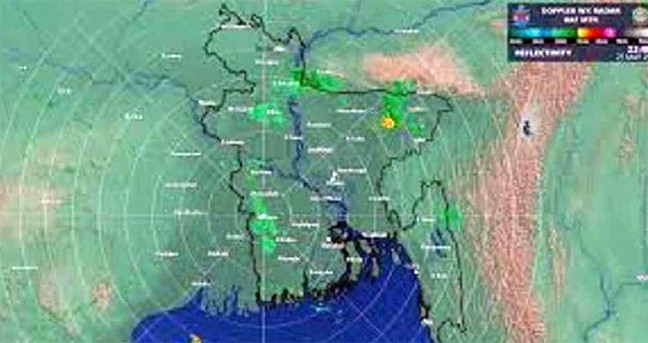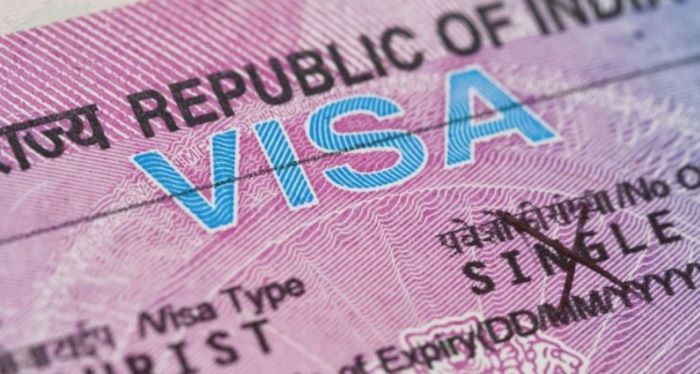বিবিসি বাংলা: সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো বিপজ্জনক। কিন্তু এটাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। যে যত সক্রিয় সাংবাদিক, যে যত বড় দুর্নীতি-অনাচার উন্মোচনকারী তার তত 'পাওয়ারফুল এনিমি' তৈরি হবার আশঙ্কা।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে নিজের দেশের নাগরিকদেরকে বহুবছর প্রহসনের মধ্যে রাখে মার্কিন প্রশাসন। যুদ্ধ জেতা অসম্ভব জেনেও ভিয়েতনামে আরো বাড়তি সেনা মোতায়েনের পরামর্শ দেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারা।
সময়টা ছিল ১৯৬৬ সাল। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মিলিটারি এ্যানালিস্ট ড্যানিয়েল এলসবার্গ। অফিসিয়াল এক ট্রিপ শেষে অ্যামেরিকা ফেরার পথে এলসবার্গের সাথে আলাপকালে মি. ম্যাকনামারা নিজের মুখেই এলসবার্গের কাছে স্বীকার করেন, এই যুদ্ধে অ্যামেরিকার কোনো আশা নেই। অথচ ওই ফ্লাইট থেকে নেমেই সাংবাদিকদের সামনে তিনি পুরাপুরি উল্টা কথা বলেন। এই ঘটনায় মি. এলসবার্গের মোহভঙ্গ হয়।
পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রশাসন দুই দশকের বেশি সময় ধরে জনগণের চোখে ধুলা দিয়ে যাচ্ছিল। তাই, ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নথি মি. এলসবার্গ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্যসমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নথি বা ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টের শত শত পৃষ্ঠা লুকিয়ে ফটোকপি করে কৌশলে বাইরে এনে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাংবাদিককে তিনি দিয়ে দেন।
মি. এলসবার্গের বিরুদ্ধেও গুপ্তচরবৃত্তি ও তথ্য চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। ঘটনার জল গড়িয়েছিল বহুদূর। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছিল আদালত।
ড্যানিয়েল এলসবার্গ 'দ্য পেন্টাগন পেপারস' ফাঁস করার চার দশক পর আসে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা। আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা এনএসএ-র একজন তরুণ বিশ্লেষক, এডওয়ার্ড স্নোডেন হঠাৎ পাড়ি দেন হংকং-এর উদ্দেশ্যে। সাথে নিয়ে যান বিশ্বব্যাপী এনএসএর বেআইনি নজরদারির প্রমাণ। এজেন্সির কম্পিউটার থেকে মি. স্নোডেন 'চুরি' করেন এমন সব তথ্য যা বিশ্ব রাজনীতির ভিত নাড়িয়ে দেবে।
হংকং-এ ২০১৩ সালের জুন মাসে এডওয়ার্ড স্নোডেন সেই তথ্য তুলে দেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড, লরা পয়ট্রাস, বার্টন জেলম্যান এবং ইউয়ান ম্যাকএ্যাসকিলের কাছে । স্নোডেন-এর ফাঁস করা তথ্য প্রথম প্রকাশ করে আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট আর ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা।
আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জবাব ছিল মি. স্নোডেনকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তার মার্কিন পাসপোর্ট বাতিল করা। এর ফলে এডওয়ার্ড স্নোডেন মস্কো বিমান বন্দরে আটকে পড়েন এবং রাশিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।
তার আগে বলি, এ তো গেল 'চুরির মাল' সাংবাদিকের হাতে তুলে দেয়ার কাহিনি। আর জুলিয়ান অ্যাসঞ্জ? তাকে তো বলতে হবে 'ডাকাত সর্দার'। গোয়ান্তানামোর বন্দি শিবিরের নির্যাতন থেকে শুরু করে শিরদাঁড়া শীতল করে দেয়া মার্কিন সরকারের যত আঁতের খবর— সেগুলোও 'জনস্বার্থে'ই পাবলিশ করেছিল জুলিয়ান অ্যাসঞ্জ-এর উইকিলিক্স।
ভয়াবহ পরিণতি
মি. অ্যাসঞ্জ তথ্য পেয়েছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য ব্র্যাডলি ম্যানিংএর কাছ থেকে। পরিণতি ছিল ভয়াবহ। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ব্র্যাডলি - পরবর্তীতে চেলসি - ম্যানিং সাত বছর জেল খাটেন। জুলিয়ান অ্যাসঞ্জ ব্রিটিশ জেল-এ বন্দি, আমেরিকায় তার বিরুদ্ধে যে মামলা আছে তাতে ১৭৫ বছরের সাজা হতে পারে।
ট্র্যাডিশনাল কায়দার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ছাঁচে অ্যাসঞ্জ-স্নোডেনকে মেলানো যাবে না। আমি এদেরকে ডাকি সাংবাদিকতা জগতের 'ডিজিটাল রবিনহুড'। অন্যায়কারীর সিন্দুক ভেঙে তথ্য ও ডকুমেন্ট 'চুরি করে' প্রকাশ করে দেয়াটা ডাকাত 'রবিনহুড'-এরই ডিজিটাল সংস্করণ
এখানে এথিকস বা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলতে চান? নৈতিকতা একটি কনটেক্সুয়াল বিষয়।
নৈতিকতার প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক নেলি ব্লাইয়ের কথা মনে পড়ছে। তাকে কোন অভিধা দেবেন — 'পাগল', 'জোচ্চুর', 'অকল্পনীয় সাহসী'— তা আপনিই ঠিক করুন। সাল ১৮৮৭। স্থান 'ব্ল্যাকওয়েল আইল্যান্ড এসাইলাম' বা মানসিক-রোগীদের চিকিৎসাগার। সেখানকার রোগীরা নির্যাতিত হয় বলে বহুদিনের অভিযোগ। কিন্তু কারো কাছে কোনো প্রমাণ নেই। পারফেক্ট মানসিক-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অভিনয় করে নেলি ব্লাই সেই এসাইলামে ভর্তি হন।
ব্যাপারটাকে সিনেমা ভাববেন না। ওখানে ভর্তি করার আগে রোগীকে ডাক্তারেরা কয়েক দফা পরীক্ষা করে। পেশাদার ডাক্তারকে ঘোল খাইয়ে মিজ ব্লাইকে মানসিক রোগী হিসেবে 'পাশ' করতে হয়।
তেইশ বছর বয়সী নেলি ব্লাই। রোগীদের সাথে এসাইলামে দশ দিন কাটান। সরেজমিনে পরখ করেন নারকীয় সব কাজ-কারবার। ফিরে এসে দুই পর্বের যে রিপোর্ট লিখেছিলেন তিনি, সেই বর্ণনা পড়ে মার্কিন-পাঠক স্তম্ভিত হয়ে যায়।
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কি গুপ্তচরবৃত্তি?
বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার আইনে মামলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগের ভিত্তি কী?
রোজিনা ইসলাম কি গুপ্তচর? তার কি কোনো বিদেশী কানেকশান পাওয়া গেছে? তিনি কি রুশ-বাংলা টিকার চুক্তির তথ্য চীন বা আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে স্পাই হিসেবে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে সচিবালয়ে গিয়েছিলেন? যদি সেটা হয়, রোজিনার বিচার হওয়া দরকার। কিন্তু যদি বিষয়টা এসপিওনাজ কেস না হয়, তাহলে একটু আলাপ বাকি আছে।
রোজিনা ইসলাম একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। বলা হচ্ছে, টিকা নিয়ে উনি রুশ-বাংলা চুক্তির ডকুমেন্ট 'চুরি' করেছিলেন। কী আছে ঐ চুক্তিতে? রোজিনা কি কোনো নয়-ছয়ের গন্ধ পেয়েছিলেন?
মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাস বলছে, জনস্বার্থে ক্লাসিফায়েড নথি প্রকাশ করা ন্যায্য। এমনকি নথি প্রকাশ হলে রাষ্ট্রীয় গোমর ফাঁস হয়ে গেলেও। গোমর রক্ষার নামে জনতাকে প্রহসনে রেখে রাষ্ট্র ও জনগণের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি ডেকে আনা অন্যায়।
তিরস্কারই যখন 'ব্যাজ অফ অনার'
আদিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ডাকা হতো 'মাকরেকার'। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাথে ক্ষমতাবানদের বৈরিতা নতুন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট অনুসন্ধানী সাংবাদিকদেরকে তিরস্কার করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মাকরেকার'। মানে, ডার্ট-ডিগার। অর্থাৎ ময়লা-নোংরা ঘাঁটা নিচু শ্রেণির লোক। কারণ তারা দুর্নীতিবাজ ক্ষমতাবানদের হাঁড়ির খবর ঘাঁটেন। অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ-দলিল সংগ্রহ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন।
কিন্তু রুজভেল্টের এই অপমান ও তিরস্কারে সাংবাদিকেরা দমে না। উল্টা তাচ্ছিল্যভরা গালিটাকেই তারা নিজেদের 'ব্যাজ অফ অনার' হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ তারা কাউকে খুশি করতে সাংবাদিকতা করে না। কর্পোরেশন্স ও ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি-অনিয়মের খবর প্রকাশ করে সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখাই তাদের অঙ্গিকার। তারা গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে এবং জনগণকে সদা জাগ্রত রাখতে ভূমিকা রাখে। সমাজের ভালো করতে গিয়েই তারা ক্ষমতাবানদের রোষানলে পড়ে।
সত্তরের দশকে অ্যামেরিকায় ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডাল নিয়ে কাজ করছিলেন কার্ল বার্নস্টাইন ও বব উডওয়ার্ড। অনুসন্ধান করতে-করতে তারা যখন দোষী ক্ষমতাবানদের আঁতের খবর জেনে ফেলে তখন তাদেরও প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। তাদের বাড়িঘর, ফোন সবখানে আড়িপাতা হয়।
বিনোদন বিট বা ডেইজ ইভেন্টস কাভার না করে অনুসন্ধানী সাংবাদিক সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকায়। তাই ক্ষমতাবানের রোষে পড়ে তারা হত্যা-নির্যাতন, জেল-জুলুমের শিকার হয়।
রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স জানাচ্ছে, ২০২০ সালেও ৫০ জন সাংবাদিক নিজেদের কাজের জেরে খুন হয়েছেন। দেশে দেশে খুন হওয়া রিপোর্টারেরা মূলত সংগঠিত অপরাধী চক্রের অপরাধ, ক্ষমতাবানদের দুর্নীতির অনুসন্ধান করছিলেন এবং পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলেন। ২০১৯ সালেও খুন হন ৪৯ জন সাংবাদিক।
সমাজের উপকার করার খেসারত এভাবে বহু সাংবাদিককেই দিতে হয়। তাই, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমকে 'এডভারসারিয়াল জারনালিজম' নামেও চিহ্নিত করা হয়।
অপরাধী ও দুর্নীতিবাজেরা চিরকালই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের মুণ্ডপাত করে। কিন্তু গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডাল, ভিয়েতনাম যুদ্ধের তথ্য নিয়ে প্রহসন, 'ক্রেস্টের সোনার ১২ আনাই মিছে' বা রূপপুরে বালিশ কেনার মতন পুকুর চুরির ঘটনা উন্মোচনের মাধ্যমে সমাজের সেবা করেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। তাই এটিকে 'পাবলিক সার্ভিস জারনালিজম' নামেও ডাকা হয়।
এই প্রসঙ্গেই 'ম্যাকক্লার ম্যাগাজিন'-এর কথা মনে পড়ছে। ১৯০৩ সাল। সম্পাদক টমাস ডাব্লিউ লসন। ম্যাকক্লার ম্যাগাজিনের 'পরের সংখ্যায় না-জানি কার খবর বের হয়'— ভেবেই তখন দুর্নীতিবাজদের গলা শুকিয়ে যেতো।
শুনতে গালগপ্পো মনে হচ্ছে! কিন্তু বাস্তবটা আরো 'এক্সাইটিং'। ওই অবস্থা সামাল দিতেই তখন পেশাদার সাংবাদিকদেরকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পাবলিক রিলেশন্স বা জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিতে শুরু করে বেনিয়া কর্পোরেশনগুলো। এর ভেতর দিয়েই জন্ম নেয় আধুনিক পাবলিক রিলেশন্স।
সোর্সই কি অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ঈশ্বর?
হ্যাঁ। যে সাংবাদিকের 'সোর্স' বা 'সংবাদ দেবার উৎস' যত বেশি, সেই সাংবাদিক তত বেশি এগিয়ে।
আবারো ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডালের স্মরণ নিচ্ছি। এই ঘটনা নিয়ে চলচ্চিত্র 'অল দি প্রেসিডেন্টস ম্যান'। সেখানে দেখবেন, 'ভেরিফাই' না করে তথ্য প্রকাশ করে কী বিপদেই পড়েছিলেন বব উডওয়ার্ড আর কার্ল বার্নস্টেইন। অনেক সময় তথ্য দেবার নাম করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য ফাঁদ পাতা হয়।
তাই, একক সোর্সের উপরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা নির্ভর করে না। দ্বিতীয় বিশ্বস্ত সোর্স দিয়ে তথ্য 'ভেরিফাই' করিয়ে নেয়।
সোর্সের পরিচয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করাও অনুসন্ধানী সাংবাদিকের অবশ্য কর্তব্য। সাংবাদিকতার ইতিহাসে এমন উদারণও আছে, মামলা খেয়ে সাংবাদিক কারাবরণ করেছে। তবু, তার সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করেনি।
সোর্সের পরিচয় গোপন রাখার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী উদাহরণ হলো 'ডিপথ্রোট'। ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডালে সিআইএ থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন মহলের সম্পৃক্ততা উন্মোচন হতে থাকে। কিন্তু এসব তথ্য ভেরিফাই করা না গেলে ব্যবহার করা যাবে না। তখন, উদ্ধারকর্তা হিসেবে নামপরিচয় গোপন রাখার শর্তে রাজি হন এক সোর্স। উডওয়ার্ড ও বাবার্নস্টেইনের প্রতিবেদনগুলোতে অতি উচ্চ পদে থাকা সেই সোর্সকে 'ডিপথ্রোট' হিসেবে উল্লেখ করা হতো।
ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করেন। এরপর গড়িয়ে গেছে প্রায় তিরিশ বছর। তবুও 'ডিপথ্রোট'-এর পরিচয় সাংবাদিকেরা প্রকাশ করেননি। অবশেষে, ২০০৫ সালে জানা যায় 'ডিপথ্রোট'-এর আসল পরিচয়। তিনি আর কেউ নন, তৎকালীন এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর মার্ক ফেল্ট।
সাংবাদিকের রক্ষা কবচ
সারা পৃথিবীতেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের পদে পদে চ্যালেঞ্জ। অ্যামেরিকার মতন দেশ— গণতন্ত্র যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুন বেশি সমুন্নত, যেখানে জন পরিসরে কথা বলার স্বাধীনতা অনেক বেশি, যেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষিত— সেখানেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা ঝুঁকি মুক্ত নন।
তাহলে, আমাদের মতন বেশি দুর্নীতি, সীমিত স্বাধীনতা ভাগকারী গণমাধ্যম ও দুর্বল গণতন্ত্রের দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কী দশা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।
বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সক্রিয় হলো ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন। পান থেকে চুন খসার আগেই এই আইনে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া যায়। বিপদের উপর আপদ হিসেবে জুটেছে উপনিবেশিক আমলের নিবর্তনমূলক অফিসিয়াল গোপনীয়তা রক্ষার কাল আইন। এদেশে এখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করাটা মাইনফিল্ডের উপর দিয়ে হাঁটার মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তাহলে, কোন ভরসায় টিনের তলোয়াড় নিয়ে ক্ষমতাবানদের বিপক্ষে যুদ্ধে নামে অনুসন্ধানী সাংবাদিক? তাদের শক্তির উৎস কী? উত্তর দেয়ার আগে আপনাদেরকে স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালিত সিনেমা 'দি পোস্ট' এবং টম ম্যাকার্থি পরিচালিত 'স্পটলাইট' দেখতে পরামর্শ দেবো। আর এলান যে পাকুলার 'অল দি প্রেসিডেন্টস ম্যান' তো অবশ্যই দেখবেন।
তিনটিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। সিনেমাগুলো আপনার কাছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চেহারাটাকে স্পষ্ট করে তুলবে।
জনস্বার্থ, জনস্বার্থ এবং জনস্বার্থ
এবার উত্তরটা দিই। অনুসন্ধানী সাংবাদিকের রক্ষাকবচ হচ্ছে 'পাবলিক ইন্টারেস্ট' বা জনস্বার্থ। জনস্বার্থ, জনস্বার্থ এবং জনস্বার্থ।
নথি যত গুরুত্বপূর্ণ, গোপনীয় ও ক্লাসিফায়েডই হোক না কেন 'জনস্বার্থে' তা প্রকাশযোগ্য। মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাসে সেই দৃষ্টান্তই সৃষ্টি হয়। সরকারের গোপন নথি প্রকাশ করার পর নিউ ইয়র্ক টাইমসকে আদালত তা আর না ছাপানোর হুকুম দেয়। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে ওয়াশিংটন পোস্ট। তাদেরকেও পরে আদালতের শরণ নিতে হয়। এক্ষেত্রে, আদালতেও জনস্বার্থেরই জয় হয়।
সরকার, রাজনীতি, রাষ্ট্র বা ধর্ম— কোনো লেবাসেই জনগণকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। আর ধোঁকা দিলে সেই তথ্য জনগণকে জানিয়ে দেয়াই সাংবাদিকের ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে পাদ্রীদের দ্বারা শিশু-কিশোরদের যৌন নির্যাতনের কাহিনি উন্মোচনের ঘটনাটা উল্লেখ করতেই হচ্ছে।
বোস্টনে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা বছরের পর বছর ধরে শিশুদেরকে যৌন নিপীড়ন করেছে। ভেতরে ভেতরে এসব অনেকেরই জানা। কিন্তু, ধর্মের 'মান খোয়াবে' বলে সেগুলো সমাজের হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যোগশাজসে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে।
সিস্টেমিক যৌন নিপীড়ন
কিন্তু ধর্মের মুখোশধারীদের অপকর্ম প্রকাশের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বোস্টন গ্লোব পত্রিকা। তারপর বের হতে থাকে সিস্টেমিক ভাবে যৌন নিপীড়নের ডজন ডজন ঘটনা।
ধর্মীয় লেবাস নিলেই বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় থাকলেই যে ব্যক্তির অপরাধ তামাদি হয়ে যায় না সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা পায় বোস্টন গ্লোবের ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। এই সিরিজ প্রতিবেদনের জন্য বোস্টন গ্লোব পত্রিকাকে ২০০৩ সালে পাবলিক সার্ভিস ক্যাটাগরিতে পুলিৎজার পুরস্কার দেয়া হয়।
কর্তারা যা লুকাতে চায় তাই সংবাদ। কেননা সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। সাংবাদিকতাকে বলা হয় সমাজের 'ওয়াচ ডগ' বা প্রহরী। শক্তিশালী সাংবাদিকতা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রকে পাহারা দেয়। প্রহরা দুর্বল হলে পাঁচ ভূতে লুটে নেবে সোনার সংসার।