
ডেস্ক রিপোর্ট : মহামারী মানেই মৃত্যু, চারপাশে মানুষের হাহাকার ও দুর্বিষহ কষ্ট। তবু মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় নতুন আশা নিয়ে। এত কিছুর পরও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, মহামারী মানুষকে নতুন অনেক কিছু শেখায়, সচেতন করে স্বাস্থ্য নিয়ে। বিভিন্ন সময় মহামারী শেষে ঘটেছে নানা অগ্রগতি। লিখেছেন আরফাতুন নাবিলা
দরিদ্রদের উন্নতি
মধ্যযুগে ইউরোপের মহামারী প্লেগ রোগকে বলা হয় ব্ল্যাক ডেথ। ১৩৫০ দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে এই মহামারীর ভয়াবহতা। ইউরোপের প্রায় ৩০-৬০ শতাংশ জনগণের মৃত্যু হয় মহামারীর প্রকোপে। ইতিহাসে মহামারীর যত তালিকা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাওয়ার রেকর্ড এই ব্ল্যাক ডেথেই। ১৩৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক অঞ্চলই ব্ল্যাক ডেথের সংক্রমণের শিকার হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই এই রোগ ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, আফ্রিকাসহ মধ্যপ্রাচ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ারের কিছু গ্রামের ৭০ শতাংশ জনগণই মারা যায় প্লেগের ছোঁয়ায়।
১৩৪৮-৪৯ সালে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয় পাহাড়ি অঞ্চল এবং তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোতে। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ইতালির ফ্লোরেন্সে প্লেগের কারণে প্রায় ৬৫,০০০ বাসিন্দা মারা যায়। ১৩৫৩ সালে এই মহামারী শেষ হলেও পরবর্তী শতকগুলোতেও এর আক্রমণ হতে থাকে। তবে পরে ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি হতে থাকায় এর সংক্রমণ কমতে থাকে। ফলে ১৪তম শতাব্দীতে ইউরোপকে ধ্বংসকারী ব্ল্যাক ডেথের ফলে সমাজের বিশাল অংশগুলোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন হয়, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমজীবীদের মধ্যে। ব্ল্যাক ডেথের কারণে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমে যায়। যারা কাজ করতে পারতেন বেড়ে যায় তাদের পারিশ্রমিক। অত্যাচারী প্রথা ভূমিদাসত্বের প্রকোপ কমে আসে অনেকখানি। লোকরা সে সময় যে শুধু কাজ পেয়েছিল তাই নয়, দেখা মেলে উন্নত জীবনযাপনেরও।রিচমন্ড ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রফেসর ডেভিড রট বলেন, ‘ব্ল্যাক ডেথের পর কৃষিশ্রমিকরা তাদের জমির মালিকের কাছ থেকে নিজেদের কাজের জন্য ভালো পারিশ্রমিক পেতে শুরু করেন। শহরগুলোতেও প্লেগ ছড়িয়েছিল ভয়াবহ আকারে। সেখানে কর্র্তৃপক্ষ মহামারীতে স্যানিটেশনের বিষয়ে আরও সচেতন হয়। জনগণ যেন এই সচেতনতা মেনে চলে তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিছু শহরে চালু করা হয় কোয়ারেন্টাইন-পদ্ধতি। বলতে গেলে এই কোয়ারেন্টাইন-পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে চলার কারণেই প্লেগের প্রকোপ কমে আসে।’
ব্ল্যাক ডেথ বড় ব্যবসায়ীদের চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনে। তারা বুঝতে পারেন তাদের তৈরি করা ব্যবসা বা দেশপ্রেম যাই বলা হোক না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। তাই তারা তাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে দান করে যান। একদম বৃহৎ থেকে শুরু করে ছোট ছোট অনেক কোম্পানি এই দানের থেকে লাভবান হয়। ভূমিদাসত্ব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলোতে শ্রমিকদের যেকোনো কাজের মূল্য পরিশোধ করা হতো নগদ অর্থে। বাকি রাখার সব পদ্ধতি তখন বন্ধ হয়ে যায়। যে ব্যবসায়ীরা বৃহৎ আকারে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করতেন, তারাও অর্থ জমিয়ে নিজেরাই সেই জিনিসের উৎপাদন শুরু করেন। যেমন একসময় এশিয়া ও প্রাচীন গ্রিকের বাইজেন্টিয়াম শহর থেকে সিল্ক আমদানি করা হতো। সেগুলো পরে ইউরোপেই উৎপাদন করা হয়। ধনী ইতালিয়ান ব্যবসায়ীরা সিল্কের ও পোশাকের দোকান দেওয়া শুরু করেন। এই ব্যবসায়ীরা যাদের দিয়ে কাজ করাতেন তাদের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পরিশোধ করে দিতেন ব্ল্যাক ডেথের কারণে। ব্ল্যাক ডেথের পর বুননশিল্পীদের হাতে কাজ ছিল না, যার ফলে তারা মেশিন কিনতে পারতেন না। আবার অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিদের কাছে নগদ অর্থ ছিল। ধনীদের থেকে এই নগদ অর্থ নিয়ে বুননশিল্পীদের শর্তসাপেক্ষে নতুন প্রযুক্তির মেশিন কিনে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, দুই পক্ষই এতে লাভবান হয়। বলতে গেলে, মহামারীর পর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের অবস্থার বেশ ভালো পরিবর্তন হয়।
চিকিৎসা সেবার বিকাশ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিহত হওয়ার ক্ষত দূর হতে না হতেই পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল এক মরণব্যাধি রোগ। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে এক মার্কিন সৈনিকের শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল। আগস্ট মাস আসতেই ঝড়ের গতিতে ছড়াতে শুরু করে রোগের মহামারী। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে আক্রমণ হলেও পৃথিবীর কোনো দেশই রক্ষা পায়নি এ জ্বরের ছোবল থেকে। ‘স্প্যানিশ ফ্লু’ নামে সেই মহামারীতে পরের দুই বছরে পুরো পৃথিবীতে পাঁচ কোটি মানুষ মারা যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে মৃতের এ সংখ্যা ১০ কোটির কম নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক এবং বিধ্বংসী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল এইচওয়ানএনওয়ান নামে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি। বলা হয় দুই বিশ্বযুদ্ধে যত প্রাণ গেছে, তার চেয়েও বেশি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে স্প্যানিশ ফ্লু। প্রাণঘাতক হলেও অস্বীকার করা যাবে না যে, এই মহামারীর পরই আমেরিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।
১৯২০ সালে, অনেক দেশের সরকার প্রতিরোধমূলক এবং সামাজিকীকরণের নানা ওষুধ নিয়ে কাজ শুরু করে। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ অনেকে কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্মীভিত্তিক বীমা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে। দুটি পদ্ধতিই মহামারী-পরবর্তী সময়ে সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন হতে সাহায্য করে। হারিসবার্গ ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষজ্ঞ ন্যান্সি মিম বলেন, ‘চিকিৎসকরা কেবল অসুস্থতা নিরাময়ের ব্যাপারে নয়, মনোনিবেশ করেছিলেন পেশাগত ও সামাজিক দুই অবস্থার দিকেই। তারা বুঝতে পেরেছিলেন মহামারী-পরবর্তী সময়ে অসুস্থতা না থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তাই তারা এসব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন।’ এডেলফি ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রফেসর কেলি রনেন বলেন, ‘এ সময়ে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তার চেয়েও বেশি মহামারীর নিদর্শন, কারণ এবং প্রভাব নিয়ে অনুশীলন করা হয়েছিল সে সময়। রোগীদের যতœ নেওয়ার জন্য ছোট থেকে ছোট বিষয়েও নজর রাখা হতো। হাসপাতালগুলোতে উন্নত স্বাস্থ্যপরিচ্ছন্নতার জন্য কাঠের বিছানার বদলে ধাতুর তৈরি বিছানা ব্যবহার করা হয়। জনস্বাস্থ্যের সংকটগুলোতেও বড় বড় পরিবর্তন আসতে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মহামারী আসাতেই হাম, মাম্পস, রুবেলা, ম্যালেরিয়া, পোলিওসহ নানা রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। যার কারণে পরবর্তী অনেক মহামারী রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।’
পোশাকে বদল
অতীত বলে, সামাজিক দূরত্বের বেশ বড় ইতিহাস ছিল। আগের মহামারীগুলোর সময় চিকিৎসক, রোগী, সাধারণ জনগণ নিজেদের মধ্যে চেষ্টা করতেন দূরত্ব মেনে চলার। মধ্যযুগীয় চিকিৎসকরা লম্বা ঠোঁটের মতো (পাখির ঠোঁট আকৃতির) এক ধরনের মাস্ক ব্যবহার করতেন। এগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হতো যেন চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে দূরত্ব থাকে। বিশ্বাস করা হতো, প্লেগ বাতাসের মাধ্যমে জীবাণু ছড়ায়। রোগীদের ঘরে প্রবেশ করলে বাজে দুর্গন্ধের কারণে বাতাস দূষিত হতো, ফলে চিকিৎসক সেই ঘরে গিয়ে রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এ সমস্যা দূর করার জন্য তাদের হাতে অথবা নাকে সুগন্ধী কোনো পাতা বা ফুল রাখা হতো। নাকে যেন সহজে সেগুলো নেওয়া যায় সে কারণে লম্বা পাখির ঠোঁটের মতো মাস্ক ডিজাইন করা হতো। এতে করে দুর্গন্ধের বদলে নাকে সুবাস লেগে থাকত। এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ছিল ১৬৬৫ সালের ‘গ্রেট প্লেগ’-এর সময়। সে সময় বলা হয়েছিল, এই রোগটি ছড়াচ্ছিল মাছি ও ইঁদুরের মাধ্যমে। শুধু মাস্ক নয়, চিকিৎসকরা আরও পরতেন তেল ও মোম লাগানো মেঝে পর্যন্ত লম্বা কোট, মাথায় থাকত লম্বা টুপি বা কোটের হুড, হাতে গ্লাভস। নিজে পরিচ্ছন্ন তো বটেই, মাছি যেন শরীরে বসতে না পারে সেজন্যও পরা হতো এ ধরনের পোশাক। এই পোশাক বেশির ভাগ সময়েই নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যরে চেয়ে বেশি লম্বা হতো। সে সময় চিকিৎসকদের হাতে নকশা করা সুন্দর এক ধরনের ছড়ি থাকত। এই ছড়ি হাতে দেখলে রোগীরা চিকিৎসকের চিকিৎসার ওপর বেশি ভরসা করতেন। যার ছড়ি যত সুন্দর, তিনি তত বেশি সফল। অনেকের ছড়িতে হাত রাখার জন্য হ্যান্ডেল থাকত। রাস্তায় কোনো ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হয়েছেন সেটি বোঝার জন্য চিকিৎসকরা তাদের সরাসরি হাত দিয়ে না ছুঁয়ে ছড়ি দিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলতেন। অদ্ভুত সে সময়ের চিকিৎসকদের পোশাককে এখনকার হ্যালোইন পোশাকের রেপ্লিকা বললে ভুল বলা হয় না কিন্তু পোশাক যেমনই হোক, রোগ থেকে দূরে থাকতে যে সামাজিক দূরত্ব আবশ্যক সেটি বলাবাহুল্য।
শুধু চিকিৎসকদের মধ্যে নয়, সামাজিক দূরত্ব ছিল সাধারণ জনগণের মধ্যেও। তবে পুরুষের চেয়ে নারীদের পোশাকে দূরত্ব নকশা বেশি দেখা যেত। নারীরা যে স্কার্ট পরতেন, সেটি ছিল ঘোড়ার লোম, সুতা বা লিনেন দিয়ে বানানো ক্রাইনোলাইন কাপড়। হুপ স্কার্ট বানিয়ে তার ওপর এই কাপড় দিয়ে পোশাক বানানো হতো। যার কারণে অন্যজনের সংস্পর্শে আসতে দূরত্ব এমনিতেই বজায় থাকত। ১৯ শতকের মাঝামাঝি এই পোশাকটি নারীদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি নারীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়।
বাড়ির নকশায় পরিবর্তন
মহামারীর কারণে শহর পরিকল্পনা ও নকশায় বেশ পরিবর্তন আসে। শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে ১৯০৬ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে ‘সøাম কোর্ট’ একটি হাউজিং কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২০ সালের দিকে এই কমিশনে ব্যক্তিসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কমিশন ও সিটি কাউন্সিল মিলে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রচারণা করে, বাড়ি মেরামত এবং পানির সঠিক প্রবাহের জন্য ৩০ শতাংশ জায়গা উন্মুক্ত রাখার জন্য বলে।
১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর পর, সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিকে উদ্বুদ্ধ করতে বাড়ির নকশাগুলোতেও আনা হয় পরিবর্তন। এই মহামারীর পর স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা দেখতে পান, শহুরে বাড়িগুলো এতটা কাছাকাছি যে, রোগ ছড়ায় আরও সহজে। বিষয়টি নিয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা করা হয়। ১৯৩০ সালে ফ্র্যাংক্লিন ডি রুজভেল্ট (নিউ ইয়র্কের গভর্নর) নিয়ম জারি করেন এলাকার প্রতিটি বাড়িতেই যেন আগুন নির্বাপণব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে রাখা হয়, মূল হলওয়ে যেন তিন ফিট প্রশস্ত হয় এবং আলাদা আলাদা বাথরুম থাকে।
নতুন শিল্প-সাহিত্য
মহামারীতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বিষহ জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছে অগণিত মানুষকে। পরে শিল্পীরা তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা তুলে ধরেন চিত্রকর্ম, সাহিত্য আর সংগীতের মাধ্যমে।
ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মেডিকেল হিউম্যানিটিজ প্রোগ্রামের কো-ফাউন্ডার এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ রেবেকা মেসবার্গার বলেন, “মধ্যযুগীয় লেখক জিওভানি বোকাসিও তার বিখ্যাত কাজ ‘দ্য ডেকামেরন (১৩৫১)’ তৈরি করেছিলেন ১৩৪৮ সালের বুবনিক প্লেগের মধ্যভাগে। নিজ শহর ফ্লোরেন্সে দেখা ভয়াবহতা নিয়ে লিখেছিলেন তিনি।” লেখালেখির এই তালিকা ছিল আরও দীর্ঘ। ১৭ শতকে ইউরোপ জুড়ে ভয়াবহতা ছড়ানো প্লেগ মহামারী নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন ব্রিটিশ লেখক ড্যানিয়েল ডিফো এবং ইতালিয়ান লেখক আলেসান্দ্রো মানজোনি। ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা সংকট সাহিত্যের আরও কিছু কাজকে ২০ শতকের শুরুতে বেগবান করে। এর মধ্যে আছে টি এস ইলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের দ্য সেকেন্ড কামিং, ভার্জিনিয়া উলফের মিসেস ডালওয়ে। ১৯৮০ সালে এইডস মহামারীর পর পরিচিতি পান ডেভিড ওজনারোউইকজ, থেরেসা ফ্রেয়ার এবং কিথ হ্যারিংয়ের মতো কয়েকজন লেখক। এই শিল্পীরা রোগ দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষয়রোগ নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলোকে গ্রাফিক চিত্রে অনুবাদ করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সময়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগতিপূর্ণ শক্তি দ্বারা লুকিয়ে রাখা হতো। বলা যায়, মহামারীর পরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েছে।
সূত্র : দেশ রূপান্তর

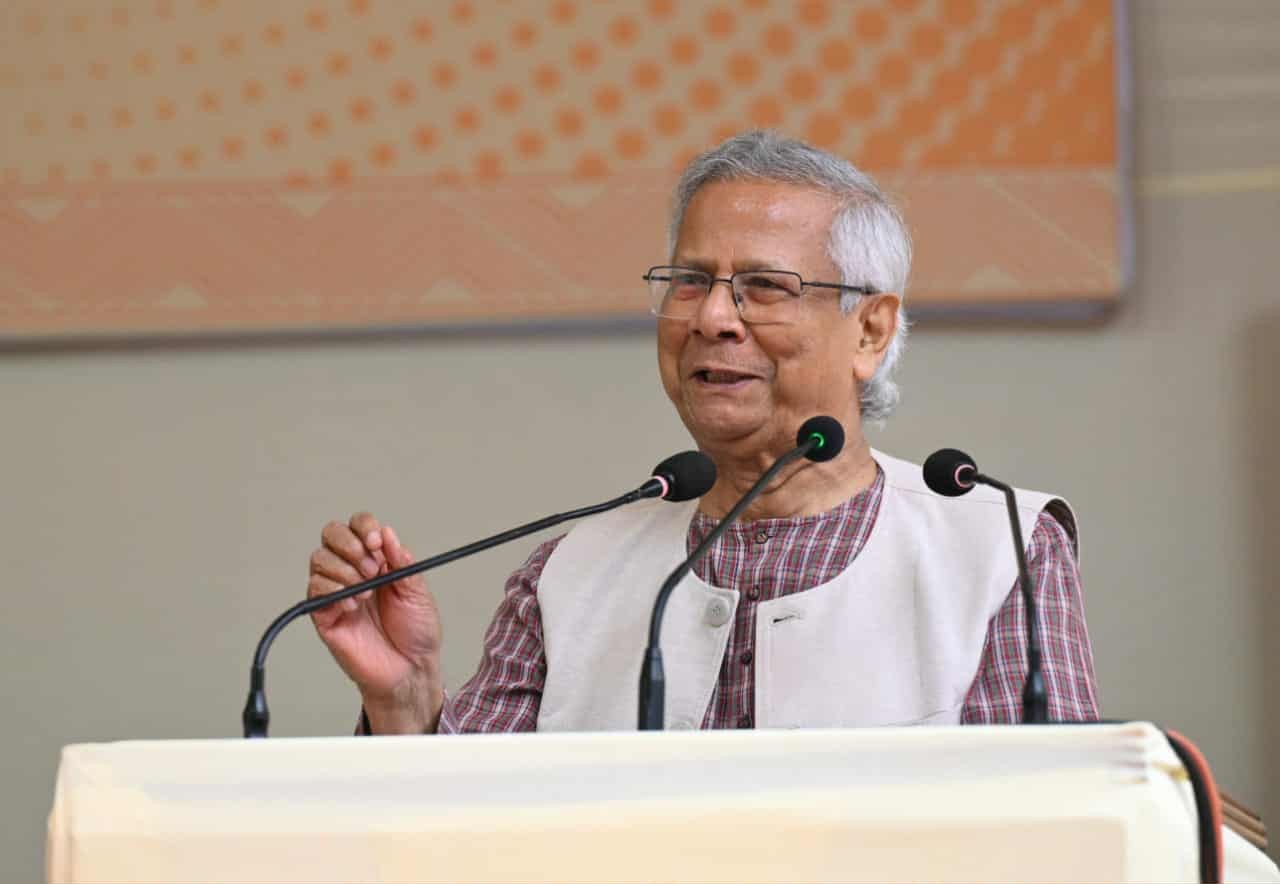
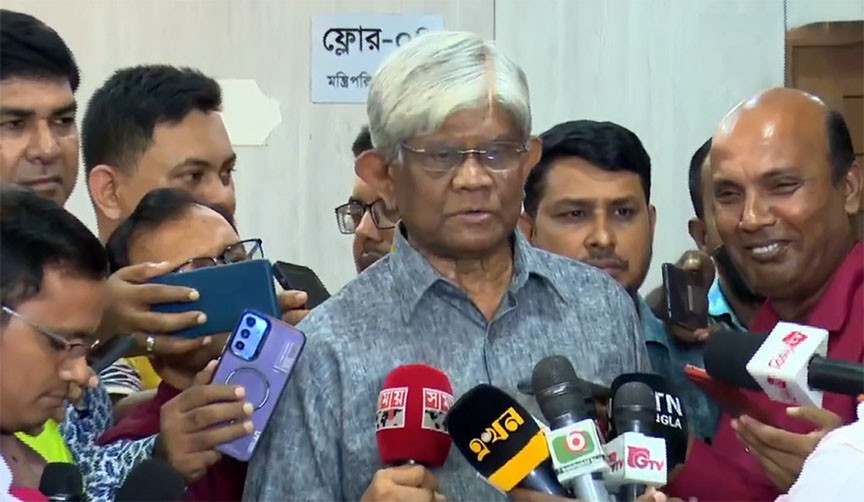










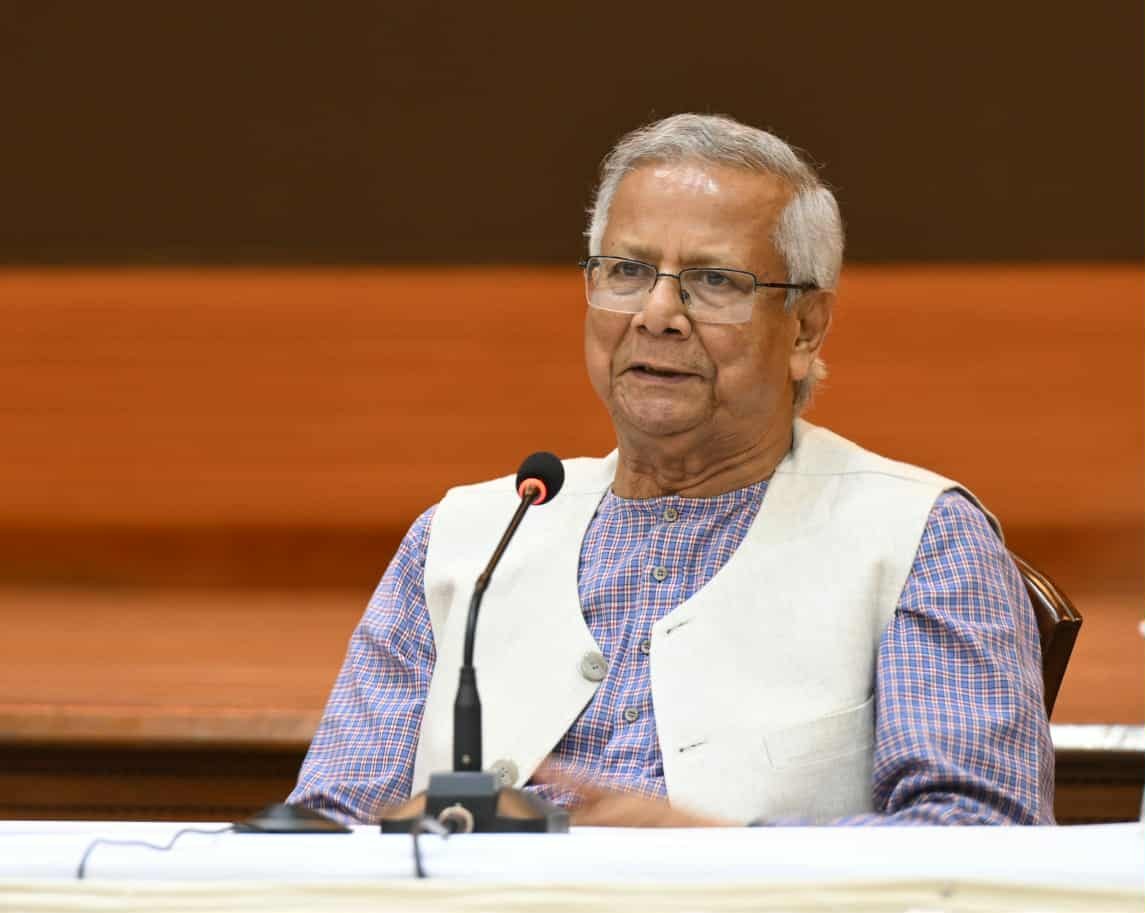




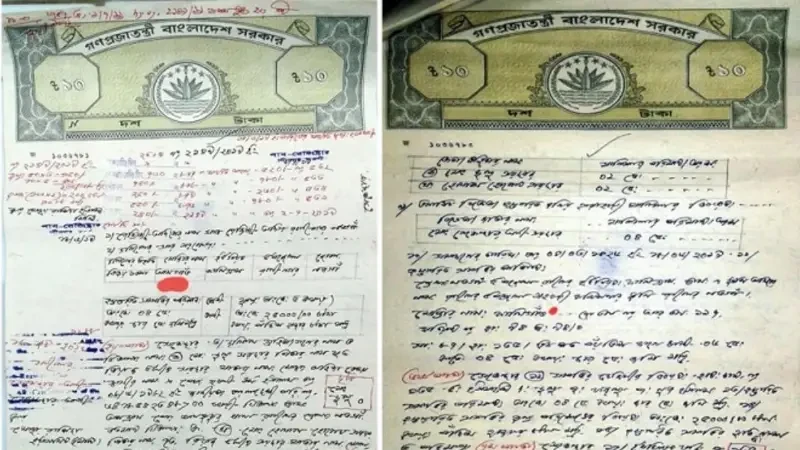

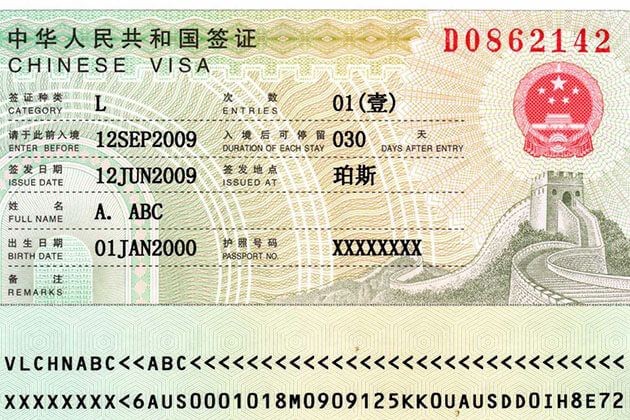







_School.jpg)


