
ড. আতিউর রহমান : বিগত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতির রূপান্তর, এক কথায়, বিস্ময়কর। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের পর্দা স্তরে স্তরে উন্মোচিত হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি খাত (শিল্প, সেবা ও কৃষি) একই লয়ে পাশাপাশি বেড়ে চলেছে। সচরাচর এমনটি ঘটে না। একটি বাড়লে আরেকটি থমকে থাকে বা খুব ধীরে বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ যেন ব্যতিক্রমী এক দেশ। এখানে সব খাত একযোগে বাড়ছে। আরও অবাক বিষয় হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশে কম খরচের শিল্পায়নের উড্ডয়নে (‘টেক-অফ’) এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে বাংলাদেশ। আর এমন একসময়ে এই উড্ডয়ন ঘটছে যখন সারাবিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার খুবই দুর্বল। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, এটি যেন এক লুকানো গুপ্তধন। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত আট বছরে বাংলাদেশে সোনার তরীটি যেন সোনার ফসলে ভরে উঠেছে। এখন কেবল পাকিস্তানই নয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশ নানা দিক দিয়ে ভালো করছে। বিশ্ব শান্তি সূচকে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিয়ে বিশ্ব নেতারা বাংলাদেশের প্রশংসা করছেন।
সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল থেকে ভালো অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার যেকোনো দেশকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীর ৩৪ শতাংশ এখন কর্মে নিয়োজিত, যেখানে পুরুষের হার ৮২ শতাংশ। এই ৩৪ শতাংশকে যদি পুরুষের কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাবে। অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। সরকারের বাজেটীয় উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নধর্মী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককেই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে ব্রতী করেছে। ফলে কৃষি ও খুদে খাতে প্রচুর অর্থায়ন ঘটেছে। এর ফলে দেশীয় চাহিদা ও বাজার যেমন বেড়েছে, তেমনি সরবরাহও বেড়েছে। দুইয়ে মিলে মূল্যস্ফীতিকে ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীলও কমিয়ে এনেছে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে এই আর্থিক স্থিতিশীলতা খুবই সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।
বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা পরিশ্রমী। তারা অনেক বেশি রিজিলিয়েন্ট। এ দেশের মানুষের মধ্যে একটা সহনীয় ক্ষমতা আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি আছে। লড়াকু মন রয়েছে। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হলেও এ দেশের মানুষ কাজ করে সেটা পুষিয়ে দেন। সেটির প্রমাণ গত এক যুগ ধরে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। আর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে উত্তম। ভারত বা শ্রীলঙ্কার জিডিপি প্রবৃদ্ধির মধ্যে অনেক ওঠানামা হয়। গত আট অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধি আরো ভালো, প্রায় ৬.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিলো ৫ শতাংশ, সেখানে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি পৌঁছে গেছে ৭-এর ঘরে (৭.১১ শতাংশ)।
এটি আমাদের জন্য সত্যিই সুসংবাদ। বাংলাদেশ এখন ৭-৮ শতাংশের মতো তার প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ঝুঁকি সমন্বয় করার পরেও যে মুনাফা অর্জন করে তা আশপাশের সব দেশ থেকে বেশি। তাই ঝুঁকি নিয়েও তারা বাংলাদেশেই বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন। আর বিরাট সংখ্যক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার যে সাহসী উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়নে সফল হলে আগ্রহী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের লাইন পড়ে যাবে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বরাবরই অন্তর্ভুক্তিমূলক। এ প্রবৃদ্ধি সকলেই ভাগ করে নিচ্ছে। দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের হারই প্রমাণ করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কতোটা গুণমানের। এর পেছনে চালিকাশক্তি হিসেব কাজ করেছে এবং এখনও করছে কৃষি, গার্মেন্টস খাত ও রেমিট্যান্স। এসবই দারিদ্র্য নিরসনে বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ৫০ শতাংশ, জীবনের আয়ু বেড়েছে ৩০ বছর। অনেক দেশে একশো বছরেও এমন সাফল্য আসেনি। আর সাফল্যের এই গতি দ্রুত লয়ে বেড়েছে বিগত আট বছরে।
অতি দারিদ্র্যের হার প্রায় ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, বিধবা যাদের একটা অংশ কোনো উপার্জনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত নেই। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় তাদের ভাতা দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের হাতে ভাতা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অতি দারিদ্র্যের এই হার অচিরেই এক ডিজিটে নেমে আসবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে ৭ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অর্জনে মাথাপিছু আয় বাড়াতে হবে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি দুর্দশার মধ্যে পড়লেও আমরা তা থেকে দূরে থাকতে পারবো। এরই মধ্যে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। বিশ্বমন্দার মধ্যেও আমাদের জিডিপি, মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কিন্তু বেড়েছে। গ্রাম পর্যন্ত প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। মানুষের হাতে হাতে এখন মোবাইল। তার মাধ্যমে সবাই টাকা লেনদেন করছেন।
কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয় পণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে। আর্থিক খাতের অগ্রযাত্রা জাতীয় অর্থনীতির সূচকগুলোকে স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক করতে বড় ধরনের প্রভাব রেখেছে।
বাড়তি মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের বড় শত্রু। ইতোমধ্যেই এতে সাফল্য এসেছে। ২০১১ এর পর থেকে মূল্যস্ফীতির হার ধারাবাহিকভাবে কমছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি কমে নভেম্বর ২০১৬ শেষে ৫.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ ধারা এখনও ক্রম হ্রাসমান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হয়েছিল ২২.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে গত অর্থবছরে হয়েছে ৪২.৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, এই আট বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে ৯১ শতাংশ। রপ্তানি ১১৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৪.২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স ৫৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চারগুণের বেশি বেড়ে এখন ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
এই পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে দেশের নয় মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থানে রয়েছে। ডলার-টাকার গড় বিনিময় হার এখন ৭৮.৭২ টাকা। এই বিনিময় হার কয়েক বছর ধরে এর আশেপাশেই রয়েছে। পাশের দেশের রুপীর চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী আমাদের টাকা। আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ ডলার। আগের বছর ছিল ১৩১৬ ডলার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এরই মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। তার মানে মাথাপিছু আয় বাড়ার হার আগামীতে আরও বেশি হবে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বয়স পঁচিশ বছরের কম। তরুণ এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান দিতে পারলে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে যাবে।
অর্থনীতির এসব অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধির চালক কৃষি, রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাক শিল্পের সমান্তরাল প্রসারের কারণে। এসবই কর্মসংস্থান-বর্ধক খাত। এ কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রাও এখনও পর্যন্ত সহনীয় রয়েছে। ষোলো কোটি মানুষের দেশ হলেও আমরা গভীরভাবে ‘কানেক্টেড’। শহর আর গ্রামের সংযোগ খুবই নিবিড়। তাই গ্রামীণ মানুষের আয় রোজগার বাড়ার প্রভাব শহরের মানুষের জীবনকেও প্রভাবান্বিত করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে চাঙ্গা রেখেছে। শিল্পায়নের গতি বাড়াতে সাহায্য করছে। দেশের বিনিয়োগকারীরা উন্নত প্রযুক্তি, বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।
নারী উদ্যোক্তারাও এতে সমানতালে অংশগ্রহণ করছেন।
এরই মধ্যে ‘নিম্ন আয়ের দেশের’ গ্লানি ঘুচিয়ে আমরা ‘নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের’ মর্যাদা লাভ করেছি। আমাদের সামনে এখন পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশ হবার হাতছানি। সে লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছি। তাই যদি সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নগরায়ন, শিল্পায়ন, তরুণ জনশক্তির সমন্বয় ঘটানোর স্বার্থে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা যায় তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ২০৩০ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতে তার কোনোই অসুবিধা হবে না। পরবর্তী সময়ে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হবার যে স্বপ্ন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেখছেন তাও অবাস্তব নয়।
বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যক্তিখাতের নেতৃত্বে রপ্তানিমুখী শিল্পনির্ভর দ্রুত অগ্রসরমান এক অর্থনীতির নাম বাংলাদেশ। এ দেশের প্রবৃদ্ধি সহায়ক উপাদানগুলোর প্রধান খাত হচ্ছে রপ্তানি আয়, যার ৮১ শতাংশই আসে শ্রমঘন গার্মেন্টস খাত থেকে। গার্মেন্টস খাত দ্রুত উন্নতি করছে। রানা প্লাজা ও তাজরীন ট্র্যাজেডির পর গার্মেন্টস খাত আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপকহারে আমাদের বস্ত্র উদ্যোক্তাদের কারখানার পরিবেশ উন্নততর করছে। ৩৬টিরও বেশি কারখানা সবুজ কারখানা হিসেবে রুপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে ২০ এরপর পৃষ্ঠা ১৪

















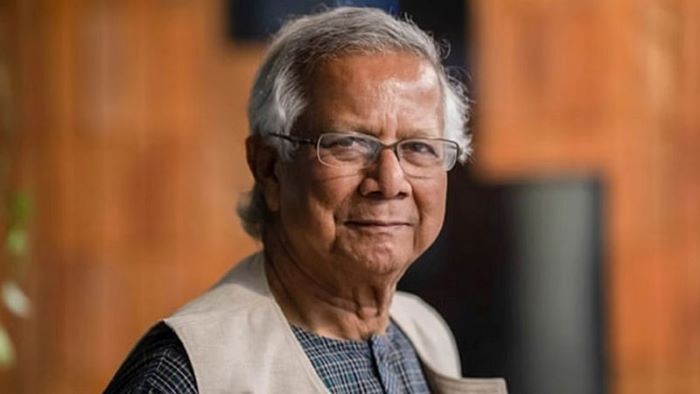



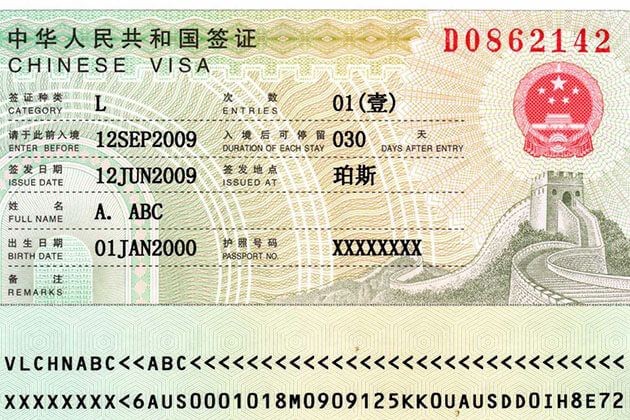



_School.jpg)






