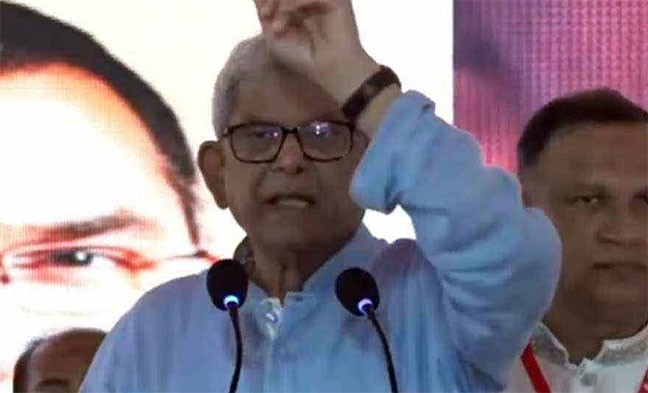তাসমিয়াহ আহমেদ : জমে থাকা ওষুধ বিষয়ক সব মামলা আগামী ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য নিম্ন আদালতের প্রতি আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এক হিসাবে দেখা গেছে ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আদালতে ওষুধ নিয়ে দেড় লক্ষাধিক মামলা ঝুলে আছে।
উচ্চ আদালত বলেছেনÑবিচারক, তদন্তকারী কর্মকর্তা, সরকারি কৌশুলীÑএরা সবাই যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এই মামলাগুলোকে নিতো, তাহলে প্রতিটি মামলা শেষ হতে একদিনের বেশি হয়তো লাগতো না।
কেবল ওষুধ বিষয়ক মামলাতেই নয়, এরকম আরও অনেক বিষয়েই আমরা মাঝেমধ্যে হাইকোর্ট থেকে নানা নির্দেশনা পাই। কিন্তু বাস্তব সেসব নির্দেশনার কয়টিই বা বাস্তবায়িত হয়। আর এটিই হচ্ছে আমাদের দেশে আইনের শাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।
আমাদের দেশে আইন ও আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ দেখভাল অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। আমার এই ভাবনাটি এমনি এমনি আসেনি। সাম্প্রতিক সময়ের দু’টি উদাহরণ দেই।
‘তুরাগকে মৃত ঘোষণার সময় হয়েছে’ শীর্ষক একটা প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন ২০১৬ সালের ৭ নভেম্বর একটি রিট আবেদন করে। দুদিন পর হাইকোর্ট সরকারকে নদী ভরাট এবং তুরাগ তীরে সকল নির্মাণ বন্ধ করতে বলেন। কেবল তাই নয়, এই আদেশ যে মান্য করা হয়েছে, তার একটা প্রতিবেদনও দাখিল করতে বলেন।
২০১৭ সালের অক্টোবরে গাজীপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাইকোর্টের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি সেখানে জানান, সেখানে নদী তীরে অবৈধভাবে ৩০টি ভবন তৈরি হয়েছে। সে বছরেরই ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন অবিলম্বে ওই স্থাপনাগুলোকে ভেঙে ফেলতে।
সবশেষে ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নদী দখল বিষয়ে একটি রায় দেয়া হয়। এই রায়টি আসে তুরাগ নদী দখলের বিষয়ে ২০১৬ সালে দায়ের করা একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে। রায়ে হাইকোর্ট নদীকে ‘জীবন্ত সত্ত্বা’ এবং ‘আইনগত ব্যক্তি’ হিসাবে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ ড. আইনুন নিশাত বলেন, আট দশ বছর আগে একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলো বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডাব্লিউটিএ), তারা নদী তীরে গড়ে ওঠা বেশ কিছু স্থাপনা ভেঙেও দিয়েছিলো। এরপর তারা একটা আজব কাজ করেছিলো, নদী তীরে নিজেরাই কিছু স্থাপনা গড়ে তুলেছিলো। এনিয়ে পরে সমালোচনা হলে, সেগুলোও ভেঙে দেয়া হয়। আর তারপর আগের সেই অবৈধ স্থাপনাগুলো আবার গড়ে ওঠে।
তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত আইন এবং আদালতের আদেশগুলো বাস্তবায়নই যেন এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
গণমাধ্যমে প্রকাশিত আর একটি প্রতিবেদনের কথা বলি। গত ২৬ জানুয়ারি ডেইলি স্টারে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, একটি ধর্ষণ ঘটনায় ধর্ষিতাকে পরীক্ষার জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে নেয়ার আগেই নানা অজুহাতে ছয়দিন পার করে দেয়া হয়েছে। অথচ ধর্ষিতাকে অতি দ্রুত পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ২০১৮ সালে এপ্রিলে হাইকোর্টের দেয়া সে নির্দেশনায় পরীক্ষার জন্য দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারাকে ‘শাস্তিযোগ্য অপরাধ’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে ২০১৫ সালে কুড়িল বিশ্বরোডে মাইক্রোবাসে একজন গারো নারীকে ধর্ষণের ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানেও ধর্ষিতাকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে নিতে তিন দিন পেরিয়ে যায়। এভাবে হাইকোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পুলিশ বারবার লংঘন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতি মাসে তাদের ওখানে যে ৫০ জনের মতো ধর্ষিতাকে পরীক্ষার জন্য আনা হয়, তার মধ্যে ২০ শতাংশকেই আনা হয় নির্ধারিত সময়েরও অনেক পরে।
এভাবে, যদিও আমরা বলি যে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলো খুবই ভালো, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় সুফলটা আর পাওয়া যায় না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যতোদিন এই প্রবণতা দূর করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্তআইনের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছবে না। (লেখক : সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এবং ডেইলি আওয়ার টাইমের নির্বাহী সম্পাদক) সম্পাদনা : রেজাউল আহসান