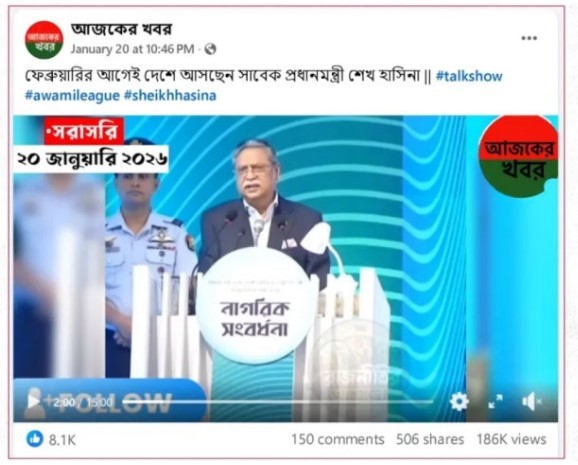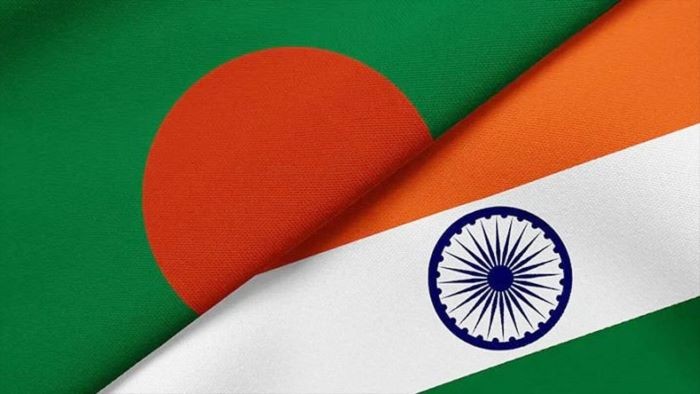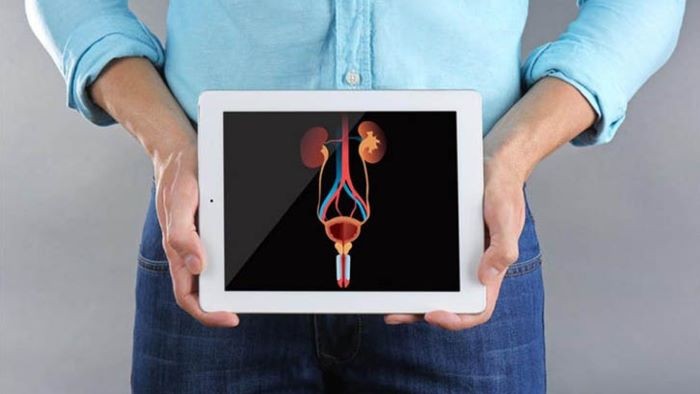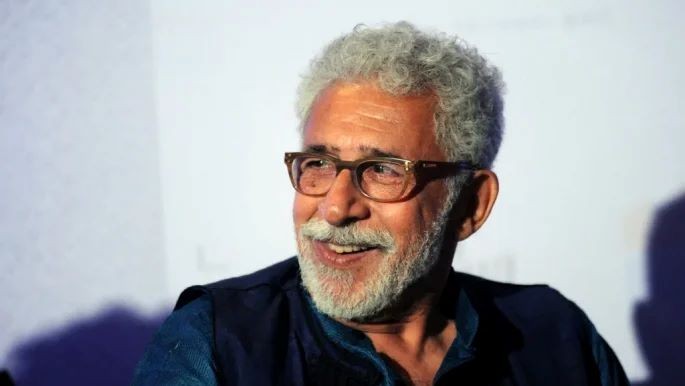তিনি আরও বলেন, শ্রমিকরা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দাবি করতেই পারে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করা উচিত এবং মজুরি বৈষম্যের যে ধারাটা অব্যাহত আছে এটাকে পাল্টাতে হবে। তা না হলে সমাজ থেকে এই বৈষম্য দূর করা যাবে না। এখন শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন স্কেলের বেতন দাবি করেছে। এটা তাদের একটা যুক্তি। কিন্তু দেখার বিষয় হলো যে, বাংলাদেশ সরকার যে পে-স্কেল ঘোষণা করেছে তার সর্বনিম্ন মজুরিটা কত। কারণ সর্বনিম্ন পে-স্কেল থেকেও শ্রমিকরা কিছু বেশি পায়। পাকিস্তান আমল থেকেই শ্রমিকরা নির্ধারিত পে-স্কেল থেকে বেতন কিছু বেশি পেয়ে আসছে। কারণ পে-স্কেলের পরও সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পেতেন, অবসরকালীন সুবিধা পেতেন কিন্তু শ্রমিকদের এই সুবিধাগুলো নেই।
পে-স্কেল থেকেও শ্রমিকদের বেতন কিছুটা বেশি থাকা উচিত, যেটা অতীতেও ছিল এবং এটা একটা ট্রাডিশন। আমাদের শ্রম আইনে আছে জীবনযাপনের মান, জীবনযাপনের ব্যয়, উৎপাদনের ব্যয়, উৎপাদনশীলতা এবং অন্যান্য সেক্টরের মজুরি এগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এর সাথে বিশ্ববাজারের পণ্য হিসাবে পার্শ¦বর্তী দেশের পোষাক শ্রমিকদের বেতনের সাথে একটা তুলনামূলক হার থাকা প্রয়োজন।
তিনি বলেন, গার্মেন্টস একটি গ্লোবাল পণ্য, একটি বৈশ্বিক পণ্য। চীনের, ভারতের, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামেরটা যেমন গার্মেন্টস পণ্য, বাংলাদেশেরটাও তেমনি গার্মেন্টস পণ্য। চীন, ভারত, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম যদি ঠিক মতো শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না। এখানে খেয়াল রাখতে হবে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি না বাড়লেও তাদের সমৃদ্ধি বেড়েছে এটা কিন্তু দৃশ্যমান। শ্রমিকদের প্রত্যাশা বিবেচনায় রেখে, জীবনমানকে বিবেচনায় রেখে এবং উপাদনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে বিশ্বজনীন বেতনের সাথে মিল রেখে একটা বেতন স্কেল রাখা উচিত।

 মারুফ হাসান নাসিম : মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি বিশ্বজনীন মাপকাঠি থাকা আবশ্যক। এই মাপকাঠি না থাকলে মজুরিটা হয়ে যাবে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দয়া অথবা আকাক্সক্ষার বিষয়। মজুরি শ্রমিকের অর্জিত অধিকার। সেই অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার একটা বিশ্বজনীন মাপকাঠি আছে এবং বাংলাদেশের বিবেচনায়ও এরকম একটা মাপকাঠি থাকা উচিত। পোষাক শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড নিয়ে আলাপকালে বিশিষ্ট রাজনৈতিক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন আমাদের অর্থনীতিকে এই কথা বলেন।
মারুফ হাসান নাসিম : মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি বিশ্বজনীন মাপকাঠি থাকা আবশ্যক। এই মাপকাঠি না থাকলে মজুরিটা হয়ে যাবে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দয়া অথবা আকাক্সক্ষার বিষয়। মজুরি শ্রমিকের অর্জিত অধিকার। সেই অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার একটা বিশ্বজনীন মাপকাঠি আছে এবং বাংলাদেশের বিবেচনায়ও এরকম একটা মাপকাঠি থাকা উচিত। পোষাক শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড নিয়ে আলাপকালে বিশিষ্ট রাজনৈতিক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন আমাদের অর্থনীতিকে এই কথা বলেন।