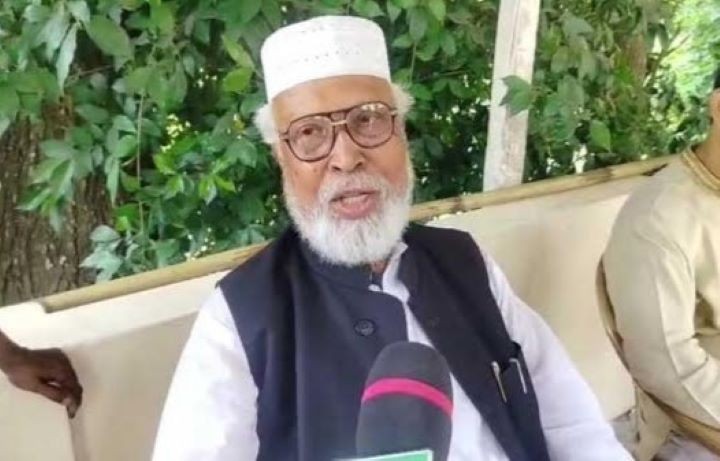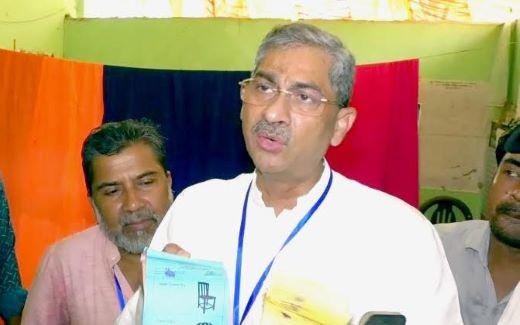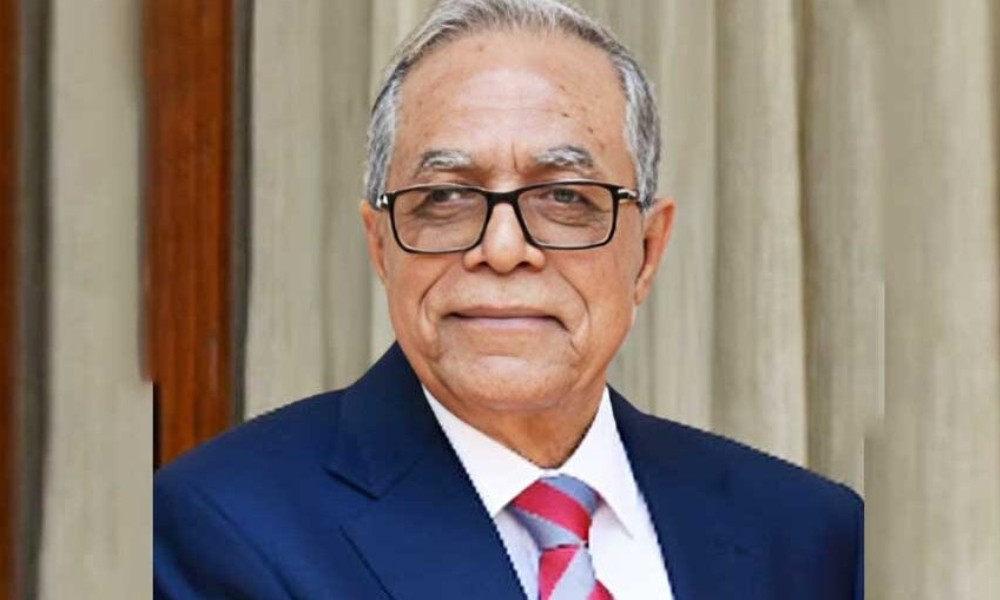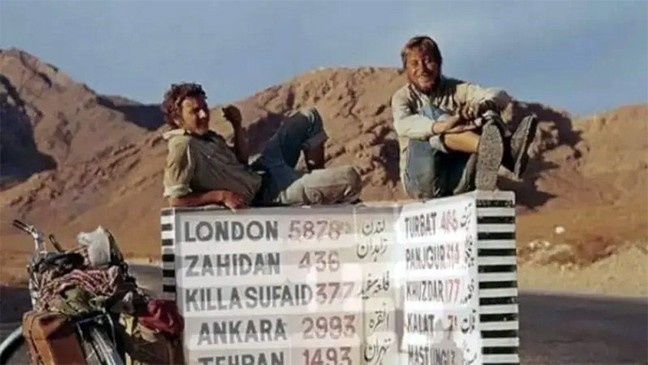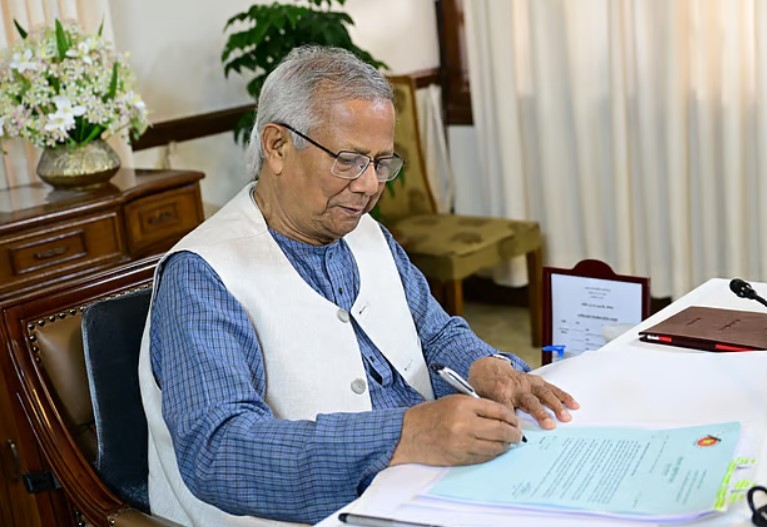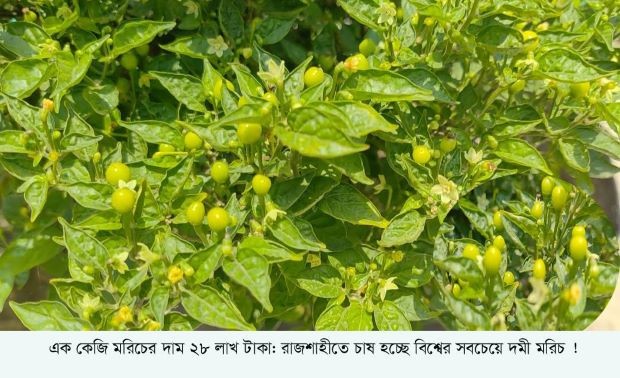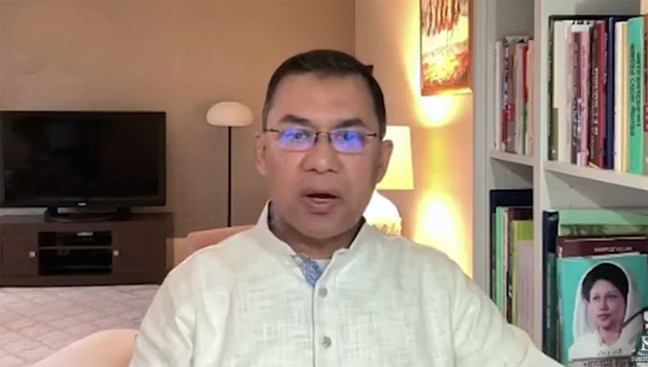আফসান চৌধুরী: সংস্কৃতি পরিচয়ের একটি মৌলিক উপাদান। কিন্তু এটি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার একটি উপজাত। মানুষ কেবল বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নিয়মগুলো ভাগ করে না বরং একে অপরের থেকে আলাদা করার জন্য একই ব্যবহার করে। সংস্কৃতিকে একটি পেঁয়াজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে বাইরের স্তরগুলো যেমন পোশাক, খাবার ইত্যাদি থেকে মধ্যবর্তী স্তরে চলে যায় যেমন সাংস্কৃতিক ও বিনোদন পণ্যগুলোর জন্য অগ্রাধিকার মূল মূল্যবোধ যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসের সমস্যা, ভাষা, জাতি ও জাতিগত উৎস ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃতির একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণ উপরোক্ত বিষয়গুলো নয় বরং সামাজিক আচরণের ধরনগুলো যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর ফলে উদ্ভূত হয় যা উপাদানগুলোর আধিপত্য, সুপ্ত থাকা পছন্দ করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। এটা সামাজিক মন সম্পর্কে পরিবর্তনের বিষয়।
সংস্কৃতির প্রয়োগকৃত মডেল : নেদারল্যান্ডসের অধ্যাপক গ্রিয়ার্ট হফস্টেড জাতীয় সংস্কৃতি চিহ্নিত করার একটি জনপ্রিয় মডেল তৈরি করেছিলেন। তার মডেলটি মূলত নৃতাত্ত্বিক প্রকৃতির যা অনুসারে সংস্কৃতি তৈরিতে ছয়টি প্রধান উপাদান রয়েছে। ১.শক্তি দূরত্ব (পিডিআই) : একটি রাষ্ট্র/সমাজে ক্ষমতার বৈষম্য মেনে নিতে কম শক্তিশালী সদস্যরা কতটা প্রস্তুত। ২. ব্যক্তিত্ববাদ (আইডিভি) : একটি ঢিলেঢালা সামাজিক কাঠামোর জন্য অগ্রাধিকার যেখানে ব্যক্তিরা কেবল নিজের ও তাদের নিকটবর্তী পরিবারের যত্ন নেবে বলে আশা করা হয়। ৩. পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব (এমএএস) : পুরুষত্ব কৃতিত্ব বীরত্বের জন্য একটি অগ্রাধিকার প্রতিনিধিত্ব করে, এটি আরও প্রতিযোগিতামূলক। নারীত্বের অগ্রাধিকার হলো সহযোগিতা, বিনয়, দুর্বলতার যত্ন নেওয়া জীবনযাত্রার মান আরও সম্মতি-ভিত্তিক। ৪. পরিহার (ইউএআই) : অনিশ্চয়তা পরিহার মানে সমাজ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন মাত্রা। ৫.লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন (এলটিও) : এটি কিভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। সমাজ কি ঐতিহ্যগত নাকি বাস্তববাদী? ৬. ইনডালজেন্স (আইভিআর) : এটি কীভাবে জীবন উপভোগ করে মজা করার সঙ্গে সম্পর্কিত মৌলিক ও প্রাকৃতিক মানব চালনার পরিতৃপ্তি নিয়ে কাজ করে। সংযম এমন একটি সমাজের জন্য দাঁড়িয়েছে, যা চাহিদার পরিতৃপ্তিকে দমন করে কঠোর সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করে।
এই মডেলটি কতটা দরকারী : এই মডেলটির ইতিবাচক বিষয় হলো এটি অন্তর্নিহিত মূল্য ভিত্তিক নয় বরং সামাজিক আচরণ ভিত্তিক। দুটি বিভাগ এমএএস আইভিআর স্টিরিওটাইপিক্যাল বিশ্লেষণাত্মক কাজ তাদের কিছু পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। এটি সম্ভবত বিশ্বায়ন ডিজিটালাইজেশন হওয়ার আগে বিকশিত হয়েছিল, যার অর্থ একটি সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু মৌলিক কোরটি কার্যকরী ও অন্যান্য বিশ্লেষণের জন্য একটি সূচনা পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ছয়টি দিক যেকোনও সমাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি উপস্থিত প্রতিটি উপাদানের ডিগ্রি পরিমাপের বিষয়। তারা ধ্রুবক নয় তালিকাটি বড় করার জন্য ক্রমাগত নতুন উপাদানগুলো আবির্ভূত হয়। সংস্কৃতি হলো আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এর জন্য আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। অন্য কথায় এগুলো কোনো সমাজের স্থায়ী সংস্কৃতি নয়।
বাংলাদেশের দৃশ্যপট : একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে একটি স্থানীয় এনজিও-ফিল্মস ফর পিস ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত একটি অধ্যয়ন প্রকল্পে সংস্কৃতির প্রধান উপাদানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সংজ্ঞায়িত করেছে। চিহ্নিত প্রধান কারণগুলো ছিল মানুষ অর্থনৈতিক চাহিদা, আকাক্সক্ষা ও শেষ পর্যন্ত সমৃদ্ধির আকাক্সক্ষা দ্বারা চালিত হয় যখন তারা ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। প্রভাবশালী মূল্য কাঠামো ঐতিহ্য বা বিশ্বাসে অবস্থিত নয় বরং জীবিকার নিরাপত্তা প্রয়োজন, যা প্রভাবশালী সামাজিক নিয়ম। মানুষ অভ্যন্তরীণ/সামাজিক/গৃহস্থালি বিষয়গুলোতে পরিবর্তন ও ঝুঁকি গ্রহণের প্রতি বিরুদ্ধ কিন্তু জীবিকার সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকির পথে রয়েছে। সমাজ সামষ্টিক, ক্লাস্টার ভিত্তিক, গোষ্ঠী চালিত পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিবাদী। ডিজিটালাইজেশন ঐতিহ্যবাহী নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও নিয়মিতভাবে নতুন সম্প্রদায় ও ঐতিহ্য তৈরি হয়। সরকারি ও বেসরকারি মূল্য কাঠামো অভিন্ন নয় তারা সংযুক্ত কিন্তু একই সময়ে স্বায়ত্তশাসিত। অংশগ্রহণকারীদের লাভ, কম লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বর্ধিত আয়ের কারণে সামাজিক মোকাবেলা করার ধরনগুলো একটি মিশ্র ব্যবসা কারণ পরিবারগুলো নিজেরাই বিভিন্ন প্রয়োজনগুলো পরিচালনা করার জন্য আরও ভালোভাবে সজ্জিত। সামাজিক পরিষেবাগুলো আরও উপলব্ধ, সামাজিক নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে যদিও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পেয়েছে।
হফস্টেড মডেল অনুসারে লিঙ্গভিত্তিক মূল্যগুলো বিতর্কিত, সমাজগুলো লিঙ্গভিত্তিক মূল্যের পরিবর্তে পারিবারিক যা আবার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে। প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক মূল্য মডেলিং দুর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ নারীরা শ্রমশক্তিতে বেশি প্রবেশ করছে, নিজেদের নায়ক ও অর্জনকারী হিসেবে ঘোষণা করছে আগের চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক পণ্য হিসাবে ইতিহাসের আনুষ্ঠানিক প্রচার সত্ত্বেও লোকেরা যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে অতীতের সঙ্গে মোকাবেলা করে। মানুষ চরম বাস্তববাদী যারা ইতিহাস ব্যবহার করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে যদি এটি তাদের উপযুক্ত হয়। তাই সাংস্কৃতিক পণ্য বেঁচে থাকার অগ্রগতির জন্য প্রত্নবস্তু হিসাবে নয়। ভোগ ও ধার্মিকতা মিশ্রিত হয় আরামে একসঙ্গে বসে পশ্চিমের মতো যৌনতার বাইরে চলে যায়। ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ্যে তাকওয়া প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে উল্টোটা চর্চা করা যেতে পারে যদিও প্রকাশ্যে নয়। ধর্ম সামাজিক নয় ধর্মতাত্ত্বিক। ‘বাংলাদেশে কেএপি ও ইসলাম’ বিষয়ে আরেকটি গবেষণা দেখায় যে, পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান কম, আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠান বেশি। যদিও এটি একটি সর্বজনীন দৃশ্য নয় যেখানে শহর-গ্রামীণ বিভাজন শ্রেণী বিভাজন ঐতিহ্যগত লিঙ্গ বিভাজনের মতো তীক্ষè হয়ে উঠছে। এটি হফস্টেড মডেলে আচ্ছাদিত নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতা নয় বৈচিত্র্যের দিকে নিয়ে যায়। এইভাবে একটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে উচ্চ আয়সহ ডিসপোজেবল এখন আরও উপলব্ধ। ডিজিটালাইজেশন নতুন সম্পদ এক্সেস, প্রভাব ও সম্প্রদায় গঠনের দিকে পরিচালিত করেছে। বৈচিত্র্যও উচ্চ যার মানে একটি ট্রানজিশন পরিবর্তনের পরবর্তী সেটের জন্য পথ তৈরি করছে। ধভংধহ.প@মসধরষ.পড়স. সূত্র : দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস। অনুবাদ : মিরাজুল মারুফ