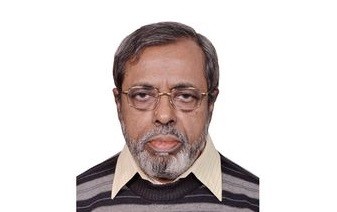
আবুল কাইয়ুম: লংকা খেতে ভারি ঝাল, বিশেষ করে ধানি লংকা। মরিচ শব্দের বিকল্প এই ‘লংকা’, যদিও আমরা অনেকে ভুলক্রমে একই অর্থে ‘লঙ্কা’ লিখতে অভ্যস্ত। অথচ ‘লঙ্কা’ হলো একটি দেশ, যা ঝাল হিসেবে খাওয়া যায় না। তবে মিষ্টি মনে করে বুঝি খাওয়া যায়? তা না হলে এখন শ্রীলঙ্কার কেনই-বা এমন হাড়জিরজিরে অবস্থা হবে! যাক গে, ওসব বড়ো চিন্তা, তা দিয়ে মোটা মাথা না-ঘামানোই ভালো। আমরা বরং আমাদের কাজে থাকি।
‘গরু’ শব্দটির জন্য খুব মায়া হয়। কারণ, আমরা ‘গরু-রচনা’ লিখে শিক্ষিত। কিন্তু দুঃখ, শব্দটি আধুনিক অভিধান থেকে হারিয়ে গেছে। ‘গোরূপ’ থেকে উৎপন্ন ‘গোরু’ এখন আভিধানিক শব্দ। কী আর করা! বর্জিত বানানটি ছেড়ে এখন ‘গোরু’ই লিখতে হয়।
আজ আবার ই-কার ও ঈ-কারের অপপ্রয়োগ নিয়ে আমরা আর একটু আলোচনায় বসি। আমরা জানি, কার-চিহ্নের হেরফের হয়ে গেলে শব্দের প্রকৃত অর্থ লুপ্ত হয়ে ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে যেতে পারে। যদি তা না-ও হয়, শব্দটি আর অর্থবহ থাকে না। সাধারণত দেখা যায়, ‘বড়ো ভাইয়ের বউ’-এই সম্পর্ক বোঝাতে ‘ভাবি’ না লিখে আমরা অনেকে ‘ভাবী’ লিখতে অভ্যস্ত। অথচ শেষোক্ত শব্দটির অর্থ ‘আগামী’ বা ‘ভবিষ্যৎ’। আবার ‘অধিক’ অর্থে ‘বেশি’-র পরিবর্তে প্রায়শ ‘বেশি’ লেখাও আমাদের অনেকের ধাতস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু ‘বেশি’ মানে ‘বেশধারী’, যা কেবল সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন-ভদ্রবেশী, ছদ্মবেশী ইত্যাদি)। ‘মালি’ ও ‘মালী’-এই দুই শব্দের প্রভেদও অনেকে বুঝি না; বাগান পরিচর্যাকারী হলো ‘মালি’ এবং যে মালা গাঁথে তাকে বলা হয় ‘মালী’। ফারসি হতে আগত শব্দ ‘বন্দি’ লিখতে গিয়ে আমরা অনেকেই ভিন্ন শব্দ ‘বন্দী’ লিখে ফেলি; এ অভ্যাসও আজন্মলালিত। অথচ ‘বন্দী’ মানে বন্দনাগায়ক আর ‘বন্দি’ অর্থ হলো অবরুদ্ধ বা আটক। ‘গৃহবন্দী’ নয়, আমরা লিখব ‘গৃহবন্দি’ এবং এভাবে নজরবন্দি, কারাবন্দি, বাঘবন্দি ইত্যাদি। আবার আমরা অনেকেই লিখি তীরধনুক, তীরন্দাজ ইত্যাদি; কিন্তু এই ‘তীর’ যে ‘নদীতীর’ এবং ‘বাণ’ বা ‘শর’ অর্থে ‘তির’ নয়-এটা হয়তো ভুলে গেছি। আমরা এভাবে কতো যে ওলট-পালট করে ফেলি তার অবধি নেই।
তবে ‘কি’ ও ‘কী’ শব্দের প্রয়োগের বেলায় আমাদের বিভ্রম একটু বেশি। এর আগে কয়েকবার এ-বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে; এবার সংক্ষেপে কিছু বলি। উৎপত্তি, গঠন ও অর্থের দিক দিয়ে দুটো একেবারেই পৃথক শব্দ। আমাদের এই সারকথা মনে রাখতে হবে-প্রশ্নের জবাব যদি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ দিয়ে হয়, সে-ক্ষেত্রে ‘কি’ এবং তা না হলে ‘কী’ বসে। অন্য কথায়, প্রশ্নকর্তা যদি কোনো বিষয়ে সোজা ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ জবাব জানতে চান তবে ‘কি’ এবং যদি তিনি প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতার বক্তব্য জানতে চান সে-ক্ষেত্রে ‘কী’ লিখতে হয়। উদাহরণ-
[১] ‘আপনি বইটি পড়েছেন কি?’- এর উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দিতে হবে বলে এখানে ‘কি’ হয়েছে। [২] ‘আপনি বইটি পড়ে কী বুঝলেন?’- এর উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দেওয়া যাবে না এবং বক্তব্যে বা বর্ণনায় দিতে হবে বলে এ-ক্ষেত্রে ‘কী’ বসেছে। এভাবে কীজন্য, কীভাবে, কীরকম, কীরূপ, কীসব, কীসে, কীসের প্রভৃতি দিয়ে প্রশ্নের জবাব ও বর্ণনায় দিতে হয়, তাই এসব শব্দ ‘কী দিয়ে। বিস্ময়সূচক পদ হিসেবেও ‘কী’ বসে।
[৩] আর ‘এমনকি’, ‘তেমনকি’, কিরূপে (যখন প্রশ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয় না), ‘কি যে’, ‘কত কি’, ‘আসল কি নকল’, কি গরিব কি ধনী’ প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত প্রয়োগ আমরা ই-কার দিয়ে লিখব। কারণ প্রশ্নবোধক নয় বলে এসব হ্যাঁ-না বা বর্ণনা দিয়ে প্রত্যত্তরের উপযুক্ত নয় । আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমরা ই-কার ও ঈ-কার ওলট-পালট করব না। আমরা যদি ‘কী’ স্থলে ‘কি’ এবং কিজন্য, কিভাবে, কিরকম, কিসব, কিসে ইত্যাদি লিখি তবে, নিজেদের যতো বড়ো বা ছোটো লেখক ভাবি না কেন, বোদ্ধা পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হবো। এসব ভুল বানান অভিধানেও নেই। সবাই ভালো থাকবেন। ফেসবুক থেকে
































