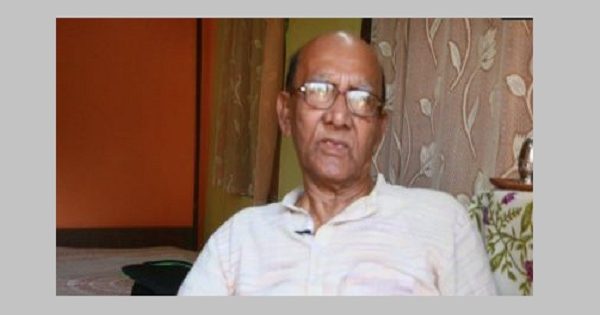
প্রিয়াংকা আচার্য্য : সুবিমল রায় কথাসাহিত্যিক। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কমকর্তা। বয়স ৮২। এখন আগরতলা শহরের অদূরে স্ত্রী পরিবার নিয়ে নিজবাড়িতে থাকেন। লেখালিখি করেই অবসরের অধিকাংশ সময় কাটান। একাত্তর সালে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প দপ্তরে কাজ করতেন। শহরের আরএমএস চৌমুহুনীতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। এর পাশেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অনেকেই সবার আগে এ ক্যাম্পে আসতেন। আর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রভূমি দৈনিক সংবাদের অফিসটিও ছিল পাশেই। ফলে পূর্ববাংলার অনেকের সঙ্গেই সহজে যোগাযোগ ও পরিচয় গড়ে উঠে। ‘মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে উন্মাদনা শুরু হয়। আসলে প্রতিবেশি রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সর্ম্পকটা ভালো ছিল না।
১৯৬৫ সালে যুদ্ধের পর থেকে তা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের পেটের ভেতর ঢুকে আছে। ফলে আমরা বেশ একটা অবরূদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। ত্রিপুরা থেকে বের হতে হলে আমাদের আসাম ঘুরে পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোথাও যেতে হতো। আমাদের মধ্যে একটা আশা ছিল যে দুদেশের সম্পর্ক ভালো হলে তা আমাদের স্বস্তির কারণ হবে। তাই শুরু থেকেই এ গণআন্দোলনের সব খবর আমরা নিতে চেষ্টা করতাম। কে আন্দোলন পরিচালনা করছে, আন্দোলন কোথায় মোড় নিচ্ছে সাধ্যমতো সব জানতে চেষ্টা করতাম।’ ‘যুদ্ধ শুরু হলে লক্ষ লক্ষ লোক ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে আসে। প্রশাসনের দিক থেকে রাতারাতি চললো ক্যাম্প তৈরির কাজ। স্কুল-কলেজসহ নানা জায়গায় শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আগরতলা শহরের জিবি হাসপাতাল, কলেজ টিলাসহ অনেক জায়গায় ক্যাম্প গড়ে উঠলো। শরণার্থীদের অসুস্থ জন্য হাসপাতালগুলো ২৪ ঘণ্টা খুলে দেয়া হলো।’ ‘ত্রিপুরা সরকার থেকে রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হলো। নতুন এই বিশাল ডিপার্টমেন্টে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে নানারকম সাহায্য সহযোগিতা আসতো। এছাড়া অন্যান্য রাজ্য এবং বিদেশ থেকে প্রচুর সাংবাদিকরা জড়ো হতে থাকে। সরকারি দপ্তরের প্রত্যেকেই আমরা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়ার সময় পেতাম না। বাসায় কোনও কোনও দিন যাওয়া হতো না। আজ এখানে, কাল ওখানে এই করে ছোটাছুটিতে দিন যাচ্ছিল।
মোট কথা ত্রিপুরায় একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।’ ‘তবে প্রচণ্ড চাপ স্বত্তেও কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে পর্যাপ্ত সাপ্লাই খুব ভালোভাবে সমন্বয় করার ফলে আমাদের রাজ্যে খুব বেশি একটা অসুবিধা হয়নি। এমন সংকটেও এখানে একজন মানুষও না খেয়ে মারা যাওয়ার রেকর্ড নেই।’ ‘এছাড়া স্থানীয়রাও ওপার থেকে আসা অসহায় মানুষদের পাশে আন্তরিকভাবে থেকেছে। এতো এতো বিপন্ন হিন্দু-মুসলমানকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরাবাসীর একটা প্রাণের আবেগ ছিল। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বাদ দিলে এখানকার প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে তাদের পাশে থেকেছেন। ‘এর পেছনের কারণটাও অনেক দীর্ঘ। দেশভাগের কারণে এখানে আসা অধিকাংশ মানুষের আদি নিবাসই বাংলাদেশ। উদ্বাস্তু হয়ে তারা দীর্ঘ সংগ্রামের পর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৭ থেকে ৭১। এর মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে তীব্র বিরোধ থাকায় ভিসা পাওয়া যেতো না। ফলে দেশ ছাড়ার পর অধিকাংশই আর কখনও নিজেদের জন্মস্থান দেখতে যেতে পারেননি। আমাদের ভেতর তাই একটা আকুতি কাজ করেছে।’ ‘আমি যেখানে থাকতাম তার সামনের দালানটিতে বাংলাদেশ থেকে আসা বিশিষ্টজনেরা বিতাড়িত হয়ে প্রাথমিকভাবে উঠতেন। তারপর সেখান থেকে উনারা অন্যান্য জায়গায় যেতেন। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক ছিল আমার অনুজপ্রতিম। লেখালিখি সূত্রেই তার সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার অফিসেও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হতো। এছাড়াও দৈনিক অগ্রগতির সম্পাদক নেপাল দে-এর সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিলো। পত্রিকা ছাড়াও তিনি অনেক টেম্পপ্ল্যাট মুক্তিবাহিনীর পক্ষে প্রকাশ করতেন। তার অফিসটিও দুই বাংলার লোক সমাগমের কেন্দ্র ছিল।’
‘সেই জন্য ওপাড়ের অনেকের সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারা অনেকেই বিভিন্ন সময়ে হতাশ হয়ে যেতেন। দেশ কবে স্বাধীন হবে বা তারা আর কোনওদিন দেশে ফিরতে পারবেন কিনা এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতেন। আমরা তখন তাদের নানা কথায় উজ্জীবিত করতাম। উৎসাহিত করতাম।’ ‘আগরতলা শহরে তখন গুটিকয়েক স্টুডিও ছিল। একটি আমার বাসার পাশে হওয়ায় সেখানে প্রায় সন্ধ্যাতেই দেখতাম যারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ট্রেনিং নিয়েছে তারা লুঙ্গি গেঞ্জি পরে লাইন দিয়ে ছবি তুলতো। একদিন স্টুডিওর মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, এরা এতো ছবি তোলো কেন? উনি বললেন, আসলে এটা আর্মির নির্দেশ। এরা এখন পর্যাপ্ত ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। এরা দেশের ভেতরে অ্যাকিশন করতে ঢুকে যাবে।’ ‘এই যুবকদের অনেককেই দেখতাম হাসি-খুশি। তারা দেশের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে উদবেলিত। আবার অনেকেই ছিল বিষন্ন। মিশন শেষে ফিরতে পারবে কিনা তা নিয়ে উদ্বিঘ্ন। কয়েকজন ছেলের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরেনি। শুধু মুক্তিবাহিনীর নয়। আমাদের পরিচিত অনেক আর্মি অফিসারও যুদ্ধে যোগ দিয়ে আর ফিরে আসেননি। বিশেষ করে প্রথম দিনের যুদ্ধে অনেক ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল। সেদিন ভারত একটা বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল পাকিস্তানকে।’ ‘যুদ্ধে আগরতলা শহরও নিরাপদ ছিল না। রাতে ব্ল্যাক আউট করা হতো। কারণ পাকিস্তানি সেনারা সুযোগ পেলেই শেল ও বোমা ফেলতো। অনেক মানুষ শহর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিল। আবার অনেকে থেকেও গিয়েছিলেন। একদিন আমার স্ত্রী-ছেলেসহ বাড়ির সবাইকে যোগেন্দ্রপুর রেখে আমি ও আমার ভাই শহরে এলাম। আর সেদিনই সন্ধ্যায় আগরতলার বেশ কিছু জায়গায় শেলিং হলো। আমার খুব কাছের এক বন্ধুকে হারালাম।’ ‘একরাতে আমরা সবাই ঘুমিয়ে আছি। প্রায় ১টার দিকে বেশ কয়েকটা গোলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফেললো পাকিস্তানিরা।
একটা গোলা পড়লো আমাদের রান্না ঘরের পেছনে। আমরা যে উঠে পালাবো সেই অবস্থাও নেই পর পর ৮-১০টা গোলা আশেপাশে পড়তে লাগলো। একই সাথে ত্রাস ও উত্তেজনায় আমরা দিন পার করছিলাম।’ ‘ভারত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক আর্মি এখানে জড়ো হতে শুরু করে। নভেম্বরের শেষদিকে এক সন্ধ্যায় আমি অফিস থেকে ফিরে বন্ধুর বাসায় যাওয়ার পথে বটতলার কাছে আখউড়ার দিকটায় দেখলাম আর্মিরা মার্চ করছে। আর বেশ কয়েকজন নারী তাদের স্বাগত জানিয়ে কপালে সিঁদুর পড়িয়ে দিচ্ছে। সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে থাকা কিছু জিনিষ উপহার হিসেবে দিচ্ছে। যেন ভাইবোনের সম্পর্ক।’ ‘এরই মধ্যে আর্মির পক্ষ থেকে নানারকম নির্দেশনা আসতে থাকে। আমাদের শহর ছাড়তে না বলা হলেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে বলা হয়। অফিস থেকে বেতন ১ তারিখেই তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়। আমার স্ত্রী বীথিকা রায় অরুন্ধতী নগরে বোর্ডারের কাছে একটা সরকারি স্কুলে পড়াতেন। সেদিন স্কুলে বেতন নিতে গেলে আর্মি অফিসাররা তাদের তাড়াতাড়ি বেতন নিয়ে বাড়ি চলে যেতে বললেন। একটা থমথমে পরিস্থিতি দেখে দ্রুত সে বাসায় চলে এলো। এদিকে দুপুর পরিচিত এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তিনিও খুব সাবধানে থাকতে বললেন।’ ‘আমি সন্ধ্যার দিকে বটতলা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ কিনলাম। যুদ্ধ বাধলেও যেন কয়েকটা দিন বাড়ি থেকে না বের হয়েও চলতে পারি। আমার ছোটবাচ্চা ছাড়াও বাড়িতে তখন মা ছিলেন।
প্রায় ৮টার দিকে বাড়ি ফিরতে দেখি কলেজ টিলার দিকে বেশকিছু আর্মির গাড়ি ঘুরছে। আমি কোনও মতে বাড়ি ফিরতেই শুনলাম বিকট এক আওয়াজ। আর সেই যে শুরু হলো সারারাত চললো। যেন প্রলয়কাণ্ড। আমাদের মনে হয়েছিল পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গেছে।’ ‘সকালে দেখলাম ৩-৪টা পাকিস্তানি বিমান শহরে উপর দিয়ে যাচ্ছে। একটাকে ঘায়েলও করা হলো। সারাদিন কার্ফিও চললেও হাজার হাজার মানুষ আগরতলা ছাড়তে শুরু করলো। বিকেলে উআমরা শুনতে পেলাম, আমাদের আর্মি আখাউড়া পার হয়ে ঢাকার দিকে এগুচ্ছে। সমস্তু আগরতলাটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছিলো।’ ‘পৃথিবীর সব দেশেই যুদ্ধ চলাকালে আর্মিরা বেপরোয়া হয়ে উঠে। কিন্তু একাত্তর সালের যুদ্ধে এমন একটি ঘটনাও শুনতে পাওয়া যায়নি। ভারত বা বাংলাদেশ কোথাও কোনও অপ্রীতিকর খবর শুনতে পাওয়া যায়নি। তারা প্রকৃত অর্থেই সেভিয়র হিসেবে কাজ করেছেন।’













.jpg)


















