
নিজস্ব প্রতিবেদক: বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশেরও আবহাওয়া-জলবায়ুর রূপ বদল চরমভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একের পর এক দুর্যোগে তৈরি হচ্ছে জনদুর্ভোগ ও সংকট। চিরায়ত ষড়ঋতুর আদি চরিত্র বদলে যাচ্ছে। পঞ্জিকা মাফিক বর্ষায় বৃষ্টি ঝরে কম, প্রাক-বর্ষা পরবর্তী সময়ে ঝরে আরও বেশি। শীতের স্থায়িত্ব তেমন প্রভাব ফেলে না। গ্রীষ্মের খরতাপ মরুর আগুনের হলকা নিয়ে আসে। শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত আলাদা করে চেনা যায় না। আবহাওয়া-প্রকৃতির বিরূপতা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষের জীবনযাত্রায় নানামুখী অনিষ্ট ও ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে মানবসম্পদের গড় উৎপাদনশীলতা। কমছে সক্ষমতা।
সেই সঙ্গে বাড়ছে নানামুখী জনদুর্ভোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ধারায় বাংলাদেশে এসে পড়ছে অনেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব। যখন-তখন আঘাত হানছে ঝড়-তুফান ও সমুদ্রে নিম্নচাপ। এর সঙ্গে বজ্রাঘাতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হচ্ছে ফসল। আবহাওয়া-প্রকৃতির বিরূপ আচরণে আতঙ্ক ভর করেছে হাওর ও চরাঞ্চলের কৃষকদের মনে। শহর ও গ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্য বাড়িয়েছে উদ্বেগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত বছর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও ব্যাপকতা গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশিই পরিলক্ষিত হচ্ছে এ বছর। এর জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনকে বড় কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের এমন ধারা অব্যাহত থাকলে আরও বড় সমস্যার কবলে পড়তে পারে এমনটিই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
চলতি মৌসুমের শুরুর দিকে ব্যাপক শিলাবৃষ্টির ঘটনা ঘটে। এতে ফসলের ভয়াবহ ক্ষতি হয়। বর্তমানে নতুন করে আতঙ্কের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে বজ্রপাত ও অতিবৃষ্টি। এ বছর কেবল বজ্রপাতে এপ্রিলেই মারা গেছেন ৩০ জন।
গতকালই সারাদেশে বজ্রপাতে বাবা-ছেলে, স্কুলছাত্র, পোশাকশ্রমিক, নারী ও কৃষকসহ ১৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জে পাঁচ ও মাগুরায় চারজন প্রাণ হারান। এ ছাড়া গাজীপুর, নওগাঁ, নোয়াখালী, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটিতে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। গতকাল রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী বর্ষণ হয়েছে। এর সঙ্গে বয়ে যায় কালবৈশাখী। বৈরী আবহাওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌ ও সড়কপথে যানচলাচল সীমিত করা হয়।
অনেক স্থানে নৌপথে যানচলাচল বন্ধ রাখা হয়। ঢাকার সদরঘাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সব ধরনের নৌচলাচল বন্ধ করা হয়েছে। পদ্মা নদীতে ঝড়ো হাওয়ায় কাঁঠালবাড়ি-শিমুলিয়া নৌপথে ফেরিসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল গতকাল কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল। এ কারণে উভয় পাড়ে পারাপারের অপেক্ষায় অনেক যানবাহন আটকা পড়ে। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়াঘাটেও নৌযান চলাচল সীমিত করা হয়। কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ৪০০ যাত্রী নিয়ে মেঘনায় আটকা পড়ে একটি লঞ্চ। গতকাল সকাল থেকে থেমে থেমে ভারী বর্ষণের কারণে ঢাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বৈরী আবহাওয়ায় দেশের বিমানবন্দরগুলোয় স্বাভাবিক বিমান চলাচল ব্যাহত হয়।
সংখ্যার হিসাবে বিশ্বের চার ভাগের এক ভাগ বজ্রপাতই হয় বাংলাদেশে। তবে গত তিন বছরে বেড়ে গেছে বজ্রপাতের হার। একই সঙ্গে বেড়েছে প্রাণহানির ঘটনাও। বর্তমান সময়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ায় ২০১০ সাল থেকে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব জিওগ্রাফির অধ্যাপক ড. টমাস ডব্লিউ স্মিডলিনের ‘রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড সোশ্যাল ভালনারেবিলিটি’ শিরোনামে গবেষণা থেকে দেখা গেছে, প্রতিবছর মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৪০টি বজ্রপাত হয়। বাংলাদেশ দুর্যোগ ফোরামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বজ্রপাতে ২৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে ২০১৬ ও ২০১৭ সালেও মৃতের সংখ্যা ছিল দুই শতাধিক। তবে বজ্রপাত ঠেকানোর তাৎক্ষণিক কোনো প্রক্রিয়া না থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তার উল্টো হচ্ছে। বড় বড় গাছ ধ্বংস করে ফেলার কারণে গ্রামাঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। নতুন করে বনায়নও হচ্ছে না।
কৃষিজমির মধ্যে অতীতে তাল বা খেজুরগাছ লাগিয়ে বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা করা গেলেও বর্তমানে সেসব গাছও কমে আসছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের হাওর ও বিল অঞ্চল আর উত্তরের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং দিনাজপুর অঞ্চলে বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনা বেশি। এসব অঞ্চলে মুঠোফোনের টাওয়ার লাইটেনিং এরস্টোর লাগিয়ে বজ্রপাতের ঝুঁকি কমানো যায়।
১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের ভয়াল প্রলঙ্কারী দিন। এই দিনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছিল উপকূলীয় এলাকা। শুধু কুতুবদিয়ায় সে দিন আনুমানিক ৪৫ হাজার মানুষ নিহত হন এবং কয়েকশ কোটি টাকার সম্পদ বিলীন হয়। গতকাল বেদনাবিধুর ঘটনার ২৭ বছর পার হয়েছে। যদিও এর পর প্রায়শই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে বাংলাদেশ।
গত এক দশক ধরে প্রায় প্রতিবছরই ছোটখাটো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার মানুষকে এর বেশি শিকার হতে হয়। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সচেতনতা ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রচারে ক্ষতি ও মৃতের সংখ্যা কমেছে অনেক। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, বন্যা, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতসহ নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যোগ হচ্ছে। এমনকি গত কয়েক বছর অতিবৃষ্টি ও বন্যায় হাওর, চরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের মুখেও পড়তে হতে পারে দেশকে।
দেশের ধানের প্রধান জোগান আসে মূলত হাওরাঞ্চল থেকে। তবে গত বছর দেশের বেশ কয়েকটি হাওরে বাঁধ ভেঙে পানি ও অতিবৃষ্টিতে ডুবে যায়। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সীমাহীন খাদ্য সংকটে পড়া কৃষকরা এবার নতুন ধান চাষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন; কিন্তু এবার ফসলের ক্ষতি হলে তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু পাকা ধানে ফসলের ক্ষেত ভরে থাকলেও চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে হাওরের কৃষকদের মধ্যে। আকাশ কালো হলেই তাদের মধ্যে অজানা এক আতঙ্ক ভর করে। গত কয়েক দিনের ঘন ঘন বৃষ্টি তাদের মনে শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বছর যদি ফসল ঘরে তুলতে না পারে, তবে অনেকেরই মানবেতর জীবনযাপন করতে হবে। অন্যদিকে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি ও করালগ্রাসে বসতি হারিয়ে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে উপকূল, চর ও দ্বীপাঞ্চলের অভাবী মানুষরা। সূত্র: আমাদের সময়




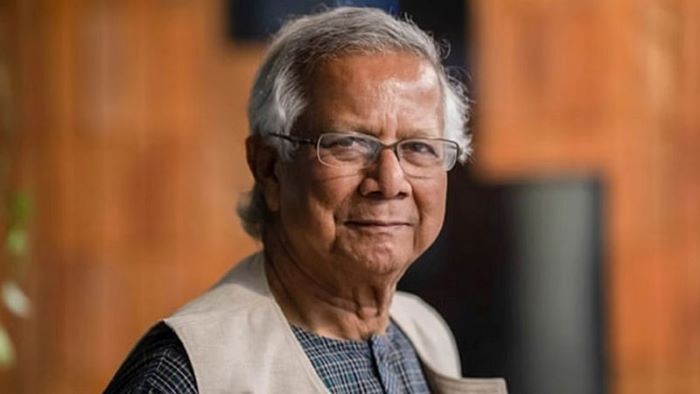
















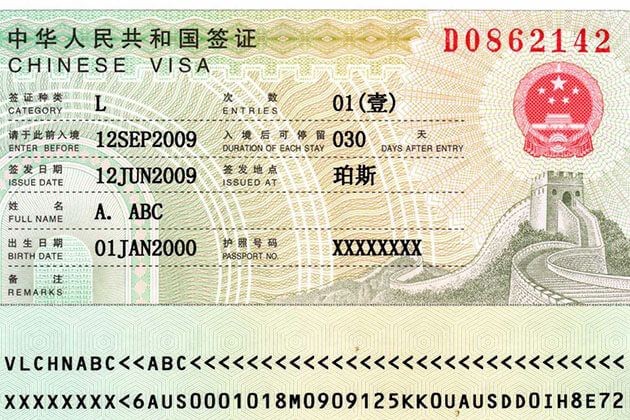



_School.jpg)






