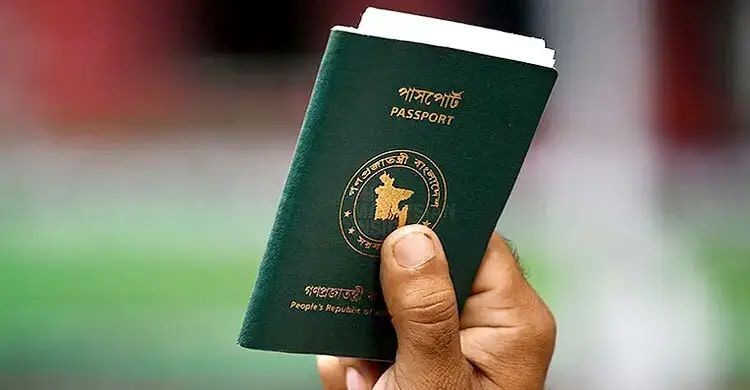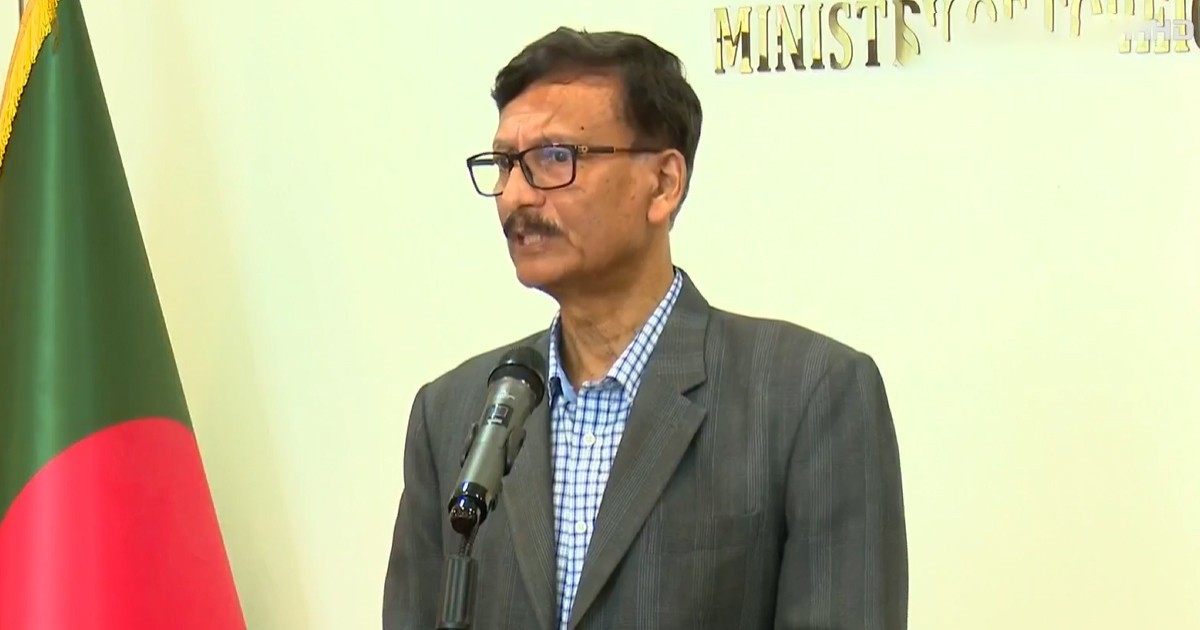বিভুরঞ্জন সরকার : বেশির ভাগ সময় রিকশায় চলাচল করতে হয়। সাধারণত আমি ভাড়া ঠিকঠাক করেই রিকশায় উঠি। মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ি; যখন চালক বলেন, যা ন্যায্য ভাড়া তাই দিয়েন।
কোনটা ন্যায্য ভাড়া? কে ঠিক করেছেন রিকশার ন্যায্য ভাড়া? বাস ভাড়া নির্ধারণের কর্তৃপক্ষ আছেন। তারপরও ভাড়া নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা আছে। বাসে যারা যাতাযাত করেন, তারা জানেন ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বচসা লেগেই থাকে।
রিকশা ভাড়া নির্ধারণের কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। মূলত রিকশাচালকরাই ভাড়া নির্ধারণ করেন এবং যাত্রীরা তা দিতে বাধ্য থাকেন। ন্যায্য শব্দটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। মজুরির ক্ষেত্রে এটা বেশি ব্যবহৃত হয়। ন্যায্য মজুরি চাই কিংবা দিতে হবে, এই স্লোগান হরহামেশাই শোনা যায়। আবার জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে গিয়েও ন্যায্য শব্দটা অনিবার্যভাবে এসে যায়। যেমন ন্যায্য দাম ইত্যাদি।
এই ন্যায্য শব্দটির ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন আছে। কোনটা ন্যায্য আর কোনটা অন্যায্য সেটা নির্ধারণ করবে কে? রিকশাচালক দশ টাকা বেশি নিতে পারলে তার কাছে তো সেটাই ন্যায্য বলে মনে হবে। আবার যাত্রীর কাছে ন্যায্য হবে কম ভাড়া দিতে পারলে। শ্রমিক বা কর্মজীবী মানুষ মজুরি বেশি পেলে সেটা ন্যায্য মনে করবেন। আর মালিক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মজুরি কম দিতে পারলে মনে করবেন ন্যায্য অবস্থানে আছেন।
কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের দাম একটু বেশি পেলে এবং ভোক্তারা কম দামে কিনতে পারলে ন্যায্য মনে করবেন। কাজেই ন্যায্য বিষয়টি আরো কিছু বিষয় দিয়ে প্রভাবিত এবং নির্ধারিত। এটা মূলত অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। আয়-ব্যয়ের সঙ্গে ন্যায্যতা সম্পর্কিত। একজন নিম্ন আয়ের কিংবা নির্ধারিত আয়ের মানুষের কাছে ইলিশ মাছের দাম পাঁচশ টাকা কেজি হাঁকলেও ন্যায্য মনে হবে না। আবার উচ্চবেতনভোগী এবং উপরিপাওনাওয়ালা ব্যক্তির কাছে ইলিশের কেজি দুই হাজার টাকা হলেও অন্যায্য মনে হবে না।
তবে ন্যায্যতা নির্ধারণের কিছু মানদ- ও মাপকাঠি আছে এবং থাকা উচিত । একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণের নিশ্চয়তা বিধান ন্যায্যতার একটি বড় শর্ত। এখানেও ন্যায্যতা নির্ধারণ খুব সহজ কাজ নয়। একজন দরিদ্র মানুষের খাদ্য তালিকা এবং একজন ধনী মানুষের খাদ্য তালিকা এক রকম হবে না। দুই অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষের ন্যায্যতা এক রকম হয় না, হবে না।
তবে ন্যায্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হলে রাষ্ট্র ও সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে বর্তমানে বৈষম্য বাড়ছে। সমতার বদলে অসমতা তীব্র আকার ধারণ করছে। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছে। নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ না হয়ে বিস্তৃত হচ্ছে। গড় আয় হিসাব করে মাথাপিছু আয় হয়তো বাড়ছে। কিন্তু এসব খবরের মধ্যে রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি। একজনের হয়তো বার্ষিক আয় বেড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা হলো। আরেকজনের হলো একশ কোটি টাকা। এই দুই জনের আয়ের হিসাব যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে গড় বের করে আমরা যদি বলি যে, আমাদের দেশের মানুষের গড় আয় বেড়েছে, তাহলে কি আমরা সত্যের কাছাকাছি হতে পারবো?
আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, দেশে ধনবৈষম্য বাড়ছে। পাকিস্তানি আমলে আমরা ২২ ধনী পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। তাদের শোষণের নিগড় ভাঙতে চেয়েছি। আজ আমাদের দেশে সেই রকম ধনী পরিবারের সংখ্যাও হয়তো হাজার ছাড়িয়ে লাখের ঘরে উঠেছে। ন্যায্যতা কমছে। বৈষম্য বাড়ছে। সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে সামাজিক অসন্তোষ বাড়বে এবং পরিণামে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও নষ্ট হবে। বাংলা শব্দ না হলেও ‘ইনসাফ’ শব্দটি আমাদের কাছে ব্যাপকভাবেই পরিচিত। আমরা দেশকে উন্নয়নের রোলমডেল বানাতে চাইছি। ভালো কথা। একই সঙ্গে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথাটিও ভুলে থাকলে চলবে না। বহুতলা আর গাছতলার মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে না আনতে পারলে এক সময় ন্যায্যতার দাবিকে কোনো শক্তি দিয়েই দাবিয়ে রাখা যাবে না।










.jpg)