
নিজস্ব প্রতিবেদক : ঢাকায় মসজিদ নির্মিত হয়েছে কখনো ধর্মীয় অনুপ্রেরণায়, কখনো বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে। গবেষক মো. মোশারফ হোসেনের ‘শহরের নাম ঢাকা ঐতিহ্যের নাম ঢাকা’র তথ্যমতে, সেকালে অভিজাত মুসলিম ঢাকাবাসীর একটা অংশ ছিল ‘মোবাল্লিগ’ বা ‘ধর্মপ্রচারক’। ঢাকায় মসজিদ স্থাপনে এবং মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে এ মোবাল্লিগদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। নাট্যকার সাঈদ আহমদের ‘ঢাকা আমার ঢাকায়’ ধর্ম প্রচারক বাবুবাজারের বাহার শাহ বাবা ও বেচারাম দেউড়ির কাশ্মীরি শাহ্ সাহেবের বর্ণনায় এর প্রমাণ মেলে। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি ওয়াল্টার্সের ‘Census of the City of Dacca’ অনুসারে ১৮৩০ সালে ঢাকায় মুসলমান ছিল ৩৫ হাজার ২৩৮ জন, আর মসজিদ ছিল ১৫৩টি। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের তথ্য মতে ১৯৮১ সালে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৭টিতে। কবি ও গবেষক রফিকুল ইসলাম রফিক লিখেছেন, ‘মসজিদের শহর’ কবিতা, যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন ঢাকার আদি মসজিদের কথা—
‘পাঠান যুগে পাকা মসজিদ প্রথম উঠল গড়ে
আরো মসজিদ শায়েস্তা খান গড়েন অতঃপরে।
বিনত বিবি মসজিদ সে তো বিরাট কীর্তি এক
পাঠান যুগে তৈরি এটা ইতিহাসে উল্লেখ।’
বিনত বিবির মসজিদের গায়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ঢাকা শহরে অবস্থিত মসজিদগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরনো। ১৪৫৭ (মতান্তরে ১৪৫৬) খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের প্রায় দেড় শ বছর আগে নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (মতান্তরে মাহমুদ) শাহ্ যখন বাংলার সুলতান, সে সময় এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। নারিন্দায় এই মসজিদের অবস্থান। মাহুতটুলীতে ছিল বিখ্যাত ‘তারা মসজিদ’। বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের টাকায় এবং স্ট্যাম্পে তারা মসজিদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমান ‘স্মৃতির শহর’-এ এই তারা মসজিদকেই ‘সিতারা মসজিদ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
মসজিদগুলোর সঙ্গে নামাজ ছাড়াও নানা রকমের যোগ ছিল সেকালের ঢাকাবাসীর। সে সময় মসজিদের পাশেই একটি করে বাড়ি থাকত। কয়েকটি ঘর থাকত এ বাড়িটিতে। এগুলো ছিল মসজিদের সম্পত্তি এবং ইমামের তত্ত্বাবধানে। তিনি এসব ঘর ভাড়া দিতেন এবং এ টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় হতো। নানা কাজে দূর দূরান্ত থেকে ঢাকায় আসত মানুষজন। এখনকার মতো অগণিত হোটেল-রেস্তোরাঁ গড়ে ওঠেনি তখনো। তা ছাড়া তখন ঢাকা শহরে বাস করার সংগতি অনেকেরই ছিল না। ফলে স্বভাবতই শেষ আশ্রয়স্থল ছিল মসজিদ। কবি বেলাল চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় জানা যায়, সে সময় এ ঘরগুলোর মাসিক ভাড়া ছিল ২৩ টাকা এবং এ রকম একটা ঘরে তাঁর বেশ কিছুদিন থাকার সুযোগ হয়েছিল।
বিচার-সালিসের ক্ষেত্রেও মসজিদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মহল্লায় কেউ অপরাধ করলে সর্দারের কাছে নালিশ যেত। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের সর্দারদের বিচারব্যবস্থা টিকে ছিল। পঞ্চায়েতের আবার দুটি ধরন ছিল। ঢাকার যেসব এলাকার অধিবাসী বাংলায় কথা বলতেন, তারা ছিলেন ‘বারাহ’ পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। আর, উর্দুভাষী ‘খোশবাস’ শ্রেণি ছিল ‘বাইশ’ পঞ্চায়েতের অধীন। এশার নামাজের পর মসজিদের খোলা আঙ্গিনায় সর্দার বিচার করতেন। সর্দারের বিচারব্যবস্থা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কঠিন মামলা-মোকদ্দমা নিয়েও কেউ আদালতে যেতে চাইত না। পুলিশের কাছে গিয়ে থানায় এজাহার লেখাটাকে ঢাকার আদি বাসিন্দারা খুবই অসম্মানজনক কাজ মনে করতেন। সচরাচর সর্দারের বিচার সবাই মেনে নিতেন। প্রায় সব পঞ্চায়েতেই একজন হাঁকিদার থাকতেন। হাঁকিদার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় আনোয়ার হোসেনের ‘আমার সাত দশক’-এ। মহল্লার তিন রাস্তা বা চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে জোরে ঢোল বাজাতেন হাঁকিদার। ঢোলের শব্দ শুনে অনেকেই তাঁকে ঘিরে ধরত।
তিনি চিৎকার করে বলতেন, ‘ভাই সব, আজ অমুকের বিচার আছে অমুক মসজিদে, এই সময়ে...।’ ধারণা করা হতো, মসজিদে বিচার করলে পক্ষপাতিত্ব হবে না। ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েত সর্দার মির্জা আবদুল কাদেরের বিচারের কাহিনি পাওয়া যায় সাঈদ আহমেদের ‘ঢাকা আমার ঢাকায়’—
‘শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী... এক শাঁখারি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। কিন্তু এ প্রেম শাঁখারিরা মেনে নিতে পারছিল না। দেবদাস চক্রবর্তীকে একতরফাভাবে দায়ী করে মেয়েটির ভাইয়েরা সরদারের কাছে নালিশ করল—‘সরদার সাহেব, বইনরে নষ্ট কইরা ফেলাইছে পোলাটা। এর একটা বিহিত করন লাগব।’...বিচারের দিন উভয়পক্ষের জিজ্ঞাসাবাদের পর কাদের সরদার দেখতে পান, মেয়ের ভাইয়ের বাড়াবাড়ি বেশি ছিল। ফলে তিনি মেয়ের ভাইকে দায়ী করে শাস্তি দেন। অন্যদিকে শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীকে ভালোভাবে লেখাপড়া করার পরামর্শ দেন।’
শুধু বিচারের ঘোষণা দেওয়াই নয়, কেউ মারা গেলেও হাঁকিদার ঢোল নিয়ে বের হতেন, মহল্লার সবাইকে জানিয়ে দিতেন খবরটা। কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে মহল্লার প্রত্যেক বাড়ি বা পরিবারের পক্ষ থেকে অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হাজির থাকতে হতো জানাজায়। লাশ দাফনসহ সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত মসজিদ কমিটি। সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবেও মসজিদ ব্যবহার হতো। বিয়ে উপলক্ষে বরপক্ষের লোকজন কনেপক্ষের বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে অবস্থান করত। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হতো মসজিদের পাশের ঘরে। জামাই আসতেন মসজিদে। কনে থাকতেন নিজের বাড়িতে। বিয়ে পড়ানোর পর বরপক্ষ কনেপক্ষের বাড়িতে যেত। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর ‘ষাট বছর আগের ঢাকা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘বরযাত্রীদের সঙ্গে মহিলা যাঁরা আসতেন তাঁরা অবশ্য প্রথমেই কন্যাগৃহে প্রবেশ করতেন। মসজিদকে এ ব্যাপারে ব্যবহার করার ফলে মসজিদের কিছু উপার্জন হতো। ইমাম সাহেব কিছু উপঢৌকন পেতেন এবং বরপক্ষীয়রা মসজিদের উন্নতি সাধনের জন্য কিছু অর্থ দান করত।’
মসজিদে শুধু বিয়ে পড়ানো হতো না। বিয়ের পর কোনো কারণে বর-কনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে বা তারা পৃথক হয়ে যেতে চাইলে বর ও কনেপক্ষের বয়োজ্যেষ্ঠরা মসজিদে এসে বসতেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা না হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন।
তখনকার দিনে পবিত্র রমজান মাসে মসজিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক বাড়ি থেকে ইফতারি পাঠানো হতো মসজিদে। ইফতারের সময় অনেক রোজাদার ইফতারি করতেন একসঙ্গে। বিশিষ্ট গবেষক হাসেম সুফির তথ্যমতে, ইসলামপুরের কাদের সরদার ২০ রোজার দিন ঢাকার অনেক মসজিদে নিজ খরচে ইফতারি হিসেবে তেহারি বিতরণ করতেন।
সেকালে জুমার নামাজের পর মসজিদের সামনে দুটি লাইনে আশপাশের বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নামাজ শেষে এ পানিতে দোয়া পড়ে দিতেন মুসল্লিরা। এ পানি পানে রোগমুক্তি হবে—এ বিশ্বাস নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরে যেত। এ ছাড়া খুব ভোরে পাড়ার ছোট ছেলেরা মসজিদের মক্তবে পড়তে আসত। মক্তবে সাধারণত আরবি ও কোরআন শিক্ষা দেওয়া হতো। এ মক্তবগুলো ছিল মাদরাসা থেকে আলাদা। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই এ মক্তবে পড়তে আসত।
সে সময় ঢাকায় ঘোড়দৌড় আর জুয়ার প্রচলন ছিল। এগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মসজিদ থেকেই। চকবাজার শাহি মসজিদ ছিল ওলেমাদের কেন্দ্র। বিশেষ করে সেকালের খ্যাতনামা আলেম মুফতি দীন মোহাম্মদ তাফসির ও বয়ানের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে ঘোড়দৌড়ের খারাপ দিকগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেন। গড়ে ওঠে মসজিদকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন। ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় সরকার ঘোড়দৌড়, জুয়া ও মদ্যপান আইন করে বন্ধ করতে সক্ষম হয়।
তখনকার দিনে নামাজিরা মসজিদের সামনে জুতা রেখেই নামাজ পড়তে যেতেন। জুতা হাতে নিয়ে মসজিদে ঢোকার প্রয়োজন ছিল না। এ প্রসঙ্গে চকবাজারের আদি বাসিন্দা আব্দুস সালাম স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে—‘তখনো চকবাজারে কোনো পাকা মার্কেট গড়ে ওঠেনি। একটি বিশাল মাঠ ছিল। ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য নিয়ে মাঠেই বসতেন। তাঁরা চৌকিতে বসে কেনা-বেচা করতেন। চকবাজারে শাহি মসজিদে আজান হলে ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য খোলা রেখেই নামাজে চলে যেতেন। কিন্তু কখনো চুরির ঘটনা হতো না।’
আদি ঢাকাবাসীর মধ্যে ধর্মীয় নিয়ম মেনে জীবনযাপন করার প্রবণতা ছিল বরাবরই। মুয়াজ্জিনের আজানের বাণী যখন আকাশে-বাতাসে ধ্বনি তুলত তখন ঢাকার মানুষ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারত না। জীবনের শেষ দিনটিতেও সম্পর্কযুক্ত থাকত তারা মসজিদের সঙ্গে। এমনি অবিচ্ছেদ্য ছিল মসজিদ আর মানুষের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা। কালের কণ্ঠ










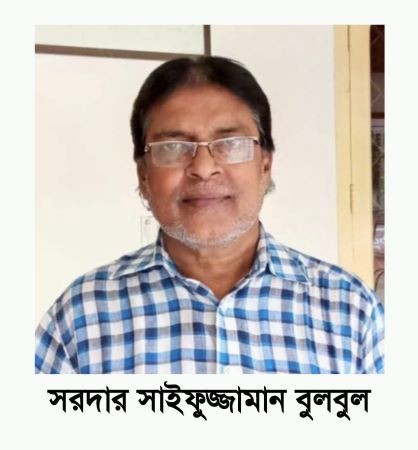








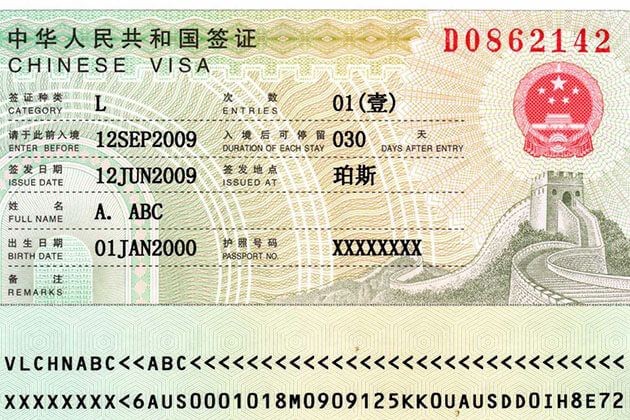









_School.jpg)
